
কবিতা, ইন্তিফাদা ও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
‘কবিতা আমার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র—কবিতা আমার ভালোবাসার বকুল—প্রতিরোধের হাতিয়ার...।’ কথাটি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্র; তাঁর অল্প কিছু গদ্য থেকে তুলে নেওয়া যায় এ রকম চমকপ্রদ উক্তি, তারুণ্যের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সমবায়ে বোঝা যায় কবিতা ও প্রতিরোধের আন্তসম্পর্ককে। রুদ্রের হাতে গোনা গদ্যগুলো আমাদের এ-ও জানান দেয়, তিনি খুব ভালোভাবেই মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা, আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও কবিতার যোগসূত্রকে বুঝে নিয়েছিলেন। যদিও আমরা রুদ্রকে স্থাপন করেছি কয়েকটি বিন্দুতে; এক. রুদ্রের বিষয়বস্তু মূলত প্রেম; দুই. মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়া তাঁর কবিতার শিল্পগত মূল্য নেই; তিন. জনপ্রিয়তার বাসনায় কবিতার ‘শিল্পত্ব’কে বিসর্জন দিয়েছেন। মোটাদাগে, এভাবেই রুদ্রকে চিহ্নিত হতে দেখা যায় বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে।
কিন্তু উল্টো দিকে ফিরে তাকালে মনে হয়, রুদ্র খুব সচেতনভাবে কবিতার আধুনিকতাবাদী ‘শিল্পত্বে’র ধারণাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন, পাঠকের সঙ্গে কবিতার দূরত্ব কমিয়ে আনতে চেয়েছেন। কবিতার প্রকরণ কিংবা শরীর সংস্থান নিয়ে তিনি মোটেও অসচেতন নন। কবিতায় প্রকরণের বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করেছেন; ছন্দের হিসেবনিকেশেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রায় অপরিচিত ও অপঠিত গদ্যগুলোতেও প্রকরণবিষয়ক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭৫ সালে ‘অশ্লীল জোৎস্নায়’ নামক এক সংকলনের সম্পাদকীয়তে নতুন রীতির লেখার প্রস্তাবনা হাজির করেছিলেন তিনি। নাম দিয়েছিলেন ‘উপলিকা’। কেমন হবে তার স্বভাব? রুদ্র লিখেছেন, ‘না কবিতা। না গল্প। সুরটা হবে কাবিতিক। এবং উপস্থাপনার ধরন হবে গাল্পিক। মূলত কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য গতি নিয়ে এর শুরু। এবং গদ্যের বিন্যাসে বিন্যস্ত। জটিলতা সবসময় পরিত্যাজ্য। যতোটা সম্ভব ধারাবাহিকতা আবশ্যক। সমাপ্তিটা ছোট গল্পের মতোন। সহজবোধ্য শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।’ উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ফরহাদ মজহারের কবিতার প্রসঙ্গ।
রুদ্র বাংলা কবিতার আধুনিকায়নের ইতিহাস সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিরিশের দশকের কবিতার সমালোচনা করেছেন। দুর্বোধ্যতা, পাঠকের সঙ্গে কবিতার দূরবর্তী যোগাযোগ তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্র অতিক্রমণের প্রয়াসটুকু বাদে বাংলা কবিতায় ‘উল্লেখযোগ্য সংযোজন’ ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন না। এ দশকের কবিতা সম্পর্কে অভিযোগ, ‘বিচ্ছিন্নতায় আড়ষ্ট, অতি সচেতনতায় সৃষ্ট উন্নাসিক, আসম্পূর্ণ এবং যোগাযোগরহিত, অহংমুখী।’ তাঁর পূর্ববর্তী ষাটের দশকের কবিতাও তাঁকে আনন্দের প্রণোদনা দেয়নি; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত এক দশকের কবিতা সংকলনের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘ষাটের কবিদের অধিকাংশই সচেতনতাহীন আবেগে মোহে জর্জরিত, আত্মকেন্দ্রিকতায় এবং ব্যক্তিক বিবর-বৃত্তে বিদ্যমান।’ ষাটের দশকের কবিতায় উত্থাপিত জীবনকে তাঁর মনে হয়, ‘এই জলবায়ু-ভূমি-ভূগোলের নয়।’
২
কবি ও কবিতার সমালোচনায় রুদ্র থেমে থাকেননি, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও সমালোচক হয়ে উঠেছেন তিনি। উনিশ শতকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দাঁড় করিয়েছেন কাঠগড়ায়। ১৯৭৮ সালে স্বরূপ অন্বেষা বইয়ের ভূমিকায় ধরা পড়ে রুদ্রের প্রখর ইতিহাস দৃষ্টি। এ লেখায় বলেছেন, ‘একটি জাতির বিকাশের যাত্রাপথে তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হয় তার জাতিসত্তা, তার ইতিহাস, তার সামাজিক শরীর কাঠামো, তার দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য—তার প্রেরণাময় ঐতিহ্য।’ [হক কথা]।
জাতি, জাতিসত্তা কিংবা জাতীয়তার পরিচয় খুঁজে ফেরা এক অর্থে আধুনিক মানুষের ইতিহাসেরই প্রাণভোমরা। রুদ্রও কড়া নেড়েছেন আত্মপরিচয়ের দরোজায়। তাঁর মনে হয়েছে, উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে ওঠা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল ‘ব্যাপক জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন, চরিত্রের দিক থেকে আপোসমুখী ও দোদুল্যমান।’ মার্কসবাদী চিন্তার পরিভাষা ব্যবহার করে রুদ্র লিখেছেন, ‘সর্বোপরি উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন সুবিধাভোগী শহরবাসী স্বার্থবাদী এই শ্রেণীর জন্ম হয়েছিলো রাজানুগত প্রভাবশালী শ্রেণী হিসেবে রাজস্বার্থ রক্ষার তাগিদে, কোনো-ক্রমেই জনাস্বার্থের সপক্ষে কাজ করবার জন্যে নয়।’ রুদ্র কথাগুলো বলেছেন মূলত কার্ল মার্কসের বইপুস্তকের বরাত দিয়েই।
বাঙালি মধ্যবিত্তবিষয়ক রুদ্রের এই ইতিহাস অধ্যয়ন অনৈতিহাসিক নয়। ঠিক নিশানায় আঘাত করেছেন তিনি। এবং যথাযথভাবেই বলেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভেতর দিয়ে এই শ্রেণির অঙ্কুরোদগম। এই শ্রেণিটি মূলত শহরবাসী; রুদ্রের কথামতো, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম ধরে এই শ্রেণি ‘আত্মসচেতনতার আস্বাদে আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের দুরূহ ও কণ্টকিত পথে যাত্রা করলো।’
রুদ্র বাংলা কবিতার আধুনিকায়নের ইতিহাস সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিরিশের দশকের কবিতার সমালোচনা করেছেন। দুর্বোধ্যতা, পাঠকের সঙ্গে কবিতার দূরবর্তী যোগাযোগ তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্র অতিক্রমণের প্রয়াসটুকু বাদে বাংলা কবিতায় ‘উল্লেখযোগ্য সংযোজন’ ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন না।
রুদ্রের মূল্যায়নে উঠে এসেছে বাংলার ইতিহাসের দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের অসম লড়াই, ৪৭-উত্তর পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্জন্ম, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অপঘাত—কোনোটিই বাদ পড়েনি তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে। জরুরি একটি মন্তব্য, ‘স্বাধীনতার সশস্ত্র-যুদ্ধ আমাদের সমাজ-কাঠামো, সমাজ-সম্পর্ক ও উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো রীতিনীতিকে ভেঙে দেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধ জেগে উঠতে পারেনি, বাঁধভাঙা জল লোকালয় জনপদকে বিনাশ করে এগিয়ে গেছে। আমাদের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা এই মূল্যবোধ গঠনের দায়-দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছেন।’ নিহিত কারণ কী?
রুদ্র লিখেছেন, ‘বিচ্ছিন্নতা’। উৎপাদিত পণ্য থেকে শ্রমিক, উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে কৃষক, প্রশাসনযন্ত্র থেকে সরকারি আমলা মূলত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু রুদ্র বিচ্ছিন্ন হতে চাননি কোনো কিছু থেকেই; দেশ জাতি জনতার সঙ্গে অবিরত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যেতে চেয়েছেন জীবনের গহন গভীরে। আর জীবন যেহেতু একরঙা নয়, জীবনের গায়ে যেহেতু মাখা থাকে অনেক রঙের আবির সেহেতু রুদ্রও জীবনকে স্পর্শ করে দেখেছেন নানা ভঙ্গিমায়।
৩
এ কথা বলা যাবে না যে, রুদ্র নিজে আমূলভাবে বদলে দিতে পেরেছেন কবিতা কিংবা জীবনকে। এমনও নয় যে, কয়েক দশকজুড়ে বাংলাদেশে আধুনিকতার যে ভাব বিস্তার ঘটেছে, তার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁকেও আলোড়িত হতে দেখি বিচ্ছিন্নতায়; তাঁকেও ঘিরে ধরে হতাশার কালো অন্ধকার। প্রেম, অভিমান, বিরহ বাঙালি মধ্যবিত্তের এই প্রিয় প্রসঙ্গগুলো তাঁরও কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বহুবার।
অবশ্য রুদ্র একাই অভিমানের কান্ডারি নন; শামসুর রাহমান, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহার মতো অনেকেই কবিতায় ভাসিয়ে দিয়েছেন অভিমানের খেয়া। কখনো কখনো হয়তোবা জীবনানন্দ দাশ কিংবা বুদ্ধদেব বসুকেও আমাদের মনে পড়বে। তারুণ্যে হয়তোবা প্রেমময় একটি উদ্ভ্রান্ত সময় ভর করেই থাকে; কেউ-ই তো আর জন্মপ্রাজ্ঞ, স্থিতাবেগ আর যুক্তিবাদী হয়ে জন্মান না। লাতিন প্রবাদে আছে, ‘যদি তুমি প্রাজ্ঞ হও, তো প্রেমিক হতে পারবে না, যদি প্রেমিক হও, তাহলে প্রাজ্ঞ হতে পারবে না।’ অতএব জীবনানন্দ দাশও বলতে পেরেছেন, ‘তুমি তা জানো না কিছু— না জানিলে,/ আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।’ আর রুদ্রও লিখতে পেরেছেন, ‘তুমি জানো নাই– আমি তো জানি,/ কতোটা গ্লানিতে এতো কথা নিয়ে এতো গান, এতো হাসি নিয়ে বুকে নিশ্চুপ হয়ে থাকি।’ ‘অভিমানের খেয়া’ ভাসতে ভাসতে রুদ্র বললেন, ‘অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোৎস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই।’ তুমুল এক অভিলাষের কবি হয়ে উঠেছিলেন রুদ্র; মন তাঁর বাসনায় বিদ্ধ। বেদনার পারাবাত ডিঙিয়ে বলেছেন, ‘বেদনার পায়ে চুমু খেয়ে বলি এইতো জীবন,/ এইতো মাধুরী...।’
১৯৭৯ থেকে ১৯৯০- এ সময়পর্বে প্রকাশিত সাতটি বইয়ে রুদ্র জীবনের বেদনা ও মাধুরীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রেম তাঁর মাধুরী, বেদনা তাঁর নিষ্প্রেম নৈঃসঙ্গ্য; সব কিছুর মর্মমূলে ঘা দেয় আর্থসামাজিক বাস্তবতা। ‘স্বর্নগ্রাম’, ‘হরিনপুরে’’র মতো কিছু আলোকিত ইউটোপিয়া বহন করেও তাঁকে ক্ষয়ে যেতে হয়। যে ফিরে পেতে চায় ‘স্বর্নগ্রাম’, ‘হরিনপুর’ হারিয়ে সে-ই বলে দেয় ‘যে পায় সে পেয়ে যায়—সকলে পায় না তারে।’’ তাহলে ব্যক্তির বেদনা নিয়ে কোথায় যাবে মানুষ? রুদ্র বলেন:
হারানো শিল্পের কাছে
হারানো প্রাণের কাছে প্রয়োজনে নতজানু হবো,
হারানো শিল্পীর কাছে পুনরায় নতজানু হবো।
এই ধুলো. ক্লান্তি. ভুল. জীর্ন দুঃখগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফিরে যাবো স্বর্নগ্রামে।।
প্রকৃতপক্ষে মর্ম বিস্তার করে রুদ্র দেখেছেন জীবনের গভীর তল। অপরাপর অনেক আধুনিকের মতো করে ঢুকে পড়েননি রোমান্টিকতার জড়সড় গহ্বরে। উপদ্রুত উপকূলের এই কবির গলায়ই ছিল অন্য সুরের গান। উচ্চকণ্ঠ রুদ্র শুনিয়েছেন, ‘আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,/ আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,/ ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে—এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?’ যে ভোলে ভুলুক, রুদ্র কিন্তু ভুলে যাননি; ১৯৭৭-এ সালে রাষ্ট্রযন্ত্রের মন্বন্তরে বসে বললেন, ‘স্বাধীনতা—একি তবে নষ্ট জন্ম?’ এই জিজ্ঞাসা বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের সামনে।
বোঝা গেল, রুদ্রের মুদ্রার এক পিঠে প্রেম, অন্য পিঠে প্রতিরোধ। যেমনটা বলা হয়ে থাকে নজরুলের প্রসঙ্গে, রুদ্রের ক্ষেত্রেও তা যেন সমানভাবে সত্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতগুলো সুস্পষ্টভাবে মেলে ধরে বলেছেন, ‘জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শুকুন’, ‘চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়’, ‘নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ’। উপদ্রুত উপকূল পরবর্তী ছয়টি কবিতার বইয়ে—মানুষের মানচিত্র, ছোবল, গল্প, দিয়েছিলে সকল আকাশ ও মৌলিক মুখোশ—একইভাবে বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের জীবনস্পন্দন। মানুষের মানচিত্র বইয়ে বহু মানুষের কণ্ঠস্বরের ভেতর দিয়ে রুদ্র চিনিয়ে দিয়েছেন বাংলার শোষণগ্রস্ত গ্রামীণ জনপদ। লোকপুরাণের অভ্যন্তর থেকে স্বপ্নবীজ নিয়ে রুদ্র বলেন:
জীবনের খেলা রাতে আজো ফুরোয় না সেই মহুয়ার পালা,
হোমরা বাইদ্যার রোষ ফেরে আজো মহুয়ার পেছন পেছন,
বিষের খঞ্জরে বেঁধে স্বপ্নবান জীবনের চাঁদ সদাগর—
বুকের খোয়াব নিয়ে জীবনের ঘোরতম আঁধারে পালাই...
৪
শ্রেণিশোষণ, অপমৃত্যু বাংলাদেশে কেউ চায়নি। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ এমন ছিল না পূর্ব বাংলার বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে। রাজনৈতিক ইশতেহারগুলোতেও ছিল না হত্যার প্রতিশ্রুতি। নিমেষেই পথচ্যুত হয়েছে বাংলাদেশ। মূলত ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকাঠামোর ছকে পরিচালিত হয়েছে রাষ্ট্র। অথচ পূর্ব বাংলা জনপদের মানুষের কাছে স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ ছিল বহুমাত্রিক। বাঙালি চেয়েছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তি; মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা বলতে যে ধরনের বিষয়বস্তু বুঝে থাকে—জাতীয় চেতনা, জাতি, গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, মানবতাবাদ—এই বিষয়গুলোও নিশ্চিতভাবেই ছিল। কিন্তু প্রার্থিত মুক্তি আসেনি, স্বাধীনতাও চলে গিয়েছে প্রতিপক্ষের করতলে।
রাজনৈতিক বাস্তবতার এই দশা তরুণ কবিদের প্রভাবিত করেছে। উদার মানবিকতাবাদ ও বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তরুণেরা প্রবহমান সময়কে বুঝতে চেয়েছেন। কারও কারও মধ্যে তৈরি হয়েছিল প্রতিরোধের ধারণা। রুদ্রকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিরোধী সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সরব হতে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জাতীয় কবিতা পরিষদের মতো সংগঠনের সঙ্গে রুদ্রের সম্পৃক্তি ছিল প্রতিরোধের প্রয়োজনে। সংগঠন দুটির আজকের পরিণতি যতোই হাস্য উৎপাদন করুক না কেন, অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রগতিবাদী ও পরিবর্তনকামী প্রেক্ষাপট নির্মাণের তাগিদ জোরদারভাবেই ছিল এ দুটি সংগঠনের মধ্যে। মূলত ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামক দুনিয়ায় সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে যাঁরাই বোঝাপড়া করে নিতে চেয়েছেন, তারাই কোনো-না-কোনোভাবে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন, শিল্প-সাহিত্যকে অভিজাতের কুটিরশিল্প থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন বহু মানুষের কাছে।
দৃষ্টান্ত হিসেবে নগুগি ওয়া থিউঙ্গোর কথা বলতে পারি। কেনিয়ার কামিরিথু নামের একটি গ্রামে ১৯৭৬ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন কামিরিথু কমিউনিটি এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার। কেন্দ্রটির লক্ষ্য ছিল কেনিয়ার ঐতিহ্যিক নাট্যধারার সঙ্গে পরিবর্তিত আধুনিক থিয়েটারের সংযোগ ঘটানো। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষের এই সংগঠনে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনেও এই ধাঁচ লক্ষ করা যাবে। তবে সাংস্কৃতিক জোট, জাতীয় কবিতা পরিষদ কিংবা গ্রাম থিয়েটার—কোনোটিই সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক সৃষ্টিশীলতাকে আধার ও আধেয়র বৈচিত্র্য দিয়ে ধরতে পারেনি। কিন্তু মানতেই হবে প্রতিটি সংগঠন প্রতিরোধী একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সেই প্রতিরোধ প্রধানত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে ঘিরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ করে তুলতে পারেনি এ দেশের শিল্প-সাহিত্যকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো। তবে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এসব সংগঠনের তৎপরতাকে উপেক্ষা করার সুযোগও নেই।
এখন প্রশ্ন হলো, রুদ্র, কবিতা ও সংগঠনের কী সম্পর্ক? জবাব এই, প্রতিরোধের চৈতন্য ব্যক্তি, শিল্পমাধ্যম ও সংগঠনকে এক করেছে। আমরা খেয়াল করতে পারি, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলের কবি লেখক শিল্পীরা নন্দনতত্ত্বের নিছক খেলায় মত্ত হননি, হন না। সময় ও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁরা তাল মেলান, সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের গোলাপি চিবুকেও তাঁরা এঁকে দেন চুমুর চিহ্ন; আর লেখায় আঁকায় বলতে থাকেন, সময় ভালো নেই, ইতিহাস ভালো নেই, বদল চাই, রূপান্তর চাই, ইন্তিফাদা চাই।
মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে রুদ্র যেন কবিতা দিয়ে ব্যক্তিগত একটি ইন্তিফাদা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। হয়তো তাই কবিতাকে বলতে পেরেছিলেন ‘আন্তঃমহাদেশী ক্ষেপণাস্ত্র’, ‘প্রতিরোধের হাতিয়ার’। শিল্পবিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে বলেছেন, ‘শিল্পের যে-কোনো শাখায় একপক্ষীয় কোনো ব্যাপার নেই। উৎপাদক ও গ্রহীতা এই দুই পক্ষের মধ্যে সব সময়ই একটি বোঝাবুঝির প্রয়োজন আছে এবং বোঝাবুঝির সুসমতার মাধ্যমেই এই শিল্প অগ্রগতি লাভ করে।’ সত্তরের দশকের বাংলাদেশে সামরিকায়ন, সংবিধানের কাটাছেঁড়া, ফ্যাসিবাদী শাসন, জাতীয়তাবাদ বিতর্ক, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার দেখে রুদ্রকেও বাজাতে হয়েছে রুদ্রবীণা। তাঁর একমাত্র কাব্যনাট্য বিষ বিরিক্ষের বীজের কথা বলা যায়; সাতটি পর্বে বিভক্ত নাটকটিতে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের একটি দশক প্রায় প্রতিচ্ছবির মতো—মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের দ্বন্দ্ব। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্র প্রতিরোধের মতাদর্শিক হাতিয়ার ছিল মার্কসবাদ। বিষ বিরিক্ষের বীজে গৌরব চরিত্রটি হয়ে উঠেছে তাঁর বাসনা পূর্তির মাধ্যম; ‘সমতামন্ত্রের কাছে সমর্পিত অস্ত্র আমার।’, ‘সাম্যমন্ত্রে উৎসর্গ করেছি আমি আমার জীবন।’
রুদ্র নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন কবিতার পথে। তারুণ্যের স্বপ্ন ও উচ্ছ্বাস, অপরিমিতি ও অসংযম তাঁর কবিতার দোসর। কিন্তু স্বপ্নের কাছে পরাজিত হয় সব। হাজার পাঠকের হৃদয়কাড়া খুব সহজ কথা নয়; স্বপ্নের করতালি দিয়ে পাঠককে চমকে দিয়েছেন তিনি; আর তাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমরা তাঁর কবিতাকে ফিরে ফিরে পাই। শুদ্ধ নন্দনতত্ত্ববাদীর যা-ই বলুন, শুদ্ধ হৃদয়বাদীর পক্ষে রুদ্রকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। হৃদয়বাদীদের কানে কানে রুদ্র চুপি চুপি বলে যান, ‘আমি সেই নতমুখ, পাথরের নিচের করুন বেদনার জল./ আমি সেই অভিমান—আমাকে গ্রহন করো।’ বাংলাদেশের ইতিহাস তাঁকে গ্রহণ করেছে।
সম্পাদকীয় নোট
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ লেখায় ‘ণ’ অক্ষরটি সচেতনভাবে পরিহার করেছিলেন। ‘ণ’ অক্ষরের ক্ষেত্রে তিনি ‘ন’ ব্যবহার করতেন। প্রকাশিত এই প্রবন্ধে রুদ্রের বানানকে অনুসরণ করা হয়েছে।


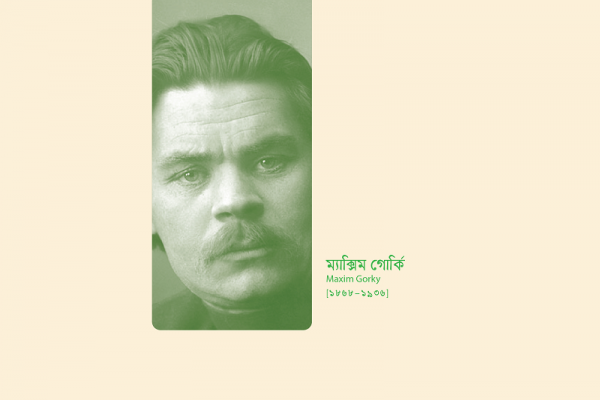

রুদ্রের রচনা-প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভালো লেগেছে। তবে, আজকের সময়ের(সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের) প্রেক্ষাপটে রুদ্রের কবিতা বা অন্যান্য রচনার আলোচনা হলে আরও ভালো লাগতো। আরও কিছু ভাববার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেত। ধন্যবাদ।
ঋতো আহমেদ
ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২২ ১৪:০৯