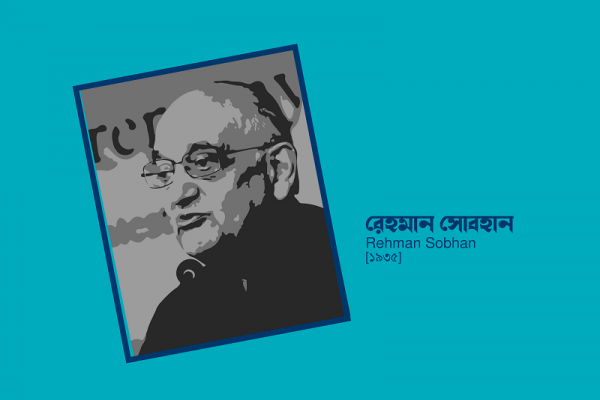
জীবন স্মৃতির বিনির্মাণ ‘উতল রোমন্থন’
এক
আত্মজীবনীতে বিকশিত মানুষের প্রকাশ ঘটে। সেই প্রকাশ মূলত নিজেকে জানা এবং জানানোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় গুরুত্ববাহী। নিজেকে জানা এই অর্থে যে, রোমন্থনের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে পেছনের ‘আমি’কে নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়। এই আত্মমূল্যায়নের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ঐতিহাসিক পারম্পর্যও সামনে আসে। যার সাপেক্ষে আত্মজীবনীকার নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুনভাবে নিরূপণ করতে পারেন। ‘Know thyself’—এর একটা লিখিত প্রক্রিয়ার মতো যার অনিবার্য পরিণতিকে শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে পারি আত্ম-আবিষ্কার। সেই আবিষ্কার ব্যক্তিতে নিঃশেষিত নয়। কেননা ব্যক্তিগত ‘আমি’কে জনসমক্ষে আনার ইচ্ছাতেই আত্মজীবনী লিখিত। ব্যক্তি তাঁর বিকশিত হবার পর্যায়গুলো বিভিন্ন ঘটনার আবর্তে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে প্রকাশ করেন বলেই আত্মজীবনীর অভিজ্ঞতাগুলো একটা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে উপনীত হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের উতল রোমন্থন এই ধারণার বিপরীতে নয়। নিজের জীবনের ব্যাপ্তিতে ইতিহাসের মহামহিম ঘটনাপঞ্জির সংস্পর্শে পাঠককে নিয়ে আসা তাঁর লক্ষ্য। ভূমিকাতে তিনি বলেছেন, ‘ইতিহাসের বিবরণ থেকে সরে এসে আমি শোনাতে চেয়েছি নিজের গল্প। এ বই লেখার ক্ষেত্রে ঘটনাগুলোর ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার গল্প এক সাধারণ মানুষের কাহিনী’।
কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে ব্যক্তিজীবনে তিনি হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের বরপুত্র। তাঁর বংশলতিকা আদি পুরুষ থেকে হালনাগাদ যে প্রজন্মে এসে ঠেকেছে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাষ্ট্রীয় উচ্চাসনে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিতকরণ, প্রতিভা ও মেধাশক্তির সদ্ব্যবহারে পদস্থ হবার গুণ, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক এবং পেশাগত জীবন ইত্যাকার বিষয় বিবেচনায় নিলে ব্যক্তি হিসেবে রেহমান সোবহানকেই শুধু নয়, এমনকি তাঁর পারিবারিক পারম্পর্যকেও ‘সাধারণ’ ভাববার কারণ নেই। তাঁর ‘সাধারণ মানুষের কাহিনি’ মূলত এক অসাধারণ রেহমান সোবহানকে উপস্থাপন করেছে। সেই অসাধারণত্ব বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে তাঁর অতুলনীয় কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে আলোকিত করে। সেই ভূমিকার কারণেই ‘পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে’ গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মি তাঁর বাড়ি তছনছ করে। কাজেই ‘সাধারণ মানুষের কাহিনী’র উল্লেখ মূলত তাঁর বিনয়ভাষণ। উতল রোমন্থন সত্যিকার অর্থেই কোনো সাহিত্যিক গল্প-কাহিনি নয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ের ঐতিহাসিক দলিল। এই স্মৃতিচারণার ব্যাপ্তিকাল লেখকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকাব্যিক অভ্যুদয়ের পর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাঁর স্বদেশ ফেরা অবধি বিস্তৃত।
দুই
লেখক তাঁর স্মৃতিচারণার অধ্যায়গুলো বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম এবং উপশিরোনামে ভাগ করেছেন বলে ধারাবাহিকতা বুঝতে সহজ হয়েছে। আবার যে কোনো অধ্যায় শুরু করলেই সেই অধ্যায়সংশ্লিষ্ট বিষয় পূর্বের ধারাবাহিকতা ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতে আসে। ফলে অনেকটা একাডেমিক আবহ ছড়ালেও পাঠকের জন্য সহজীকরণের পন্থা আবিষ্কারে লেখকের জন্য এটি একটি আঙ্গিকগত মুনশিয়ানা তো বটেই।
তাঁর বংশপরম্পরার আদি পুরুষ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রা:]। ১৯২৬ সালে তাঁর দাদা খোন্দকার ফজলুল হক সিদ্দিকীর লেখা একটি মনোগ্রাফ থেকে এই তথ্য জানান দেন লেখক। কিন্তু বংশগত আধ্যাত্মিকতায় জড়িত থাকার সেই পরম্পরা ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ভেঙে পড়ে। তাঁর দাদার চাচা দেওয়ান ফজলে রাব্বি বাংলার শেষ নবাব নাজিমের সঙ্গী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ১৮৬৯ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই খোন্দকার বংশের লোকেরা ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। আধুনিক নাগরিক হবার প্রচেষ্টাতেই তাঁর দাদা খোন্দকার ফজলুল হক ১৮৮৯ সালে স্নাতক হন। তিন মেয়াদে জেলা শাসকের পদে দায়িত্ব পালন করেন। যথাসময়ে তাঁকে খানবাহাদুর উপাধিও দেওয়া হয়। ঢাকার নবাব পরিবারের সঙ্গে লেখকের যোগসূত্রের উৎপত্তি তাঁর মা হাসমত আরা বেগমের মাধ্যমে। হাসমত আরা বেগম হলেন নবাব আহসানুল্লাহর কন্যা আলমাসি বানোর মেয়ে। আলমাসি বানো আবার নবাব সলিমুল্লাহর ভাগ্নি। আলমাসি বানোর দুই ভাইয়ের একজন খাজা নাজিমুদ্দীন। সেই সূত্রে খাজা নাজিমুদ্দিন লেখকের নানা। পরবর্তীকালে বাবা ও মা উভয়ের বংশপরম্পরা থেকে তাঁর পরিবার সরে যায়।
লেখকের নানার পরিবারের লোকদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গর্ব ছিল। কিন্তু পিতৃ ও মাতৃকুলের বংশগত গৌরব ক্রমশ ঔপনিবেশিক আভিজাত্যে রূপান্তরিত হয়। ফলে পরিবারের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল যে ব্যাহত হবে এটা স্বাভাবিক। তাই রেহমান সোবহানের স্মৃতিচারণাতেও তাঁর পরিবারের কারোর মধ্যে ধর্মাক্রান্ত মনোভাবের লক্ষণ বর্ণিত হয়নি; বরং সরাসরি বর্ণনা না থাকলেও একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর পরিবারের আধুনিক সেক্যুলার পরিবেশ তাঁর মনন গঠনের সহায়ক ছিল। ফলে তাঁর বাবার অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং পরবর্তীকালে তাঁর নিজের মধ্যে সেই চেতনার বিস্তার ঔপনিবেশিকতারই ইতিবাচক প্রভাব বলতে পারি। বিশ্লেষণের তাগিদেই হয়তো পাঠকের খেই হারাবার মতো পূর্বপুরুষের বহু নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝতে পারি বংশীয় আভিজাত্যে পরিতৃপ্তি আছে লেখকের। আবার সমালোচনাও আছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে ঢাকার নবাব পরিবারের ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনকে তখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় লেখক দূরদর্শিতা হিসেবে দেখেছেন। ফলে খাজা আব্দুল গণির ‘নাইট’ খেতাব এবং বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি লাভ। পরবর্তীকালে এই উপাধি ‘নবাব বাহাদুর’ উপাধিতে উন্নীত হয়। এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়ন ও নেতৃত্বদানে ঔপনিবেশিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত খেতাব ও উপাধি গ্রহণ সেই ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করেছে বলে ধারণা হয়। কাজেই লেখকের অভিমত অমূলক নয়। লেখকের বিশ্লেষণী অভিমত জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে দুটো মন্তব্যে:
পাকিস্তানের উত্থান এবং ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগ হওয়া—দুটো ঘটনায় প্রধান ক্ষয়ক্ষতির তালিকার একটি হয়ে যায় ঢাকা নবাব পরিবারের ঐশ্বর্য। [পৃ: ১০]
বহু বছর ধরে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার যে সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থেকেছে ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্যরা— বাংলা শেখার চেষ্টা করেনি অথবা যাদের মাঝে বসত সেই স্থানীয় জনসমষ্টির ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি—এগুলোই বিচ্ছিন্ন করেছে তাদের। এই বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়ে তোলে ক্রমে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠা মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের ইতিহাসগত ঘনিষ্ঠতা। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্যরা বাঙালিদের থেকে ভিন্নকূল হিসেবে বিবেচিত হয়। [পৃ:১]
এই বিশ্লেষণে স্মৃতিচারণা ডিঙিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পূর্ব ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৪৭-এর দেশভাগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং তৎপরবর্তী ইতিহাসের অভিমুখ হিসেবে এই গ্রন্থ তাই যথেষ্ট কার্যকর বলে মনে হয়।
তবে ‘বাংলা না-শেখার’ অদূরদর্শী প্রবণতা থেকে লেখক রেহমান সোবহান নিজেকে কতটা সরাতে পেরেছেন তা স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেননি। তাঁর নিজের বাংলা শেখা বা না-শেখার প্রেক্ষাপটও অনুল্লেখিত। অবশ্য বাংলা না জানার বিড়ম্বনা তাঁকে কীভাবে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল, পরবর্তী এক অধ্যায়ে তিনি সেই অকপট বর্ণনা দিয়েছেন।

রেহমান সোবহান © ছবি: ঢাকা অপেরা
তিন
ঔপনিবেশিক আমলে জন্ম নেওয়া এই মহারথী পাকিস্তান আমলে বিকশিত হয়েছেন। বাংলাদেশ আমলে তাঁর পূর্ণতার উপভোগ। তাঁর এই বর্ণাঢ্য জীবনে নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার কারণে রোমান্সের সুযোগ তাঁর খুব একটা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, পুরো গ্রন্থে নিজের মহীয়সী মা, সৎমা, স্ত্রী বা পারিবারিক পরিমণ্ডলের কয়েকজন ছাড়া আর কোনো নারী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি তিনি। স্ত্রী সালমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯৫৫ সালে। পরে বোন নাজকে চিঠির মাধ্যমে সালমা জানান রেহমান সোবহানকে তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, সালমার এই ধারণার উন্নতি ঘটে এবং তারা ১৯৬২ তে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। লন্ডনের ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেই বিয়ের কাবিননামায় সাক্ষী হিসেবে সই করেন তৎকালীন টোরি সরকারের পররাষ্ট্র সচিব স্যার অ্যালেক ডগলাস হোম, যিনি পরে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। এর আগে খ্যাতিমান ভাস্কর নভেরা আহমেদের সঙ্গে তাঁর স্বল্প সময়ের সম্পর্ক ঠিক রোমান্স পর্যায়ে গড়িয়েছিল কি না, বোঝা যায় না। তিনি জানাচ্ছেন, ‘ওর শৈল্পিক প্রকৃতির প্রতি আমি অনুভূতিহীন ছিলাম না, তবে আমি তখন আমার রাজনৈতিক পর্বে প্রবেশ করছি এবং আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের দুই পৃথিবী সর্বদাই দুই মেরুতে বিভাজিত থাকবে। ফলে যেটা হয়েছিল, আমাদের সম্পর্ক প্লেটোনিক স্তরেই থেকে যায়’। [পৃ: ১৯]
আমরা আঁচ করতে পারি রেহমান সোবহান তাঁর রাজনীতি, উচ্চ শিক্ষা, কূটনীতি এবং স্বল্পকালীন ব্যবসায়িক সাফল্যের পর্বেও একটা পরিশীলিত যাপন পদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন।
উতল রোমন্থন সত্যিকার অর্থেই কোনো সাহিত্যিক গল্প-কাহিনি নয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ের ঐতিহাসিক দলিল। এই স্মৃতিচারণার ব্যাপ্তিকাল লেখকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকাব্যিক অভ্যুদয়ের পর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাঁর স্বদেশ ফেরা অবধি বিস্তৃত
এই গ্রন্থের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যা লেখক প্রয়োজন বোধ করেননি, তা নিয়ে একটা বাড়তি শব্দও লেখেননি। আবার প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তিও করেছেন। তাঁর মা-বাবার বিবাহবিচ্ছেদের কারণ তাই আমাদের কাছে অস্পষ্ট। সম্ভবত লেখক নিজেও অস্পষ্ট ধারণা রাখেন বলেই এ বিষয়ে খুব অগ্রসর হননি। শুধু জানতে পারি, তাঁর মা-বাবার মধ্যে অমিল ছিল। তাঁরা ছিলেন বিপরীত মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। তাদের বিবাহবিচ্ছেদের সময় লেখকের বয়স মাত্র নয়। আর সাত বছর বয়স থেকে পনেরো বছর বয়স অবধি তাঁকে দার্জিলিংয়ের বোর্ডিং স্কুলে প্রায় বন্দিজীবন কাটাতে হয়। সেন্ট পল’স-এর অবরুদ্ধ জীবন তাই তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ইংরেজি কায়দায় পরিচালিত এই স্কুলের বাইরের ঠাট যা-ই থাকুক, ভিতরের ঠাসাঠাসি, অপর্যাপ্ত খাবারের ফলে সৃষ্ট অপুষ্টি এবং বাড়াবাড়ি রকমের কড়াকড়ি একটা অবদমিত বৈরী মানসিকতা তৈরি করেছিল লেখকের। তাই শৈশবের স্কুলজীবন তাঁর মনে একটা নিস্তরঙ্গ অভিঘাত নিয়ে টিকে ছিল। শীতকালে মাস তিনেকের ছুটি কাটাতে কলকাতায় চলে আসতেন। তিপ্পান্ন এলিয়ট রোডে মায়ের পিতৃগৃহে কাটানো ওই সময়টাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আনন্দের। তাই তাঁর অভিব্যক্তি: ‘আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে আমার শৈশব-স্মৃতিতে চির অমলিন রইবে বাড়িটা’ [পৃ:৩১]। তাঁর মনন গঠনে এ সময় কার্যকর ছিল বই পড়া এবং সিনেমা দেখা। মায়ের সিনেমা দেখার প্রবাদপ্রতিম ক্ষমতা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছেন লেখক। একথা স্বীকারের পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ‘তাঁর জীবনের এক অপরিবর্তিত অঙ্গ ছিল দুই পুত্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসা...ক্যাডবেরি, আইসক্রিম, সিনেমা ইত্যাদি ধরনের বহু রুচিকর বিষয়ের সাথে পরিচয় করে দিয়ে গেছেন আমাকে’ [পৃ: ১৭]। আরও এক চমকপ্রদ কথা লেখকের জবানিতে জানতে পারি আমরা। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে জাপানিরা দ্বিতীয় দফায় বোমা ফেলে। তখন কলকাতার লাইট হাউস হলে মায়ের সঙ্গে সকালের শোতে সিনেমা দেখছিলেন তিনি। শেষটুকু না দেখে উঠে আসবার পাত্রী ছিলেন না তাঁর মা। এই অধ্যায়গুলো লিখতে গিয়ে অসংখ্য সিনেমা, সিনেমার চরিত্র, উপন্যাস ও উপন্যাসের চরিত্রকে উদ্ধৃত করেছেন লেখক। তাঁর স্মৃতিশক্তির তারিফ করতেই হবে এ ক্ষেত্রে।
যেকোনো পাঠকের স্মৃতিচারণার এই অধ্যায়গুলো বড় প্রেরণাদায়ী। মা-বাবার বিচ্ছেদের পর দীর্ঘ সাতাশ বছর বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর খুব সামান্য সুযোগ লেখক পেয়েছেন। একটা ভগ্ন পরিবার থেকে উচ্চশিক্ষা এবং যোগ্যতার বলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন হয়ে দেশের কাজে নিবেদিত থাকা কেবলই দৈব কোনো ঘটনা নয়। সুদৃঢ় চেতনা এবং নিরঙ্কুশ কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়া তা অসম্ভব। লেখক এবং তাঁর সুযোগ্য ভাই ফারুক সোবহান মূলত বেড়ে উঠেছেন প্রায় পুরোটাই মায়ের পরিচর্যা ও দিকনির্দেশনায়। ফারুক সোবহান পরবর্তীকালে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং পররাষ্ট্রসচিব পদে কর্মরত ছিলেন। মা সম্পর্কে লেখক আরও জানান: ‘প্রাণপ্রাচুর্যময় ছিলেন তিনি। শিখলেন টেনিস খেলা, ঘোড়ায় চড়া, রোলার-স্কেটিং, প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ কলকাতার সক্রিয় সামাজিক জীবনের আমোদফুর্তি। তাঁর আমলের সেরা সুন্দরীদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন’। [পৃ: ১৬]
তবে সৌন্দর্যেই সেরা ছিলেন না এই মহীয়সী নারী, সেরা ছিলেন জীবনচৈতন্যেও। একই রকমের প্রাণবন্ততা নিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল, বক্সিং, হকি, টেনিস, সুইমিং, দৌড় ইত্যাকার খেলায় শৈশব থেকেই স্ব-উদ্যোগে জড়িয়ে ছিলেন লেখক। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫১-সালে প্রথম সারিতে মায়ের সঙ্গে বসে ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। অভিবাদন নিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এরপরেই এইচেসন স্কুলে ভর্তি হতে লাহোর বিমানে দুই ভাইকে তখন একাকী তুলে দেন মা। পরে অবশ্য মা-ও পাকিস্তান চলে আসেন। আবার পাকিস্তানে থাকাকালীন করাচি জিমখানা ক্লাবে ১৯৫৩ সাল বরণের প্রাক-নববর্ষ পার্টিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয় তাঁর। সঙ্গে ছিলেন লেখকের বাবা। সেখানেই তিনি দেখতে পান আরেক জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। অতঃপর ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক রেহমান সোবহানকে আমরা আবার কলকাতায় পাই। এবার তাঁর বন্ধু নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন। তাঁর গাড়িতে চড়ে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের তুখোড় ঐতিহাসিক রণজিত গুহ'র বাড়িতে অনিয়মিত আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ রকম কত কত গ্রেটের সঙ্গে যে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, সেসবের ইয়ত্তা নেই। হয়তো এই দেখাদেখি, কথার আদান-প্রদান অথবা বন্ধুত্বের গভীর সারবত্তাও তাঁর মনন গঠনের সহায়ক হয়ে থাকবে।
বিশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং তৎপরবর্তী সময়ের কলকাতা ও লাহোরের রাস্তাঘাট ও অবকাঠামোগত চালচিত্র খানিকটা বিশদে উঠে এসেছে তাঁর স্মৃতিকথায়। কলকাতা, লাহোর, আর ঢাকার জীবনধারা এক অনন্য মিথষ্ক্রিয়ায় তৈরি করেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা সর্বভারতীয় রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য ১৯৫৭ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় আগমনের আগে এখানে তিনি একবারই এসেছিলেন। সেটা ১৯৪৮ সালে তাঁর মায়ের সঙ্গে। খাজা নাজিমুদ্দিনের অতিথি হয়ে সেবার তাঁরা দুই ভাই ঢাকায় কাটিয়েছিলেন মাত্র মাসখানেক। প্রথম দিকের বর্ণনায় তাঁর স্মৃতি রোমন্থনের ‘উতল’ অংশটি প্রকটভাবে ধরা পড়ে না। কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি যখন রাজনীতি-সচেতন হচ্ছিলেন, তখনই মূলত শুরু হয় তাঁর জীবন ও যৌবনের উত্তাল মুহূর্তগুলো। এ পর্যন্ত বণর্নায় লেখক তাঁর নান্দনিক পরিচর্যা ঘনীভূত রেখেছেন বলে একটা সাহিত্যিক ঘরানা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা না জানার বিড়ম্বনা কাটিয়ে কবে কোথায় কীভাবে তিনি এই চমৎকার গতিশীল লেখার ভাষাটি আয়ত্ত করলেন, সেটা বর্ণিত না হওয়ায় পাঠকের ঔৎসুক্য অমীমাংসিত থেকে যায়।
চার
রেহমান সোবহানের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরও বেশি অবারিত হবার সুযোগ পায় তাঁর লন্ডন সফরের সময়। বাবার পরামর্শে চামড়ার ব্যবসায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্যেই তিনি বাষ্পচালিত জাহাজে লন্ডন পৌঁছান। সময়টা ছিল ৬ মার্চ ১৯৫৩, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরের দিন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গির এটিও একটি বিশেষ দিক যে, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কথার মধ্যে সেঁটে দিয়ে অতীত সময়টাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। শৈশবের বর্ণনায় যেমন সিনেমার কিংবা পঠিত বইয়ের চরিত্রের উপমায় শিল্পিত করেছেন বিভিন্ন অনুষঙ্গ। লন্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্য লেখকের প্রাথমিক আকুলতা জাগিয়ে তোলেন তাঁর ফুফাতো ভাই ড. কামাল হোসেন। কিন্তু সেন্ট পল’স-এর এক সহপাঠীর পিতা মির্জা হাসান ইস্পাহানির সঙ্গে আলাপচারিতা তাঁর সমস্ত উদ্যম চুপসে দেয়। মির্জা সাহেব তখন লন্ডনে পাকিস্তানি হাইকমিশনার। কেমব্রিজে ভর্তির প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ‘ইয়ং ম্যান, তোমার কেমব্রিজ পড়তে যাওয়ার থেকে সুচের চোখের মাঝ দিয়ে উট গলে যাওয়া সহজ’। [পৃ:১০]
মির্জা সাহেবের এই মন্তব্য বাঙালি প্রসঙ্গে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের একটা সাধারণ নেতিবাচক প্রবণতার প্রোজ্জ্বল প্রতীক। বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ বিষয় আরও স্পষ্ট করেছেন লেখক। কিন্তু সৎমা শওকত বেগমের বিচক্ষণ ও প্রেরণাদায়ী একটা বিপরীত উপদেশ তাঁকে শক্তি দিয়েছে বলে আজও তিনি কৃতজ্ঞ। সৎমা বলেন, ‘জীবনে কোনো আক্ষেপ রেখো না। কেমব্রিজ যেতেই যদি চাও, তবে যাও’। [পৃ: ১১]
বিকশিত মানুষের হাতেই আত্মজীবনী শোভা পায়। কিন্তু সেই বিকাশের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কোনো দৈব ঘটনার কবলে পড়ে মানুষ শিখরে আসীন হয়, এ ধারণা অমূলক। প্রয়োজন দৃঢ় সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ। দৈবের বদলে কিছু আন্তরিক মানুষের পরামর্শ ও সহযোগিতা। রেহমান সোবহানের জীবনচিত্রে এর সব কটির আত্মস্থ প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মতো।
লন্ডন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার শুরুর প্রেরণা হলেও কেমব্রিজেই তাঁর সেই দীক্ষা শিখর স্পর্শ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর বক্তব্য: ‘কেমব্রিজে তিন বছরের প্রভাবে আমার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির ছবিটা ফিরে দেখলে স্পষ্ট বুঝি এখানেই গড়েছিল আমার পটভূমি, আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং ঢাকায় জীবন গড়বার সিদ্ধান্ত। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার ভাবাদর্শগত ঝোঁকগুলোর একটা রাজনৈতিক ঘর দরকার যেখানে একটা নির্দিষ্ট জাতীয় এবং সামাজিক অনুষঙ্গে তাদের অর্থবহ প্রকাশ সম্ভব। আবিষ্কার করি যে বিশ্ববীক্ষায় আমি আনত বাঙালির মনোজগতে তা আরও তীব্র অনুরণিত। বাঙালি রাজনৈতিক, সামাজিক অবিচারের শিকার’। [পৃ: ১৩১]
এই উদ্ধৃতির অর্থ হলো বাঙালির পক্ষে তাঁর অবস্থান মূলত নিপীড়িতের সমর্থনে নিজেকে একনিষ্ঠ রাখা। চেতনার এই নৈতিক ভিত্তি এতটাই সুদৃঢ় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের সুপরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের যেকোনো কসমোপলিটান শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিতে চাননি। ঢাকার মতো মেট্রোপলিটান শহরে জীবন গড়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন এ যাবৎ। তবে কৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসে তিনি স্বীকার করেন চেতনার এই ভিত তাঁকে গড়ে দিয়েছে কেমব্রিজের মতো শিক্ষায়তন। তিনি বলেন, ‘ঠিক বলতে পারব না আমার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে কেমব্রিজ স্বয়ং কী করল! কেমব্রিজের পদ্ধতি উৎসাহ দিত সৃজনশীল জিজ্ঞাসাকে যেখানে বিদ্বান হবার চেয়ে মৌলিক হওয়া বেশি গুরুত্বের ছিল’। [পৃ:১৩২]
হয়তো অন্তর্গতভাবে এই প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন লালন করে বলেই বহু মহারথীর সঙ্গে বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ার সুযোগ দিয়েছিল এই কেমব্রিজ। যাদের মধ্যে রয়েছেন সে সময়ের সেরা উন্নয়ন অর্থনীতিবীদ পি টি বাওয়ার, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিন, নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানি পদার্থবিদ অধ্যাপক আবদুস সালাম, স্যার টমাস ব্যালো, জন রবিনসন, ই এম ফর্স্টারসহ বহুজন। আর ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্রদের ফোরাম ‘কেমব্রিজ মজলিশ’-এ সামাজিকতা বিনিময়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনার বন্দোবস্ত হতো। আয়োজন হতো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার। প্রথাগত উপমহাদেশীয় ছাত্ররাজনীতির বাইরে রুচিশীল রাজনৈতিক চেতনা গঠনে মজলিশের ভূমিকা আজকের দিনেও একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হতে পারে। অমর্ত্য সেন নিজেও এই মজলিশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রেহমান সোবহানের রাজনৈতিক চেতনার পরিণতি লাভে কেমব্রিজ মজলিশের অনিবার্য প্রভাব এই স্মৃতিচারণার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক সংযোজন। লেখকের ভাষায়, ‘জীবন তখন কানায় কানায় ভরা। নোয়েল আন্নান অথবা নিক্কি কালডোরের লেকচার উজ্জীবিত করছে; টিউটোরিয়ালে জোন রবিনসন উসকে দিচ্ছেন; আমাদের প্রসারিত মননচর্চার সুযোগ মিললেই অমর্ত্য, দীপঙ্কর, মাহবুব হক, জগদীশ ভাগবতী অথবা লাল জয়বর্ধনের সঙ্গে অফুরান তাত্ত্বিক মতবিনিময় চলেছে। আমি নিবিড় অধ্যয়ন করছি, খেলাধূলার চর্চা বজায় রেখেছি, রাজনীতির পাঠ নিচ্ছি মজলিশে অথবা ইউনিয়নের সান্ধ্য সভাগুলোয় অথবা কেমব্রিজের অসংখ্য রাজনৈতিক সমিতিগুলোয় ব্রিটিশ সমাজের সেরা মেধাদের ভাষণ শুনছি এমনকি মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কও করছি আমরা।’ [পৃ: ১২৪]
তার মানে গড়ে ওঠার জন্য শুধু অন্তর্মুখী মগ্ন যাপন পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয়। উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে সামাজিক মেলবন্ধন যদি সুস্থ ও রুচিকর পরিবেশ দেয়, তবে গড়ে ওঠার সাধনা আরও বেশি গণবিস্তারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু সেই সুযোগ সৃষ্টির কাণ্ডারির ভূমিকা নিতে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র শিক্ষাদর্শন থাকা জরুরি। আর সেই দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ ও নিষ্ঠা। ছাত্রদের শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যবহারের ফলে সেই উদ্যোগ ও নিষ্ঠার কবর রচনা শুরু হয় পাকিস্তানি শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই। যার সর্বগ্রাসী ও বিধ্বংসী ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে লেখকের এই স্মৃতিচারণা অনুপুঙ্খ বিবেচনায় নিলে কেমব্রিজের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা তুলনামূলক চিত্র সামনে আসে। পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠার বিমূর্ত উচ্চাশা নিয়ে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আসেন লেখক। পরবর্তীকালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেন তিনি। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট ছাত্রসংগঠন এনএসএফ কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো ঘটনার রাজসাক্ষী তিনি। যে ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক বমি করে দিয়েছিলেন। অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তাঁর ছাত্রতালিকার উজ্জ্বল নক্ষত্র যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এঁদের একজন হলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমেদ। অন্যজন মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যিনি ফখরুদ্দীন ক্যাবিনেটের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। আরও ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ড. ইউনূস সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো, ‘আমি একজন নোবেল লরিয়েটের শিক্ষক ছিলাম এই জানাটা সর্বদাই খুব সন্তোষজনক হলেও তাঁর জীবনে পরিবর্তন আনা আবক্র পথে কোনো প্রভাব ফেলেছি এমন দাবি আমি করতে পারি না’। [পৃ:১৮]
অর্থনীতি বিভাগকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির হালচাল বুঝতে উতল রোমন্থন একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ১৯৭১ সালে টিক্কা খানের সামরিক প্রশাসন লেখককে দেশদ্রোহী ঘোষণা করেছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর স্বপদে পুনর্বহাল হন।
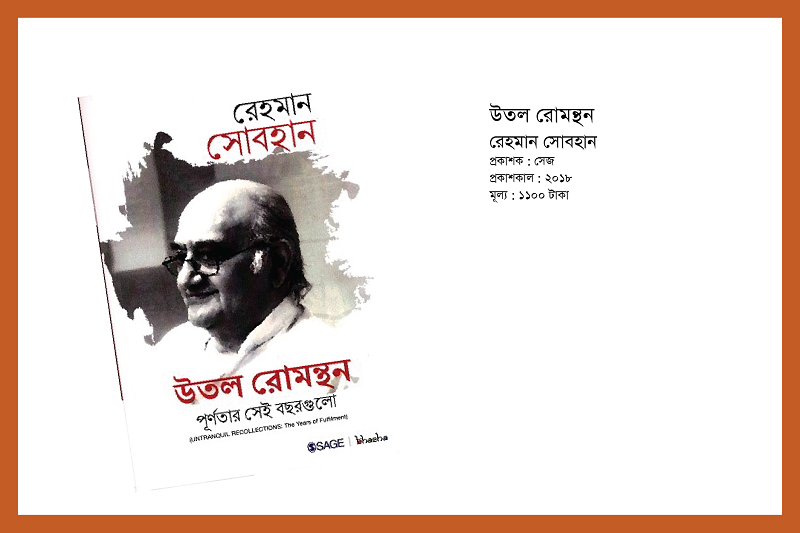
পাঁচ
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তাঁর রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা আরও বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। শিক্ষক হিসেবে যোগ দেবার আগেই রাজনীতিসম্পৃক্ত বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন তিনি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক উত্থান, মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ থেকে ভাগ হয়ে যাওয়া, ন্যাপের রাজনৈতিক গুরুত্ব সবই তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের সভাগৃহে উপস্থিত থেকে বক্তাদের আবেগঘন বাকপটু ভাষণ তিনি শুনেছেন আগ্রহসহকারে। ছয় দফার আগেই যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীন বিদেশ নীতির জোরালো দাবি ছিল। আওয়ামী লীগ পরিচালিত পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীরকে সেই গণদাবির প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে ভাসানী ও তাঁর অনুগামীরা জোরদার বক্তব্য দেন। ‘পূর্ব পাকিস্তানকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে’—সোহরাওয়ার্দীর এমন মন্তব্যের জেরে ভাসানী অসন্তুষ্টি নিয়ে দল ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে সম্বোধন করতেন ‘বস’ বলে। বসের কথায় খুশি না হলেও তাঁর প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শই দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।
বর্ণনার অকপটতা সত্ত্বেও একথা বলতে হয় যে, এই জায়গায় রেহমান সোবহান আরেকটু বিশ্লেষণী হতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন বিদেশ নীতির দাবি থেকে সোহরাওয়ার্দীর সরে আসার প্রেক্ষিত এবং হঠকারী মন্তব্যের গূঢ়ার্থ বিবেচনা রেহমান সোবহানের লেখায় নেই। প্রধানমন্ত্রী হবার পর ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে আসন পোক্ত রাখার কিছুটা ঝোঁক তাঁর মধ্যেও তৈরি হয়েছিল কি না, সোহরাওয়ার্দীর মন্তব্যের জের ধরে সেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল মনে করি। মওলানা ভাসানীর দাবি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ন্যায়নিষ্ঠ এবং যৌক্তিক ছিল। তবু কোন অমোঘ কৌশল কার্যকর ছিল বলে ভাসানী পরাজয় বরণ করেছিলেন, সে বিষয় খোলাসা হয়নি। পরবর্তীকালে ছয় দফার মূলমন্ত্র হিসেবে ওই দুই দাবিই তো সকল আন্দোলনের শক্তি জোগায়।
ভাসানীর পরাজয় নিজের চোখে দেখবার অভিজ্ঞতা রেহমান সোবহানকে রাজনীতি পর্যবেক্ষণের আরও সুযোগ করে দেয়। সেই সুযোগের একটি ছিল ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই রূপমহল সিনেমা হলে ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাবেশে উপস্থিত থাকা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেমব্রিজের সাংবাদিক বন্ধু হার্ভে স্টকউইন। সমাবেশের সংবাদ কভার করতে তিনি এ দেশে ছুটে এসেছিলেন। সমাবেশ ভণ্ডুল করতে পিকেটিংয়ে যথারীতি অংশ নিয়েছিল এনএসএফ। আশ্চর্যজনক হলো—আওয়ামী লীগের ছাত্র শাখা ইস্ট পাকিস্তান ছাত্রলীগের অনেককেই তিনি এনএসএফ-এর সঙ্গে দেখেছেন। সমাবেশ ভণ্ডুল করতে এনএসএফ-এর সঙ্গে ছাত্রলীগের এই উপস্থিতি কি রাজনৈতিক কৌশল নাকি নীতিভ্রষ্টতা, সে ব্যাপারে রেহমান সোবহান মন্তব্যরহিত। কিন্তু ভাসানীর সমাবেশবিরোধী জমায়েত নিয়ে যে চমকপ্রদ মন্তব্যটি তিনি করেছেন, তা-ও আগ্রহব্যঞ্জক। তিনি বলেন, ‘এই স্বল্পসংখ্যক জটলা নিয়ন্ত্রণ করছিল ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন [এনএসএফ]-এর প্রতিষ্ঠাতা খল-দর্শন এ আর ইউসুফ, মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ বলে যার খ্যাতি ছিল এবং সে গুপ্তচর সংস্থাগুলোর মদদ পেত। স্পষ্টতই এই জমায়েতের নাটের গুরু ছিল ইউসুফ। যদিও আমরা যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তখন উচ্চস্বরে ‘ভাসানী গুণ্ডা’, ‘ভাসানী ভারতের দালাল’ ইত্যাদি বলে বেশ জমকালো বক্তব্য রাখছিল মাহবুব রহমান নামের এক যুবক। এটা আমার স্মৃতিতে গেঁথে ছিল পরের পঞ্চাশ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক জীবনের অন্তিম পর্বে মওলানা যখন ভারতবিরোধী হয়ে উঠেছেন, তাঁর হক কথা পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু পরিচালিত আওয়ামী লীগ জমানাকে কঠোর নিন্দা করছেন ভারতপন্থী বলে, এই স্মৃতিগুলো তখন পরিহাস হয়ে ফিরছিল’। [পৃ: ১৬]
কেমব্রিজে থাকাকালীন সমাজতান্ত্রিক নীতির দিকে কিছুটা ঝোঁক ছিল লেখকের। তবে কমিউনিস্ট বিশ্বদর্শনের গোঁড়ামি নিয়ে প্রশ্নও করতেন তিনি। যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশে ফেরেন লেখক, তাঁর পরিপূরণে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কখনো দেখা যায়নি তাকে। আওয়ামী লীগের সদস্য হয়ে পদ-পদবির আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ধাতে ছিল না। ফলে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের কোনো খবর দিচ্ছে না তাঁর স্মৃতিচারণা। কাজেই তিনি না চাইলেও তাঁর উচ্চশিক্ষা, পেশাগত অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট থাকায় অর্জিত আভিজাত্য আম জনতা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই রেখেছে তাকে
ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে ছাত্রলীগকেও সমাবেশ ভণ্ডুলে একাকার করে দিয়েছিল, সেও এক পরিহাস হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। আয়ুব খানের সামরিক শাসন, মোনেম খানের অপতৎপরতা, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল, উনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থানসহ স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিস্পৃহ পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। আইয়ূব শাসনামলের দুর্নীতির চিত্র তখনকার স্বাধীন সংবাদমাধ্যমগুলোতে পাঠ করার ফলে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল লেখকের। ফলে আয়ূবের তথাকথিত ‘বেসিক ডেমোক্রেসি’ যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কূটকৌশল, তা সহজেই আঁচ করতে পারেন তিনি। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ ‘বেসিক ডেমোক্রেসিস, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান’ সেই অন্তর্দৃষ্টির ফলাফল। ছয় দফা ঘোষিত হবার অনেক আগে কার্জন হলের এক সেমিনারে আরও অনেকের সঙ্গে দুই অর্থনীতি বিষয়ে তারও একটি নিবন্ধ পঠিত হয়। পরের দিন অবজারভারের হেডলাইন ছিল—‘রেহমান সোবহান বলেছেন পাকিস্তানে বর্তমানে দুই অর্থনীতি বিদ্যমান’। আয়ুব আমলে এমন দুর্নামের ভাগীদার হওয়া শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, সাহসিকতারও ব্যাপার। ১৯৬৪ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারের খসড়া তৈরিতে পরামর্শের জন্য কামাল হোসেনের সঙ্গে রেহমান সোবহানও বঙ্গবন্ধুর ডাক পান। পরে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা লিপিবদ্ধকরণে তাঁর সক্রিয় সংযোগ তাকে সত্যিকার অর্থেই ইতিহাস সম্পৃক্ত করে তোলে। এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য হলো, ‘পরবর্তী বছরগুলোতে বিশেষত স্বাধীনতার পরে আমি ছয় দফার রচয়িতা আখ্যায়িত হয়ে অভিভূত হয়েছি। তবে সত্যি কথা হলো এ রকম কোনো দাবি আমি করতে পারি না, যদিও... সহযোগী অর্থনীতিকদের সঙ্গে ওই দলিলের বৌদ্ধিক উৎসে আমার কিছু অবদান ছিল’। [পৃ:২৫২]
ছয়
কেমব্রিজে থাকাকালীন সমাজতান্ত্রিক নীতির দিকে কিছুটা ঝোঁক ছিল লেখকের। তবে কমিউনিস্ট বিশ্বদর্শনের গোঁড়ামি নিয়ে প্রশ্নও করতেন তিনি। যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশে ফেরেন লেখক, তাঁর পরিপূরণে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কখনো দেখা যায়নি তাকে। আওয়ামী লীগের সদস্য হয়ে পদ-পদবির আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ধাতে ছিল না। ফলে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের কোনো খবর দিচ্ছে না তাঁর স্মৃতিচারণা। কাজেই তিনি না চাইলেও তাঁর উচ্চশিক্ষা, পেশাগত অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট থাকায় অর্জিত আভিজাত্য আম জনতা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই রেখেছে তাকে। আমাদের প্রথাগত ধারণায় রাজনীতি বরং জনসম্পৃক্ততা দাবি করে। তবু তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কেবলই ভাবগত বিমূর্ত অভিব্যক্তি মনে করা ঠিক হবে না। তাজউদ্দীনের নির্বাচনী প্রচরণায় ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। সে সময় বাম দলগুলোর ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু বাঙালি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তথা শ্রমজীবী মানুষের বিপুল সমর্থন তাঁকে যেভাবে আশা ও স্বপ্নের প্রতিমূর্তি করে তুলেছিল, তা বাম দলগুলোর ধারণার বিপরীত। আবার মনপুরার ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে তাজউদ্দীনেরও সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। এসব সফরে তাঁর নিজের ভূমিকা ছিল পর্যবেক্ষকের মতো। দুই নেতার সঙ্গ তাঁকে প্রশিক্ষিত করেছিল। তবু সবদিক বিবেচনায় রাজনীতিক হিসেবে তাঁর কাজ পুরোটাই প্রায় বুদ্ধিবৃত্তিক। আবার বুদ্ধিজীবিতার দিক থেকে তাঁর ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক। এ দুয়ের সমন্বয় তিনি করেছিলেন একজন বলিষ্ঠ কূটনীতিক হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর কূটনৈতিক যুদ্ধের যে খবর দিচ্ছে তাঁর স্মৃতিকথা তা এককথায় বিস্ময়কর। তাঁর আগে আইয়ুবের একনায়কতন্ত্রের জঘন্যতম পর্যায় কিছুকাল দর্শক হিসেবে অবলোকনের পর তিনি লন্ডন চলে যান। ফিরে আসেন উনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব শাসনের পতনের পর। লন্ডন ছাড়ার আগে ‘নিউ স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় নিবন্ধন লিখে তিনি জানান দিয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানা হলে এর পরিণতি স্বাধীনতাসংগ্রামে গড়াবে। তাঁর এই দূরদর্শী ইঙ্গিত ইতিহাস সত্য হিসেবে সাক্ষ্য দেয় আজ। ‘লন্ডন টাইমস’ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সহযোগিতায় ভুট্টোর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। ‘ভুট্টোর ঔদ্ধত্য, বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ কিন্তু নীতিহীন মনের পরিচয়’ তিনি পেয়েছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করায় তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ হয়েছিল।
সেই উত্তাল সময়ের অভিজ্ঞতা ধারণ করে ইতিহাসের এত এত আবর্তনকে তিনি সচল স্মৃতির রেখায় তুলে এনেছেন। মনে হয় সেই শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস একটা গ্রন্থবন্দী কালের পরিক্রমা। উতল রোমন্থন খুলে পড়লেই তা জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতার যে বর্ণনা ধারণ করছে, বইটি তা যেন একটা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প।

রেহমান সোবহান © ছবি: ঢাকা অপেরা
সাত
গল্পের পর্যালোচনার আগে কিছু বিষয়ের উল্লেখ জরুরি বোধ করছি। রেহমান সোবহান লিখেছেন, “একবার ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর উপলক্ষে ইয়াহিয়া ও স্থানীয় সম্পাদকদের এক বৈঠকে সাংবাদিক হিসেবে আমি আমন্ত্রিত হলাম; যেখানে আমি তাকে প্রশ্ন করি কেন তিনি একজন বাঙালিকে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ার পদে নিয়োগ করছেন না। ইয়াহিয়া বেরসিক ছিলেন না এবং ব্যঙ্গভরেই আমাকে পদটা নেবার প্রস্তাব দেন। আমি জবাবে বলেছিলাম, আমার পরামর্শ দরকার হলে ‘ফোরাম’-এর সাপ্তাহিক গ্রাহক মূল্যেই তা পেতে পারেন! শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসন ‘ফোরাম’-কে আমাদের প্রত্যাশার থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে তাদের গণহত্যা শুরুর আগে যে তিনটি কাগজ টিক্কা খান নিষিদ্ধ করে, তাঁর মধ্যে একটি ছিল ‘ফোরাম’।” [পৃ:২৭৭]
মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি বইটির সূত্র ধরে লারকানা চক্রান্তে ভুট্টোর ন্যক্কারজনক ভূমিকা সামনে নিয়ে আসেন রেহমান সোবহান। ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে ঢাকা ছাড়েন ইয়াহিয়া খান। লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর অতিথি হন। বঙ্গবন্ধুকে শায়েস্তা করার প্রসঙ্গে তাঁরা একাট্টা হন। সেই আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভুট্টো হুমকি দিলেন ছয় দফার ব্যাপারে আপোস রফায় রাজি না হলে ৩ মার্চ আইনসভার অধিবেশন তিনি বর্জন করবেন।
এ রকম আরও একটি ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন তিনি রাঘবন লিখিত ১৯৭১-এর সূত্র ধরে। খন্দকার মোশতাক সেই ষড়যন্ত্রের হোতা। রাঘবন তাঁর বইয়ে টেস্ট ডিপার্টমেন্টের ফাইল থেকে কাজী জহিরুল কাইয়ুম এবং কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার জর্জ গ্রিফিনের আলোচনার রিপোর্ট উদ্ধৃত করেন। কাজী জহিরুল মূলত মোশতাকের কাছের লোক। আর সেই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা। ভাগ্যক্রমে এই আলোচনার কথা ফাঁস হলে তাজউদ্দীন এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ করেন।
রেহমান সোবহান মনে করেন, ‘আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তারিখ যাই হয়ে থাক, সেটা বঙ্গবন্ধু করে থাকুন বা অন্য যে কেউ করে থাকুন, কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার তারিখ হওয়া উচিত ৫ মার্চ ১৯৭১, যেদিন বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ন্যাস্ত হয়েছিল। এই তারিখের পর, সামরিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের যে কোনো পদক্ষেপকে সমস্ত বাংলাদেশী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসন বলে মনে করেছে’। [পৃ:৩০২]
এই উদ্ধৃতি এবং ঘটনার উল্লেখ থেকে কিছু বিষয় আমরা বুঝে নিতে পারি, রেহমান সোবহান সরাসরি ইয়াহিয়া খানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বলে ‘ফোরাম’ নিষিদ্ধ হয়। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ভূমিকায় ভুট্টো এবং মোশতাকের মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্য ছিল। আর স্বাধীনতার দিন নির্ধারণে সূক্ষ্মদর্শী রেহমান সোবহান প্রচল মতের বাইরে নিজের বিশ্লেষণের অনুগামী হতে চেয়েছেন।
আট
২৫ মার্চ কালরাত্রির আগে বিকেল পাঁচটার মধ্যে লাহোর থেকে আসা মাজহার আলি খানকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩২ নম্বরে দেখা করেন রেহমান সোবহান। মাজহার এসেছেন সম্ভাব্য রক্তস্নান এড়াতে পিপিপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংযোগ স্থাপনের শেষ চেষ্টায়। বঙ্গবন্ধু ঘর খালি করে একাকী দু’জনের সঙ্গে আলাপ করেন। বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন তাঁর অর্থ হলো, তাঁর কবরের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। অতঃপর ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান আর্মি তাঁর ঢাকার বাড়ি আক্রমণের পূর্বেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে সরে পড়েছিলেন রেহমান সোবহান। ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে পলায়মান হাজারো জনতার স্রোতে মিশে গিয়েছিলেন। আগরতলা পৌঁছার আগ পর্যন্ত বহু অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হন তিনি। তাঁর বাংলা না জানা, ‘অবাঙালি’ চেহারা এবং ছদ্মবেশ ধারণ করার ফলে যে অদ্ভুত পোশাক তিনি পরেছিলেন, এসব নানা কারণে অনেকে তাঁকে পাকিস্তানের চর সাব্যস্ত করে। তাঁর বিপন্ন জীবন রক্ষা পায় তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ মুকতাদা তাঁকে শনাক্ত করার পর। আগরতলার পর তিনি দিল্লিতে পৌঁছান। এখানে বন্ধু অমর্ত্য সেনের সহযোগিতার পরও ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ লাভ অতটা সহজ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ২৫ মার্চের গণহত্যার বিষয়ে তখনো তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না। দিল্লিতেই তাজউদ্দীন এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং শুরু হয় তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত গঠনে তাঁর এই কূটনৈতিক ভূমিকা তাক লেগে যাবার মতো। ফলে বাংলাদেশের ফরেন ক্যাডারের তরুণ অফিসারদের জন্য এই বইটি ট্রেনিং ম্যানুয়ালের মতো শিক্ষণীয় অবদান রাখতে পারে। ভারতে বসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি অংশ নেন।
প্রথমত বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে ভূমিকা নিতে তাজউদ্দীনকে রাজি করানো। রেহমান সোবহান লেখেন, ‘আমার ধারণা সে সময় তাজউদ্দীনের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময়ে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র মূল্যবান মুহূর্তে আমার বিনম্র এবং অযাচিত ভূমিকা নিশ্চয়ই আমাকে অপ্রিয় করে থাকবে’। [পৃ: ৩৩৪]
দ্বিতীয়ত আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে মিলে তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দিলেন তাজউদ্দীন। ‘বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র’ এই ঘোষণায় ‘গণ’ শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর তাঁর পরামর্শেই সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ঘোষণাপত্রে। এই ঘোষণাপত্রেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথমে আওয়ামী লীগের আবদুল হান্নান এবং পরে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক সম্প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র হিসেবে সংযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর পরই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ দূত হিসেবে পাকিস্তানের যুদ্ধ-মিশনকে অর্থ জোগাবার যেকোনো প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দেওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তাঁর কূটনৈতিক ভ্রমণ শুরু হয়। সেই ভ্রমণের উপশিরোনাম দেখলেই তাঁর তৎপরতার ব্যাপ্তি বোঝা যায়। নানা উপশিরোনাম-সংবলিত লেখায় তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা, মনোবল ও আন্তরিকতার প্রমাণ মেলে। যার ফলাফল ছিল অভূতপূর্ব কূটনৈতিক সাফল্য। মুক্তিযুদ্ধের সার্থক পরিণতিতে যা আমাদের স্বাধীনতা লাভে পূর্ণতা পায়। সম্ভবত এ কারণেই উতল রোমন্থন বইটির উপশিরোনাম তিনি দিয়েছেন ‘পূর্ণতার সেই বছরগুলো’। পূর্ণতার সেই অলৌকিক অনুভব নিয়ে ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি দেশে ফেরেন।
রেহমান সোবহান লিখেছেন, ‘আমি এবং কামাল রাজনীতি বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছিলাম সোহরাওয়ার্দীর কাছে। ...পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় আমার রাজনীতি শিক্ষা দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছিল’ [পৃ: ২৪৪-২৪৫]। তিনি আরও লেখেন, ‘তাজউদ্দীনের সঙ্গে প্রতিটি বৈঠক আমার রাজনৈতিক শিক্ষাকে পরিণত করেছিল’ [পৃ:২৬৭]। আর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর আরও এক মন্তব্য হলো, ‘বঙ্গবন্ধুর সেরা গুণ ছিল মানুষের কাছে পৌঁছার ক্ষমতা এবং তাদের উপলব্ধ গুণাবলী তাঁর তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজে লাগানো’। [পৃ:২৬৮]
এভাবেই নিজের পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি কাজে লাগাতে লাগাতে তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়েছেন। ১৯৬৪ সালের মতো সত্তরের নির্বাচনের ইশতেহারও কামাল হোসেনের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করেন তিনি। সে সময় তাজউদ্দীন আহমদের নিবিড় পরামর্শে তাঁরা তৈরি করেন সেই ইশতেহার। কাজেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পরিক্রমার বড় ঘটনার সঙ্গেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জড়িত এবং সেই অর্থেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী এই দলটির ইতিহাসের অংশও তিনি। রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পেছনে যাঁরা বাংলাদেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, রেহমান সোবহান তাঁদের একজন। রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকা প্রকাশ্য, অনেকটা শরীরের যত্ন নেওয়ার মতো। তিনি পরিচর্যা দিয়েছেন আত্মার। তাই তাঁর প্রকাশ অতটা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু ইতিহাসের অনন্য সারবস্তু হিসেবে বিরাজমান।
যে পূর্ণতার অনুভব নিয়ে রেহমান সোবহান দেশে ফিরেছেন, সেই পূর্ণতার বিস্তৃতি এত বছর অতিক্রান্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে কত দূর গড়াল, সেসবের প্রাসঙ্গিক বিবেচনা সামান্য মন্তব্যে আরও বেশি করে তুলে আনা সম্ভব ছিল। যেমন তিনি বলেছেন, ‘১৯৬০ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে আমরা যেসব নিবন্ধ লিখেছি, বিভিন্ন সেমিনারে মন্ত্রী, বরিষ্ঠ আমলাদের সঙ্গে যেসব বিতর্কে জড়িয়েছি সেই সময়ের নিরিখে সেগুলো যথেষ্ট সাহসী ছিল। ওই ধরনের প্রয়াস আজকের স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশেও সামান্যই সহ্য করা হবে’। [পৃ: ২৩৫]
স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তান আমলের নিপীড়ন, বৈষম্যের নীতি, সামরিক শাসনের অত্যাচার, ত্রুটিপূর্ণ সাংবিধান, দ্বৈত নীতি, বাঙালির অধিকারহীনতা, ভোটাধিকার হরণ ইত্যাকার বিষয়ে যেকোনো অভিমত আজ বড় নিরাপদ গণ্ডি থেকে বলে দেওয়া সম্ভব। কেননা এ বিষয়ে কারোরই কোনো দ্বিমত নেই এবং রাষ্ট্রীয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কেউ সেই মতামত প্রদান ঠেকাতে আসবে না। সত্তরের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের প্রশংসা করেছেন রেহমান সোবহান। স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক শাসন এসেছে, এসেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন, উত্থিত হয়েছে বাকস্বাধীনতার প্রশ্ন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের সবলতা এবং দুর্বলতার প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিও উপেক্ষার নয়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে এসব ব্যাপারে একটা তুলনামূলক পাঠ নিতে পারত পাঠক তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে। রেহমান সোবহান প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন। হয়তো পরিসর বিবেচনায় সাম্প্রতিক এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিতে চাননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ গঠনে যেভাবে আত্মিক পরিচর্যা দিয়েছেন তিনি, একজন বর্ষীয়ান মহারথী হিসেবে বাংলাদেশ পর্বেও তাঁর দিকনির্দেশনা সেই পরিচর্যা দেবে বলে মনে করি। উতল রোমন্থন শুধু মুক্তিযুদ্ধের নিরাপদ আবেগের পরিপুষ্টি দেবে না, বরং হয়ে উঠবে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পথনির্দেশ, এটাই সবার কাম্য।
পরবর্তী সংস্করণে কিংবা ভিন্ন কোনো পুস্তিকায় লেখক এসব ব্যাপারে আলোকপাত করবেন কি না জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে নজর দেবার জোরালো দাবি রাখি। তা হলো বইটির বাড়াবাড়ি রকমের মুদ্রণ প্রমাদ। জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বলেই সব বিষয়ে একটু পরিশুদ্ধি পাবার অধিকার রাখে।


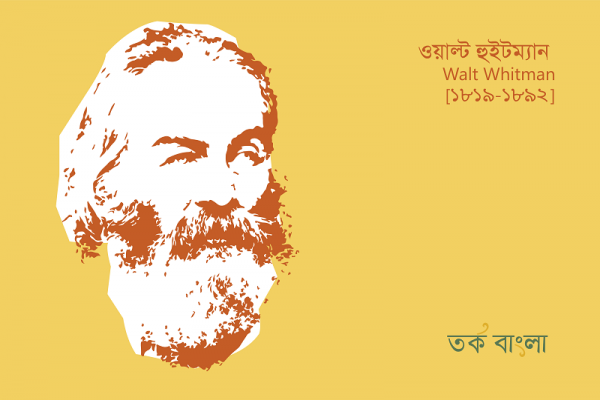

পর্যালোচানা দারুণ ছিল। গদ্য সাবলীল। তবে খুব না। উতল রোমন্থন পড়ার আ্গ্রহ জাগল আপনার রিভিউ থেকে। ধন্যবাদ।
umair mahbub
জানুয়ারি ০৫, ২০২২ ১৩:০৭