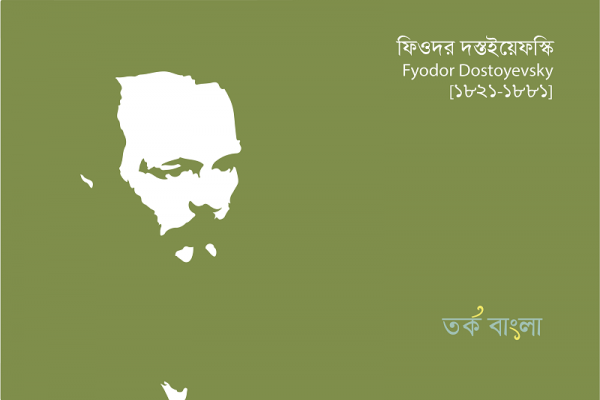কিংবদন্তি ‘টুকা কাহিনী’র বুলবুল চৌধুরী
বুলবুল চৌধুরীর মস্তিষ্কে গল্পের প্রথম প্রদাহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আরেক নির্বাসিত কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদ। হ্যাঁ, নির্বাসিতই তো! জীবন থেকে যে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন! সেটা ১৯৬৩ সাল। কে এল জুবিলী স্কুল। টাটকা টাটকা বেরিয়েছে স্কুল-বার্ষিকী। তারই এক পাতায় ‘চোর’ নামক গল্পের নিচে লেখকের নাম দেখে চমকে উঠলেন বুলবুল চৌধুরী। এ কোন কায়েস আহমেদ? তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিই কি? তাই তো মনে হচ্ছে। লেখকের নামের নিচে তো ক্লাস নাইনই লেখা। আশ্চর্য! কায়েস গল্প লিখল! ও জানল না? সারাক্ষণই তো দুজন একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে চলে! মানুষ এত কথা চেপে রাখতে পারে কীভাবে?
কায়েস আহমেদকে জিজ্ঞেস করতেই মুচকি হাসি মিলল। তখন বুলবুল নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন আর কথায় কথায় কায়েস আহমেদ ওকে বলেছিলেন, চেষ্টা করলে তুমিও তো গল্প লিখতে পারবে!
এই প্রথম কেউ ওকে বলল, চেষ্টা করলে গল্প লিখতে পারবে। লেখার ব্যাপারটা সূক্ষ্মভাবে ঢুকে গেল মাথায়। ওদিকে ক্লাস থ্রি থেকেই তো দুজন পুরান ঢাকার অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন। ক্লাস নাইন-টেনে এসে তা থিতু হলো আরমানিটোলা সরকারি পাঠাগারে নিয়মিত বইপড়া, মাঝেমধ্যে বাংলাবাজারের বইপাড়ায় ঢুঁ মারা—এমন সব সৃজনীবৃত্তে। কায়েস আহমেদের সুবাদেই পশ্চিমবঙ্গের নামকরা সব লেখকের বই তো পড়া হচ্ছেই। কায়েস আহমেদ নানা কথায় চোখ-কানও খুলে দিচ্ছেন, লিখতে হলে ভালো ভালো বই পড়তে হবে আর দেখারও চোখ থাকা চাই।
এর কয়েক বছর পর যখন বুলবুল জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, কায়েস আহমেদই একদিন নিয়ে গেলেন বিউটি বোর্ডিংয়ে। আর সেখানে প্রথম দিনই ঘনিষ্ঠতা হলো কবি আবুল হাসানের সঙ্গে। সেদিন কায়েস আড্ডা ছেড়ে চলে গেলেও বুলবুল রয়ে গিয়েছিলেন আবুল হাসানের কথার মায়াজালে। দুজন রাতের ঢাকা চষে বেড়িয়েছেন। তারপর শুরু হলো আবুল হাসানের সঙ্গে উরাধুরা আড্ডা আর বল্গাহারা ঘোরাঘুরি। হাসান ছিলেন জাত বোহেমিয়ান। নির্দিষ্ট থাকার জায়গা ছিল না। নতুন নতুন আস্তানায় জুটে যেতেন। আরমানিটোলায় ছিল জগন্নাথ কলেজের আবদুর রহমান হোস্টেল। বন্ধু দেলোয়ার মোর্শেদের আমন্ত্রণে আবুল হাসান এবং বুলবুল চৌধুরী সেখানে হাজির হতেন, কাটিয়ে দিতেন রাতের পর রাত। এ সময়ে এ ত্রয়ীর সঙ্গে আরও যুক্ত হন কবি মাকিদ হায়দার, গাজী আজিজুর রহমান।
আবুল হাসান তখন দেদারসে কবিতা লিখছেন। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলবুল চৌধুরীও একদিন লিখে ফেললেন, রঘুবংশীর বাংলা ঘর। আবুল হাসানকে দেখালেনও সে কবিতা। প্রশংসা জুটলেও বুলবুল চৌধুরী বুঝতে পারলেন, কবিতার কোমল সুগন্ধি জগৎ তাঁর নয়। ওদিকে কায়েস আহমেদের প্রেরণায় গদ্য লেখায়ও হাত মকশো করছিলেন চুপিচাপি একান্ত গোপনে। নিজের কাছেই তা সন্তোষজনক মনে হচ্ছিল না।
হলযাপনের এ সময়েই একদিন জগন্নাথ কলেজে শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ছাত্রদের কাছে চাওয়া হলো গল্প। গাজী আজিজুর রহমান বুলবুল চৌধুরীকে উসকে দিয়ে বললেন, আমি গল্প জমা দেব। তুমিও দাও।
আজিজুরের আমন্ত্রণ পেয়ে বুলবুল চৌধুরী এক রাতে লিখে ফেললেন ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’ নামের গল্পটি। দেলোয়ার মোর্শেদও সে গল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।
কদিন পর নোটিশ বোর্ডে নাম এলো। দেলোয়ার মোর্শেদ সে গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন, বুলবুল চৌধুরী দ্বিতীয় আর তৃতীয় হয়েছেন গাজী আজিজুর রহমান। সহপাঠীদের কাছে রাতারাতি লেখক হয়ে উঠলেন বুলবুল চৌধুরী। বাংলা বিভাগের শিক্ষক শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাহাত খান এবং শামসুজ্জামান খানের প্রশংসাও জুটল।
.jpg) বুলবুল চৌধুরী © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
বুলবুল চৌধুরী © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
২
‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’ আশ্চর্য পরিণত গল্প। পাঠমাত্রই বোঝা যায় গল্পকার যেন অনেক অনেক দিন ধরে ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিলেন। অন্তর্গত বোধ ও উপলব্ধির জায়গাটি সুগভীর থাকায়, একদিকে কায়েস আহমেদের সান্নিধ্যছায়ায় যেমন উপযুক্ত রুচিবোধ তৈরি হয়েছে, তেমনি কবি আবুল হাসানের বন্ধুত্ব পেয়ে লেখার উচ্চতাটুকু কেমন হতে পারে, তার যেন মাপকাঠিও পেয়ে গিয়েছিলেন। আর বাকিটুকু ভেতরের সহজাত ক্ষমতা ও লেখবার শক্তি। সব মিলিয়ে ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’ একটি শিল্পসফল গভীর জীবন উপলব্ধির গল্প।
ভেবে দেখুন তো! বিশ-একুশ বছরের এক যুবা তাঁর জীবনের প্রথম গল্পটি শুরু করেছেন ‘জোনাকি’ অনুষঙ্গ ব্যবহার করে এবং তা কতটা প্রাকৃতিক, গল্পটির সময়কাল ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে যাওয়া আর চরিত্রের সঙ্গে কী নিবিড় সংযুক্ত, ‘জানালার কাছে জোনাকিটা ঘুরে ঘুরে একসময় সেঁধিয়ে গেল। জিনাত ইচ্ছে করলে ওটাকে মুঠোয় আবদ্ধ করতে পারে, মেরে ফেলতে পারে, ছোট বোন মীনা জেগে থাকলে নিশ্চয় এতক্ষণে ওটার পিছু নিত। ঘুরে ঘুরে জোনাকিটা ধরে ফেলত—স্পর্শে স্পর্শে হয়তো অক্কাও পেত’...
এই যে জোনাকিটা—এ কে? একে মেরে ফেলার ব্যাপার আসছে কেন? এবং ছোট বোন মীনার হাতেও অক্কা পেতে পারত! এ রকম ভাবনা কি একটু অস্বাভাবিক নয়! হুঁম, অস্বাভাবিক তো বটেই, প্রকৃতিজাতও। জিনাত মনোবিকলনের শিকার। গল্পকারের বর্ণনা এগিয়ে চলেছে, ‘বাইরের বাতাস ঘন হচ্ছে। দূরের প্রবল বাতাস কিছু মিলিত কণ্ঠের কান্নার মতো বইতে থাকে।’ কেন এই বেদনাবোধের সমস্বর? আজ বিকেলেই যে মা সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, জাহিদ ভাই চলে যাচ্ছেন।
এ-জাহিদ ভাইকে ঘিরে যে ওর মনের মধ্যে প্রেম বোধই বলি বা কাম বাসনা একটু একটু করে গাঢ় হচ্ছিল। একদিন জাহিদ ভাই ওর হাত ধরেছিল চেপে। বলেছিল, তোর চুল কী জিনাত! সত্যি বিশ্বাস কর। সে মুহূর্তে ও পালিয়ে এসেছিল। আজ জিনাত, এ-রাতের অন্ধকারে যখন কিছুতেই ঘুম আসছে না, মনে মনে ভাবছে, সেদিন পালিয়ে না এলেই বুঝি ভালো ছিল!
গল্পকার জিনাতের মনের গতিপ্রকৃতিকে আবিষ্কারের জন্য উপস্থিত করেছেন জোনাকি অনুষঙ্গ। জোনাকি হলো দুরন্ত রিপুতাড়না। যা মনের গহন অন্ধকারলোকে জ্বলে আর নিভে। যা থেকে ছোট বোন মীনাও মুক্ত নয়। রাতটা যাক, দিনের আলোয় সবকিছু আরও স্পষ্ট হবে। মানব-মনের জটিল গ্রন্থিকে উন্মোচনের জন্য বুলবুল চৌধুরীর এমন ধারার প্রকৃতি-নির্ভরতা, শেষাবধি হয়ে উঠেছে তার ছোটগল্পের অনন্য এক শিল্পবৈশিষ্ট্য।
গল্পের পরের দিনে প্রবেশের আগে, এর আখ্যানের সঙ্গেও বোধ হয় পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে। ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’ গল্পটি গড়ে উঠেছে মফস্বল শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই উদ্ভিনা যুবতী বোনের মনোজগৎকে ঘিরে। যে-সময়ে গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৯৬৭ কী ৬৮ সালে, তখন মধ্যবিত্তের বাড়িতে ব্যাপকভাবে লজিং মাস্টার রাখার প্রচলন ছিল। এতে দু-তরফেরই লাভ। লজিং মাস্টার বিনা ভাড়ায় থাকতে পারছে, খাওয়াদাওয়া নিয়েও ভাবনার কিছু থাকছে না। আর বাড়িওয়ালার লাভ হলো, তার ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হচ্ছে না। সকাল-বিকেল লজিং মাস্টারের কাছে পড়ালেখার শিক্ষাটা হচ্ছে। তবে কী বলেন তো! মানুষ তো রক্তমাংসে গড়া। অধিকাংশ সময়ই দেখা যেত, লজিং মাস্টারের সঙ্গে বাড়ির কোনো মেয়ের মনোদৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সে রকম একটি ব্যাপারই ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র-’এ উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গল্পের সংকট তৈরি হয়েছে ঝাউতলি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে জাহিদের রাজশাহীর এক কলেজে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে। বেসরকারি কলেজ হওয়ায় এখানে সহজে ওর বেতন জোটে না।
সকালে ঘুম থেকে উঠে জিনাতকে জাগাল ছোট বোন মীনা। পরমুহূর্তে ও প্রশ্ন করল, তোর কি খেয়াল আছে, জাহিদ ভাই আজ চলে যাচ্ছে! তারপর প্রাতঃকৃত, চোখেমুখে পানি দেওয়া, রান্নাঘর। ইতিমধ্যে সকালের রোদ দুয়ারে। এক ফালি রোদ জিনাতের পিঠও ছুঁয়েছে। জাহিদের ঘরে জিনাত আজ নাশতা নিয়ে গেল না। ছোট বোনকে পাঠিয়ে দিল। রোদ ক্রমে প্রখর হতে থাকলে জাহিদের ঘরে ঢুকে জিনাত দেখল, নাশতা পড়ে আছে টেবিলে। জিনাতের রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল, কাঁদতে ইচ্ছে করল, এখনো যে নাশতা খাওনি? আমায় অপমান করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? জাহিদ বই বন্ধ করে আঁকড়ে রাখল দুহাতে, তোকে অপমান! সত্যি আমার মন ভালো নেই। যেতে হচ্ছে আমাকে!
অদ্ভুত এক অনুভবের গল্প। দু-বোনের। পুকুরে ডুব সেরে ভেজা চুল আর ভেজা কাপড়ে এসে জিনাতের সামনে দাঁড়াল মীনা। ও আজ স্কুলে যাবে না! কী সাধারণ সব ঘটনা অথচ কত সুগভীর!
তারপর একসময় সূর্য ডুবল। কান্নার আবেগ নিয়ে জিনাতের কাছে নেমে এলো রাত। রাত একসময় আরও গভীর হয়। মীনা জিনাতের কাঁধ ছুঁয়ে বলে, জিনাতবু! বাগানে কত জোনাকি উঠেছে! ধরবি যদি আয় আমার সঙ্গে। ফুল বাগানের দিকে জোনাকির ক্রমাগত জ্বলা-নেভার খেলা দেখতে দেখতে ও বলে উঠল, চল তবে।
আজ কিন্তু জোনাকি মারার কথাটা একবারও অনুভবে এলো না। জোনাকি মুঠোয় নেয় আর ছেড়ে দেয়। রিপুতাড়না নেই আজ, গল্পকার গল্প শেষ করেন এভাবে, জ্বলা-নেভার ক্রমান্বয় পরিক্রমণে জোনাকির ছোট পরিধির জীবনও অপরাজিত!
শেষটার মধ্যে একটু অস্পষ্টতা আছে না? এ-ও বুলবুল চৌধুরীর গল্পের এক স্ববৈশিষ্ট্য! পরবর্তী গল্পসমূহেও, বিশেষ করে ‘টুকা কাহিনী’-তে এ ধারা আরও সুস্পষ্ট হবে।
এই যে নারী প্রথম গল্পে যেভাবে এলো, তার সব স্পষ্টতা নিয়ে কামবাসনাসুদ্ধু, কোনো রকম বানোয়াট আবেগের ওপর ভিত্তি করে নয়, বাস্তবতার মর্মমূলের ওপর দাঁড়িয়ে—বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে ঋজু সংহত হয়ে, এর গাঢ় বিকাশও অব্যাহত থাকবে তাঁর পরবর্তী গল্পসমূহে। তাই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে গুনগুনাচ্ছে, আচ্ছা, এই যে প্রকৃতিকে নারীর ভেতরে এত গভীরভাবে সংলগ্ন করতে পেরেছেন প্রথম গল্পেই, এটা কি তিনি সচেতনভাবেই করেছিলেন, নাকি ভেতর থেকে আপনাআপনিই এসেছিল শিল্পের গাঢ় সংহিতা? মেলে না উত্তর!
.jpg) মাহবুব রেজা, শেখ আবদুল হাকিম, আবু সাঈদ জুবেরী, বুলবুল চৌধুরী ও ধ্রুব এষ © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
মাহবুব রেজা, শেখ আবদুল হাকিম, আবু সাঈদ জুবেরী, বুলবুল চৌধুরী ও ধ্রুব এষ © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
ঠিক এ প্রশ্ন তাঁকে করা হয়নি, তবে ‘জোনাকি এবং সন্নিকট কেন্দ্র’ নিয়ে খাপছাড়া গোছের আলোচনা তাঁর সঙ্গে আমার ঠিকই হয়েছিল। জানতে চেয়েছিলাম, বুলবুল ভাই, ও বয়সে নারীকে এতটা জীবন্ত কীভাবে তুলে আনতে পেরেছিলেন আর জোনাকির অনুষঙ্গটি কীভাবে আপনার গল্পে এত ন্যাচারালি প্রতীকায়িত হলো। বুলবুল ভাই যা বলেছিলেন, তা তো আর হুবহু বলা যাবে না। তবে যা মনে আছে জানানোটা প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে হয়।
হামিদ, আপনি তো জানেনই, আমার ছোটবেলাটা পুরাই দক্ষিণবাগে কেটেছে। পাখিডাকা গ্রাম ছিল, গাছগাছালিতে ভরা। দিনে ফড়িং উড়ত রাতে জোনাকি। কত যে জোনাকির মেলা দেখেছি। নানির ঘরে ঘুমিয়ে পড়তাম হাস্নুহেনার ঘ্রাণে। আর এ গল্প লেখার আগে নারী অভিজ্ঞতা তো আমার হয়েছেই। তবে এ গল্পের জিনাতের মধ্যে হয়তো পদ্মাপাড়ের জাহাজঘাটার মিনারা-বুর প্রভাব কিছুটা পড়লেও পড়তে পারে।
মিনারা-বুর পরিচয় সেদিনই জানতে পারি, ১৯৫৭ সালে ঢাকায় আসার আগে বুলবুল চৌধুরীর বাবা আবদুল মতিন চৌধুরীর চাকরিসূত্রে তাঁরা কিছুদিন গোয়ালন্দের জাহাজঘাটায় ছিলেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল পাকা দালানকোঠার কোয়ার্টার। সেখানে বুলবুল চৌধুরীর মা সুফিয়া বেগম চৌধুরী, গায়িকা হিসেবে বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গান শোনার জন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা ভিড় জমাত। পাশের বাড়ির মিনারা-বু আসতেন সে সূত্র ধরেই। তিনি সুফিয়া বেগমের কাছে গান শিখতে চাইতেন। মা তো বটেই, বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গেও বেশ সখ্য জন্মেছিল। বুলবুল চৌধুরী বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলেন মিনারা-বুর। সে অনেক গল্প।
এর পরেই লিখেছিলেন ‘সমূহ অনুভব’ গল্পটি। এখানে আরেকটি তথ্য দেওয়া প্রয়োজন যে, তখন দেলোয়ার মোর্শেদ, গাজী আজিজুর রহমান—সবাই মিলে ‘সবাক’ নামের একটি ছোট কাগজ বের করেছিলেন। সবাক সম্পাদনা করেছেন বুলবুল চৌধুরী নিজেই। সবাকেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’। এরপর ‘সমূহ অনুভব’সহ আরও একটি গল্প লিখেছিলেন। সে গল্পটি সম্ভবত গ্রন্থভুক্ত হয়নি বা হলেও জানা নেই আমার।
‘সমূহ অনুভব’ গল্পটি ‘জোনাকি ও সন্নিকট কেন্দ্র’ থেকে পুরোই আলাদা ধাঁচের। এ গল্পে যেন লেখক নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। পাপপুণ্যির ভেদ-অভেদ ঘোচাতে চেয়েছেন। যতবার আমি ‘সমূহ অনুভব’ পড়েছি, ততবারই কেন যেন শামসুর রাহমানের ‘দুঃসময়ে মুখোমুখি’ কবিতাটি মনে পড়েছে—
বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও, চলে যা সেখানে...
... এখন এই তো আমি, ব্যস্ত অবসন্ন, বিশ্রামের
নেই মহলত।
উজাড় মাইফেলের প্রেত ঘুরি হা-হা বারান্দায়।
এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়
জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনো-বা
আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর
স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি
গৃহিণীকে। আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস, না রে?
এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধু-ধু অন্তরালে চলে গেছে। তুইও যা, চলে যা।
একটা কথা তো ঘোর সত্য, ষাটের দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক যে সাহিত্যচর্চা হয়, তাদের সামনে ছিল কল্লোল যুগের লেখক; আর তারা ইউরোপীয় মানসকেই প্রতিফলিত করে যাচ্ছিলেন। ইউরোপের কবিসাহিত্যিকদের সাহিত্য তো বটেই, তাদের জীবনাচরণও এ দেশের কবি-লেখকদের আকৃষ্ট করত। বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ার অনুবাদ করছেন, আমেরিকা সফর শেষে ফিরে এসে লিখছেন হাউলখ্যাত অ্যালেন গিন্সবার্গের গাঁজা খাওয়ার অভিজ্ঞতা। নৈরাজ্যকেও অনেকে শিল্পের বান্ধবে সংযুক্ত করে নিলেন। আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ যেমন জাত কবি, বুলবুল চৌধুরীও তেমনি জাত কথাশিল্পী। কিন্তু তাঁরাও যে ইউরোপীয় কবি-শিল্পীদের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলাই বাহুল্য। সুখের কথা এই যে, জীবনাচরণে সে প্রভাব পড়লেও নিজেদের সাহিত্যকর্মে যেন তারা খুঁজে চলছিলেন নিজস্ব স্বকীয়তা। সে কারণেই আবুল হাসানের কবিতাগুলো যেমন পাথরের লাবণ্যে চিরকালের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে, বুলবুল চৌধুরীর গল্পগুলোও বাংলার মাটি বাংলার জলের ফসল হিসেবেই আদৃত হবে বহুকাল।
‘সমুহ অনুভব’ গল্পে তার ব্যক্তিসত্তা যেন শিল্পীসত্তার মুখোমুখি হয়েছে। জিয়াউল হক নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে গল্পের শরীর। আমরা আস্তে আস্তে সেখানে নানান চরিত্রের উপস্থিতি পাই। পাই প্রকৃতিকেও—
দরজা খুলেই দাও না, অন্তত কিছু আলো আসবে।
বিজলী আঁতকে উঠেছে, না, না, বৃষ্টিতে ভিজে যাব যে!
সেই মুহূর্তে তুমি চরম বাণটা নিক্ষেপ করলে, কিন্তু দরজা না খুললে যে আমরা ভিজে যাব।
ও নিশ্চুপ। বাইরে বৃষ্টি।
বাইরে বৃষ্টি। ভেতরেও বৃষ্টি।
ঘটনাটা হলো জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিজামের বাসায় অবাধে যাওয়া-আসা করত জিয়াউল হক। একদিন বাসায় আর কেউ না থাকার সুযোগে গভীর মেলামেশা হয়ে যায় দুজনের। কয়েক মাস পর নিজাম বাসায় এসে ক্ষোভ ঝাড়ে, তুই বিজলীর সর্বনাশ কেন করলি জিয়া?
অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ প্রেমিকা রোকেয়ার কাছে জিয়া একজন সাধুসন্ত পুরুষ। নিজের আলোক সত্তা আর অন্ধকার সত্তাকে মুখোমুখি করে এবং পাপ ও পুণ্যর বিশ্লেষণ খুঁড়তে খুঁড়তে একটি দার্শনিক উপলব্ধির সামনে আমাদের পৌঁছে দেন গল্পকার, পৌঁছেই ছেড়ে দেন, চাপিয়ে দেন না কোনো কিছু।
.jpg) নাসের মাহমুদ, বুলবুল চৌধুরী ও ধ্রুব এষ © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
নাসের মাহমুদ, বুলবুল চৌধুরী ও ধ্রুব এষ © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
৩
মুক্তিযুদ্ধের বিজয় আমাদের শিল্প-সাহিত্য জগৎকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছিল নিঃসন্দেহে। আমরা যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি আমাদের সংগীত, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক, টেলিভিশন নাটক, কথাশিল্প, কবিতা, চিত্রকলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কাজ হতে থাকে। এ ধারা মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ বছরকালব্যাপী বেশ ফলবান ছিল। তারপর যেন ক্রমশ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের তোড়ে হোক বা সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের ফেরে; সে ধারা আর বেগবান থাকেনি, বরং পথই যেন হারিয়ে ফেলেছে পুরো।
যাহোক, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালীন সেই সৃষ্টিশীলতার জোয়ারের ধারাস্রোতে বুলবুল চৌধুরীও নিজের প্রতিভাগুণেই বাংলাদেশের ছোটগল্পের জগৎকে আমূল নাড়িয়ে দিলেন ‘টুকা কাহিনী’ লিখে। ১৯৭২ সালে আবুল হাসনাত সম্পাদিত গণসাহিত্য পত্রিকায় ‘টুকা কাহিনী’ প্রকাশের পরই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে।
কী আছে এই ‘টুকা কাহিনী’ গল্পে? কেন তিনি সে গল্প লিখে রাতারাতি পৌঁছালেন খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে? অনেক আগে পড়া গল্পটি আলোচনার স্বার্থে আরও একবার পড়লাম। বলতে দ্বিধা নেই, টুকার মতো অনন্য চরিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব কমই এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচু লেখকের মতোই লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে সমান পরিচিত, টুকাও তাই। বুলবুল চৌধুরীকে লোকজন শনাক্ত করে এভাবে, ওহহ্? সেই টুকা কাহিনীর?
টুকা যেন এক ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি। মানুষের বাড়ি কামলা দিয়ে খায়। বিধাতা ওকে প্রায় কিছুই দেয়নি—না শরীর, না স্বাস্থ্য, না চেহারা। লেখকের বর্ণনায়, ‘খাঁটো মানুষ সে, মাথার চুল যথাসম্ভব ছোট ছোট করে ছাঁটা—তার গোলগাল মুখ সব সময়ই তেল চকচকে দেখায়। আর ফোলা-ফাঁপা পেট-টুকার পেট এ রকমই থাকে, সেরেক চালের ভাত খেলে, দুদিন অভুক্ত থাকলেও। যদি আলো-আঁধারি কোথাও গাঁট মেরে বসে থাকে, তাহলে মানুষ বলে ঠাহর করা সম্ভব নয়। ঠাহর হয়, কেউ গোবর-পচা বা কোনো আবর্জনা কোদালে কুপিয়ে পাতিতে বয়ে এনে দু-এক পাতি ফেলে রেখেছে।’
টুকা স্বভাবেও জানি কেমন। কুইচ্চা খায়। গ্রামের লোক যেটিকে মাছই মনে করে না, ফেলে দেয়, সেটাই ও খায় মজা করে। নিজের রান্নাটুকু নিজেকেই সারতে হয় ওর। মাঝেমধ্যে ভাই একুবের বউ আয়মুনা রেঁধে দেয়, তরকারিও দেয়। বিয়ে একটা করেছিল বটে, গ্রামের লোকজন ওকে ডাকত টুকিনি। অভ্যাস বড় খারাপ ছিল বউটার। সুযোগ পেলেই এটা-সেটা চুরি করত। একদিন মানইজ্জত বিসর্জন যাওয়ায় বউটাকে ও এমনভাবে পিটাল যে, পরদিন ঘুম থেকে জেগে দেখে নেই, পালিয়েছে!
বিধাতা ওকে বাবা দিয়েছিল একটা, দেখতে যেমন বদ, আচার-আচরণেও খবিস। মাকে যে কী নিষ্ঠুরভাবে পেটাত। অথচ মা ছিল দেখতে সুন্দরী এবং গুণবতী। সে কারণেই সংসারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নায়েব সালিসে বাবার কাছ থেকে মাকে তালাক দেওয়াল। আর নিজের জিম্মায় নিয়ে নিল কদিন পর বিয়ে করে।
কোন্ কালে বাপ মরেছে, মাও নায়েবের সঙ্গে গিয়ে খুব বেশি দিন বাঁচেনি, তবে নায়েবের প্রতি সেই যে ক্ষোভ জন্মেছিল টুকার, সেটা ওর কোনোকালে মরল না। মায়ের অভাব অনুভব করে অহর্নিশ। সে যন্ত্রণার কারণেই একদিন নায়েবের ঘোড়াটাকে নির্জনে বাগে পেয়ে কোঁচ বসিয়ে দেয় বেমক্কা। ঘোড়াটা মরে যায়। সন্ধ্যায় কুয়োতলায় ঘোড়াটার বাচ্চা বুঝি মাকে খুঁজে বেড়ায়। টুকা এগোয় সেদিকে। ঘোড়ার বাচ্চা ওর দিকে এগিয়ে আসে। বাচ্চাটার জন্য ভারি মায়া লাগে টুকার। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। ও ঘোড়ার বাচ্চাটাকে নিয়ে ছুটে যায় নায়েবের বাড়ি। নায়েব ঘোড়ার বাচ্চা পেয়ে প্রথমে খুব খুশি হয়। কিন্তু টুকার ভেতরের শুভ সত্তা যখন নায়েবকে নিজের অজান্তেই জানিয়ে বসে যে, ঘোড়াটাকে ও-ই মেরেছে! তখন নায়েব ওর মুখে তীব্র জোরে লাথি মেরে বসে।
তারপর? তারপর কী হয়?
অস্পষ্ট এক গোলকধাঁধা তৈরি করে রাখেন গল্পকার বুলবুল চৌধুরী। আমার কাছে তাঁর এ প্রবণতাকে যথাযথ মনে হয়। সত্যজিৎ রায়কে তাঁর কোনো এক চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শোতে এক দর্শক জিজ্ঞেস করে বসেন, এই শেষ দৃশ্যটায় আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? সত্যজিৎ উলটো তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কী বুঝেছেন? দর্শক তার নিজের ব্যাখ্যা জানায়। সত্যজিৎ তখন বলেন, আমিও এটাই বোঝাতে চেয়েছি। তখন পাশ থেকে আরেকজন দর্শক ভিন্ন এক অবলোকন তুলে ধরে বলেন, আমি তো ভেবেছিলাম এমন হবে। সত্যজিৎ তখন তাকেও উৎসাহিত করলেন, আমি এটাও বোঝাতে চেয়েছি। আপনি ঠিকই বুঝেছেন।
তখন আরেকজন প্রশ্ন করলেন, আমরা কোনটা ঠিক ধরে নেব? সত্যজিৎ রায় তখন বোঝালেন, যখন কোনো শিল্প বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করতে পারে, তখনই সেটা সার্থক। একেকজনের কাছে তা ভিন্ন অর্থ নিয়ে ধরা দেয়। বুলবুল চৌধুরীর গল্পের শেষটা অধিকাংশ সময়ই বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করতে সক্ষম হয়। টুকা কাহিনীর শেষাংশই যদি দেখি—
‘ফুলের গন্ধ আছে বাগানে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে টুকা। কনুইয়ে শরীরের ভর। শীত আসে কোথ্ থেকে? এখন ত শীতের সময় না। ঠক ঠক কাঁপুনিতে সে ঘোলা দেখে সব।... টুকা উঠতে চাইল। পারল না। শুনতে চাইল। শুনল না। ফালি চাঁদ ছিল আকাশে। তাও কি আছে?’
একটা বিভ্রমের মধ্যে আপনাকে রেখে দেওয়া কিংবা সিদ্ধান্তটা আপনার ওপরই ছেড়ে দেওয়া, টুকার কী হলো, নিজের মতো ভেবে নেওয়ার অবকাশ। তবে আমি কোনোভাবেই চাইব না, কেউ ভাবুক টুকার মরণ হয়েছে, টুকাকে মেরে ফেললে কিন্তু টুকা কাহিনী গল্পেরও মরণ হবে। আর বুলবুল চৌধুরী নিজেও তো সে-রকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি, ব্যাপারটা ধোঁয়াশা রেখেছেন, অস্পষ্ট করেছেন, সে কারণেই তো টুকা কাহিনী বাংলা সাহিত্যের সেরা ১০০ গল্পের মধ্যে একটি হওয়ার দাবি রাখে।
টুকা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে থাকে, নিড়ানির দরকার হয় না, তবু মাটি খুঁটে বেড়ায়, সব সময় নিড়ানি হাতেই থাকে ওর। প্রকৃতিসংলগ্নতা, প্রতিবাদী সত্তা আর মানবিক বোধ—সব নিয়েই টুকা বাংলা সাহিত্যের অনন্য চরিত্র। তবে শুধু টুকা চরিত্রের জন্য নয়, টুকা কাহিনী গল্পে বুলবুল চৌধুরী গ্রামকে যেভাবে আমূল শিকড়সুদ্ধু তুলে এনেছেন, তা বাংলাদেশের আর কজন লেখক পেরেছেন, সন্দেহ আছে! ‘এ অঞ্চলে আষাঢ়-শ্রাবণে কাজ থাকে না’, ‘সজারুটা মানুষের মাচানের কুমড়ো কাটছে, ঢেঁড়স গাছের ডগা কাটছে, বেগুন কাটছে। ইনুচ মোল্লার বাঁশঝাড়ের কড়ুল সব শুইয়ে দিয়েছে জন্তুটা। এ বছরের বাঁশ কি আর পাবে সে।’ ‘এবারের নতুন চাঁদ ছিল মেঘকুড়োলী। তাইতে ঝড়-তুফান হবে, বৃষ্টি হবে।’ ‘মাঝরাতের অনেক আগে মাছ চলাফেরা কমাল। ভোররাতে ওগুলোর আবার খিদে হবে। তখন খাওয়াদাওয়া শেষে সূর্য উঠবার আগেভাগে মাছ নামবে পানির আরো তলানিতে।’
কী অদ্ভুতভাবেই না চরিত্রগুলোকেও প্রকৃতি-সংলগ্ন করেছেন, ‘একুবের একটা লগ্গা অসুখ আছে। নাভির কাছ থেকে কাঁচির মতো কিছু একটা হেঁচড়ে হেঁচড়ে বুক পর্যন্ত ওঠে, আবার নামে। চাঁদের পূর্ণতায় অসুখটা দেখা দেয়, ফালি চাঁদের বেলায়ও।’
টুকার মতো একটি আর্কিটাইপ চরিত্র, প্রকৃতির অসাধারণ চিত্র, অনন্য নিজস্ব ঋজু সরল ভাষাভঙ্গি, শুরু থেকে শেষ নকশির মতো শিল্পের সংহত বুনন গল্পটির শক্তি ঠিকই, তবে টুকা কাহিনীর রয়েছে আরও এক অন্তর্মূল ঋজুতা। বুলবুল চৌধুরী সুকৌশলে গল্পের ভেতরে ব্যবহার করেছেন প্রচলিত গ্রামবাংলার মিথ। যে গল্পগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে, টুকা কাহিনী গল্প পড়তে পড়তে অনেকেরই চট করে সে-গল্পের কোনোটি মনে পড়ে যাবে। এই যেমন টুকার বিয়ের প্রসঙ্গটিই যদি তোলা যায়, বন্যার কারণে একবার খুব আকাল এসেছিল। ‘খবর পেয়ে টুকাও সেখানে গিয়েছিল রিলিফের আশায়। ফেরার পথে কালীতলার বটগাছের নিচে একটা মেয়েমানুষকে বসে থাকতে দেখল জড়সড়। সন্ধ্যার প্রলেপ নেমেছে চারদিকে। গাছপালাও ঘোমটা ঢাকা হয়েছে। টুকার ভয়ডর চিরদিনই কম। ও রকম একাকী নারী দেখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেডা গো?
জবাব নেই।
বাড়ি কই? আন্ধাইর রাইতে একলা ক্যান তুমি? ঠিকানা কইলে আমি আগ্গাইয়া দিতাম পারি।
অন্ধকারে সে ধরতে পারে না কীবা বয়সের মেয়েমানুষ, বিয়ে হয়েছে কি হয়নি। ঘর-পালানো বউ, না-বর্ষা ভিটেছাড়া করেছে—কোনটা! আবার ঘোমটা ঢাকা মেয়েমানুষটা তার কোনো প্রশ্নে কোনোভাবেই নড়ে না। এতে ভীষণ ক্ষেপে গেল টুকা। তাই খেঁকিয়ে জানতে চাইল, ওই, আমার লগে বিয়া বসবি?
সেই জিজ্ঞাসায় নড়ে উঠল মেয়েমানুষটা। হাতে ছিল কাচের চুড়ি। হাত নাড়তেই তা বেজে উঠলো।’
কী, ভূতের গল্পের কথা মনে পড়ছে না? মনে পড়লে কী হবে, গল্পের ভেতরে এটি বাস্তবিকই একটি নির্মম বাস্তবের চিত্র হিসেবে গল্পের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে উঠেছে।
অথচ জানেন, একজন মানুষ যদি সক্রিয় না হতো, টুকা কাহিনী গল্পটি হয়তো আমরা আজ পেতামই না। বুলবুল চৌধুরীর অভিন্ন হৃদয় ধ্রুব এষ একটি কথা প্রায়ই আক্ষেপ করে বলেন, বুলবুল ভাই তাঁর প্রতিভা আর ক্ষমতাকে ঠিকমতো কাজে লাগালেন না। কথাটা যে কী নির্মম সত্য, অনেকেই তা হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করবেন। সংসার সামলাতে জীবিকা নামের সতীনের কারণেই হোক বা নিজের সত্তা দুয়োরানী খামখেয়ালিময় নানা নেশার চক্করেই হোক, সৃজনশীলতার জগতে মগ্ন হওয়ায় তাঁর মধ্যে ছিল নানান শৈথিল্য। সে কুহেলিকুঞ্জটিকায় টুকা কাহিনী গল্পটিও শব্দে অধরা হওয়ার সমূহ আশঙ্কায় পড়েছিল বটে। তাহলে একটু বিস্তারেই যাওয়া যাক।
.jpg) বুলবুল চৌধুরী, শেখ আবদুল হাকিম, মামুন হুসাইন ও আনিস রহমান © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
বুলবুল চৌধুরী, শেখ আবদুল হাকিম, মামুন হুসাইন ও আনিস রহমান © ছবি : হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পর বুলবুল চৌধুরী ওয়াপদায় সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টার চাকরি সেরে চলে যেতেন ভিক্টোরিয়া পার্ক-সংলগ্ন অলক বারী সম্পাদিত রোমাঞ্চ অফিসে। সেখানে শেখ আবদুল হাকিম আর তাঁর পরিকল্পনায় বের হতো সে বিনোদন ম্যাগাজিন। রোমাঞ্চের ডিজাইন এবং লেখালেখির সূত্রে আরও যেতেন লেখক সিরাজুল ইসলাম, শেখ আবদুর রহমান, অভিনেতা আফজাল হোসেন, ইমদাদুল হক মিলন। ছিলেন হেলাল নামের আরও একজন। তাঁকে একদিন কোন খেয়ালে বুলবুল চৌধুরী শুনিয়েছিলেন গ্রামের টুকার গল্প। টুকা তো শুধু তাঁর গ্রামেরই মানুষ নয়, পাশাপাশি বাড়ির। টুকার কথা জানিয়ে বলেছিলেন, ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে, সব তো মাথায়ই আছে, বসলেই হয়ে যাবে।
কিন্তু, সেই বসাটাই আর হচ্ছিল না বুলবুলের। রোমাঞ্চে আসেন। কাজ সারেন। তারপর সন্ধ্যা থেকে বসে যান জুয়া খেলায়। কোনো দিন সে খেলা শেষ হয় মাঝরাতে, কোনো দিন বা ভোরও হয়। হেলাল প্রায় প্রায়ই টুকার কাহিনী লেখার তাড়া দেন, ‘কাহিনি তো জানাই আছে, বসে গেলেই শেষ করতে পারেন।’ বুলবুল চৌধুরী তাস ফেলতে ফেলতেই সায় দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসে যাব একদিন। কিন্তু সেই দিন যে কবে আসবে, কেউ জানে না।
একদিন আর হেলাল শুনলেন না কারও কথা। বুলবুল চৌধুরীর কোনো ওজরেও কান দিলেন না। জোর করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাসায়। খাইয়ে-দাইয়ে বসিয়ে দিলেন টেবিলে। সামনে এনে দিলেন কাগজ আর কলম। কাহিনি তো জানাই আছে, খালি নামাইয়া দেন।
কী আর করেন বুলবুল! যতটা না গল্প লেখার ভেতর তাড়নায়, তার চেয়ে বেশি হেলালের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে মগ্ন হলেন গল্প লেখায়। সারা রাত কেটে গেল। গল্প শেষ হলো না। পরের রাতেও হেলাল জোর করে নিয়ে এলেন বুলবুল চৌধুরীকে। সেদিন রাতে অবশ্য শেষ হলো টুকা কাহিনী। বুলবুল চৌধুরীর লেখাটিতে ছিল বিস্তর কাটাকাটি ঘষামাজা। পরদিন হেলাল গল্পটি নিজের হাতে সযত্নে কপি করে নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলেন গণসাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাতের হাতে। তারপর তো ইতিহাস!
পরবর্তীকালে এই হেলাল কিন্তু বুলবুল চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যিক বন্ধু কায়েস আহমেদের মতোই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কী কারণে, সে রহস্য বের করতে পারেননি বুলবুল চৌধুরী, যেমনটি অজ্ঞাত রয়ে গেছে কেন নাছোড়ের মতো হেলাল ওকে দিয়ে জোর করে লিখিয়েছিল ‘টুকা কাহিনী’!
‘টুকা কাহিনী’সহ আরও সাতটি গল্পসমেত বই হয়ে বের হয় ১৯৭৮ সালে টুকা কাহিনী নাম দিয়েই। বই হওয়ার পর আবারও নতুন করে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্য-মহলে গল্পকার হিসেবে তাঁর নাম হয়ে যায় স্থায়ী। প্রতিটি গল্পেই উঠে এসেছে চিরন্তন বাংলাদেশের রূপ, নারী, জীবন। গল্পগুলো হলো খরা, মাছ, অচেনা নদীতে ঢেউ, দংশন, মৃত্যু, দ্বিতীয় উদ্ধার এবং নিরবধিকাল।
এই আটটি গল্পসমৃদ্ধ টুকা কাহিনী বইটি পাঠ করার পর কেন বুলবুল চৌধুরীকে বাংলাদেশের সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক বলে অভিহিত করা যায়, সে কারণগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে।
১. এ শুধু বাংলাদেশেরই গল্প। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের জীবনের চালচিত্র, বেঁচে থাকা সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে খণ্ড খণ্ড চিত্রে। যদিও ছেটিগল্পের ফর্মটি ইউরোপীয়, আমাদের লেখকগণের লেখায়ও বিদ্যা-জ্ঞান-গর্বের ব্যাপারগুলো কখনো প্রচণ্ড কখনোবা ছিটেফোঁটাভাবে আসে, টুকা কাহিনী সে দৌরাত্ম্যমুক্ত। এসব গল্প পড়ে দেখে বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু মনে হয় না।
২. অনন্য ভাষাভঙ্গি। বুলবুল চৌধুরীর বলার নিজস্ব একটি ধরন আছে। যা তাঁর গল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ কথা বা ডায়ালেক্টগুলো তিনি অকৃত্রিমভাবে হুবহু উপস্থাপন করতে পারেন। মনে হয় যে, গ্রামেই বসে আছি।
৩. বিষয়ের অভিনবত্ব। বুলবুল চৌধুরী প্লট হিসেবে বেছে নেন বিচিত্র ঘটনা বা বিচিত্র চরিত্রকে। কিন্তু সুকৌশলে তিনি বাংলার প্রচলিত মিথ ব্যবহার করায় সে ঘটনা বা চরিত্র পাঠকের কাছে অচেনা বা অজানা মনে হয় না। মনে হয় চিরচেনা কোনো ব্যাপার।
৪. অকৃত্রিম শৈল্পিক উদ্ভাস। মিথের কথা বলা হয়েছে। ভাষায় প্রতীক এবং উপমা সংযোজনের কারণে সাধারণ আটপৌরে সরল ভাষার সৌজন্যে মনে হয় তাঁর গল্প বাসরসজ্জায় এখনো অলংকার খোলেনি। অর্থাৎ সালংকরা ভাষা, কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে ক্ল্যাসিক টোন আছে। আর গল্পের সমাপ্তির কথা তো বলাই হয়েছে, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে শেষ হয় গল্প।
৫. প্রকৃতির অপূর্ব ব্যবহার। প্রকৃতির সঙ্গে গল্পের ঘটনাপ্রবাহ গভীরভাবে সংলগ্ন হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলো প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়।
‘টুকা কাহিনী’ গল্প নিয়ে আগেই আলোকপাত হয়েছে। বাকি গল্পগুলোর দিকে চোখ ফেরালেও উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর দেখা মিলবে। ‘খরা’ গল্পটি পাঠমাত্রই আবহমান বাংলার ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একদা এই বাংলায় কত মহামারি হানা দিত, কত দুর্যোগ উপস্থিত হতো—কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা। এটা তো সত্য যে, কালের বিবর্তনে সেসব অনেক দুর্বিপাকই আর আগের মতো প্রখরভাবে ছোবল হানে না। তবে করোনার মতো নতুন কোনো উপদ্রব এসে তছনছ করে দেয় সাজানো বাগান। প্রতিটি দুর্যোগে মানুষের অসহায়ত্বের চালচিত্র একই। ‘খরা’ গল্পে এক বুড়ির মাধ্যমে গল্পকার সেই সময়ের ঘোর দুর্দিনকে চিত্রিত করেছেন। বুড়ির দিন চলে ভিক্ষা আর দাইয়ের কাজ করে। সে ভিক্ষা করার পাশাপাশি আজ বেরিয়েছে মুরগির ডিমের সন্ধানে। আমরা এটা জানতে পারি, মুরগির প্রতি ছুড়ে দেওয়া তার সংলাপে, আলো মুরগি, তলে মোডে একখান আণ্ডা নাই, তয়ও এমুন ভাব করস যে, আণ্ডা পাইয়া ছাও তুলতে বইছস!
এখানেই আবার যুগপৎ উল্লেখ করতে হয় বুলবুল চৌধুরীর বিষয়ের অভিনবত্ব এবং গ্রামের চালচিত্রকে নিখুঁতভাবে তুলে আনার কথাটা। এ গল্পের বুড়ি চাল ভিক্ষার চেয়ে মুরগির ডিমের সন্ধানে বেশি তাড়িত। কেননা ঘরের মুরগিটার ডিম সব তিনি খেয়ে ফেলেছেন খরার অভাবজনিত কারণে। এখন মুরগিটা ঝুমছে। যদি ও ডিমগুলো রাখত, তাহলে সেখানে ওম দিয়ে এত দিনে বাচ্চা ফুটাত। মুরগির এই ঝিমানো বুড়িকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, গল্পের শেষে দেখব সে নিজেই মুরগিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।
এর আগে বুড়ি ভনভন চরকি কাটা রোদে বেশি দূর এগোতে পারিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। ওঝা বাড়ির আমগাছটার ডালে ভর রেখে দাঁড়িয়ে গেছে। ওঝা বাড়ির মেয়ে জয়গুন দোলনায় খেলছিল। বুড়িকে দেখে এগিয়ে এলো। দুজনের কথার ভেতর থেকে আমরা খরার ভয়াবহ দিকগুলোর চিত্র পাই। চিল দেখি। ছোঁ মেরে ওঝা বাড়ির মুরগির ছানা নিতে চাইছে। জয়গুন বুড়িকে পানি খাইয়ে শীতল করতে পারে, চালও দিতে পারে, কিন্তু ডিম দিতে পারে না। ঘরে ফিরে এসে সে চালটুকু দিয়েই রাঁধে। নিজে খায়, মুরগিকেও খাওয়াতে যায়। তখনই ডিম না পাওয়া মুরগিটির দিকে তাকিয়ে টের পায়, নিজেই হয়ে যাচ্ছে মুরগি। একটা পরাবাস্তব আবহ ফুটে উঠেছে। আমি বুলবুল ভাইয়ের কোনো গল্পে পরাবাস্তব চেতনা পাইনি এর আগে। খরা বোধ হয় ব্যতিক্রম।
হ্যাঁ, বলতে দ্বিধা নেই। ‘খরা’ গল্পটি পড়ে মন ভরেনি আমার। গল্প ঠিক জমে ওঠেনি। তবে এর পরের গল্প মাছ-এ আদি এবং অকৃত্রিম বুলবুল চৌধুরীকে ফিরে পাওয়া যায়। কী অদ্ভুত সরল বর্ণনা। কিন্তু গভীর একটা অনুভবের জায়গা আছে। পুরোই প্রাকৃতিক গল্প। বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতিকথার বই ‘অতলের কথকতা’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা মাত্রই জানেন, তাঁর শৈশব কেটেছে পুরোটাই কালীগঞ্জের দক্ষিণবাগ গ্রামে। সে সময়ে বর্ষায় সে অঞ্চল পানিতে প্লাবিত থাকত। আর কাছেই শীতলক্ষ্যা। বালক বুলবুল নানাভাবে মাছ মারার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর অনেক গল্পে মাছ-প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। জলজীবন তাঁর প্রতিটি সাহিত্যকর্মেই ছেয়ে আছে কোনো না কোনোভাবে।
‘মাছ’ গল্পে ইদ্রিস যেন মাছে পাওয়া মানুষ। পাশে শোয়া স্ত্রী ওর ডাকের জবাব না দেওয়ায় মৃত ভেবে যে মানুষটা ভয় পায়, তার ভয় লাগে না রাত গভীরে বিলের মধ্যে মাছ মারতে যেতে। ও বউকে ঘুমের মধ্যে রেখেই টেঁটা হাতে বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার পথে ঘুম থেকে টেনে তোলে সিরাজকেও নেয় সঙ্গে। সিরাজ খালুই হাতে। নানান পদের মাছ আসতে থাকে। খালুইও ভরে। কিন্তু মাছের নেশায় ইদ্রিস বিভোর হয়ে যায়। কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। সিরাজ ওকে ডাকে। ইদ্রিস জবাব দেয় না। কোন ঘোরে জঙ্গলের দিকে ছুটছে। আলো নিভে যাচ্ছে। ইদ্রিসের কোনো কথা নেই। ভয়ে শরীর কেঁপে ওঠে সিরাজের। একটা রহস্যময় আবহ রেখে গল্প শেষ হয়।
পাঠকমনে নানা রকম অভিঘাত তৈরি হয়। ইদ্রিসটা আসলে কে? জবাব দিচ্ছে না কেন? গ্রামবাংলায় মাছমারা নিয়ে কত রকম মিথ আছে! পাঠকের মনে সেসব মিথ আর গল্পগুলো খাপছাড়াভাবে উজিয়ে আসে, ক্ষণকালের জন্য হলেও ‘মাছ’ ঘাই তোলে স্মৃতির কোষে কোষে, মগজে।
বুলবুল চৌধুরীর গল্পের এমনই জোর!
‘অচেনা নদীতে ঢেউ’ খুনির হৃদয়ে শুভ বোধ জাগ্রত হওয়ার গল্প। ‘দংশন’ গল্পে রিপুতাড়িত পিয়ারু মৃধা বিবেকবিষে জর্জর। ‘মৃত্যু’ গল্পে মৃত্যুতাড়িত হওয়ার ভেতরবাহির, ‘দ্বিতীয় উদ্ধার’ গল্পে ছায়েদ শীতে খেজুর রস বিক্রি করে চলে। কোনো বন্ধনেই সে জড়াতে চায় না এবং ‘নিরবধিকাল’ গল্পে আয়েশার বিস্ময়কর উপলব্ধি, ‘মাইনষের পেডে মানুষ!’
হ্যাঁ, মাইনষের পেডে মানুষ আসে বলেই তো এক মানুষ গল্প লেখে, আরেক মানুষ করে সেই গল্পের ব্যবচ্ছেদ, আরেক মানুষ আবার তা তর্ক বাংলায় ছাপায়। মাইনষের পেডে পেডে যেমন মানুষ হয়, মাইনষের পেডে পেডে কত গল্প আখ্যান রচিত হয়! সেই-সব গল্পের কয়টা থাকে ঘরের শিকায়, পাতিলায়? বুলবুল চৌধুরীর গল্প থাকব ঘরের কোনায় কোনায়, দুফুরে-রাইতে-সকালে। আষাঢ়ে শ্রাবণে, বৈশাখে চৈত্রে—বারোমাসই।