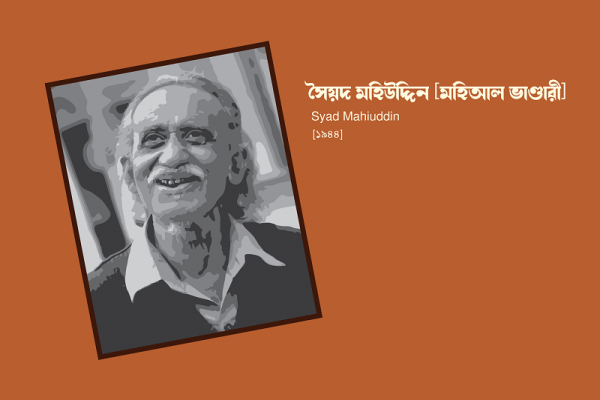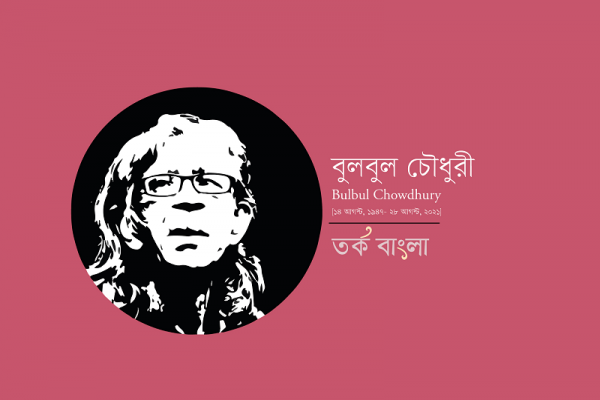
আমার সামনে দিয়ে শাবানা বেরিয়ে আসছেন...
বুলবুল চৌধুরী [Bulbul Choudhury]
বুলবুল চৌধুরী মারা গেলেন ২৮ আগস্ট। বেশ কিছুদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন। চিরচেনা, প্রাণবন্ত, তাগড়া এই কথাসাহিত্যিক শেষ দিনগুলোতে চুপসে গিয়েছিলেন, যেন বাতাসের ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অক্সিজেন নিয়ে, আকাশের পর আকাশে দেদার উড়ে বেড়ানোর পর আচমকাই স্বয়ং বাতাসের সঙ্গে তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার শত্রুতা! ২০১৮ সালের ২১ ডিসেম্বর ধ্রুব এষের বাসায় বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ করতে গিয়েছিলাম, চাকরিসূত্রে। একে সাক্ষাৎকার বলা যায় কি না, জানি না। কেননা আনুষ্ঠানিক আলাপ বলেই তৈরি করে রাখা কিছু সীমারেখা ছিল; গভীরতর আলাপে পৌঁছানোর চেয়ে বরং জীবনীভিত্তিক গড়পড়তা জিজ্ঞাসা ছিল। সেই দীর্ঘ আলাপের মার্জিত ও সম্পাদিত খুবই সামান্য অংশ ছাপা হয়েছিল একটি দৈনিক পত্রিকায়। সেই আলাপের পূর্ণাঙ্গ ও অবিকল রূপ হাজির করা হলো তর্ক বাংলায়—যেন কথোপকথনে বুলবুল চৌধুরীর বলার ভঙ্গি টের পাওয়া যায়। তাই ‘আপনি-তুমি-তুই’ সম্বোধন এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বাচ্য একাকার হয়ে গেছে; সম্পাদনার দোহাইয়ে ‘মার্জিত’ করা হয়নি।
সাক্ষাৎকার ও ভূমিকা : রুদ্র আরিফ ♦ গ্রন্থনা: সোহেল তারেক
রুদ্র আরিফ: আপনার ছোটবেলার কথা শুনতে চাই। জন্ম, বেড়ে ওঠা…
বুলবুল চৌধুরী: আমি জন্মেছি নানাবাড়িতে। জন্মের পর চলে গিয়েছি ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে; যেখানে জাহাজ ঘাট ছিল। এটা অনেক আগের কথা, ব্রিটিশ আমলের কথা। ওখানে আব্বার চাকরি ছিল জাহাজ কোম্পানিতে। আর মা বেশ গান-টান গাইতে পারতেন! আমি এখনো ভাবি মাঝে মাঝে যে, আমাদের জীবন... যখন মায়ের পেটে থাকি, তখন তো কিছু বুঝি না। জন্মের পরে হয়তো অনেক কিছু জানা থাকে। অনেক কাল কাটে কাজ করে। নিজেকে নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করি, এই যে আমি জীবনটা পেয়েছি, প্রথম স্মৃতি কোনটা? প্রথম আঁকিউঁকি কোনটা? খুঁজলে আমি দেখি যে, প্রথম স্মৃতি, হয়তো আগে ছিল, মনে হয় যেন আমি সেই জাহাজ ঘাটের কাছের বাড়িতে। যেহেতু আব্বা চাকরি করতেন—ফাঁকা বাড়ি একতলা, জানালা, সামনে বামপাশে জাহাজ কোম্পানির অফিস, সামনে পদ্মা…। একদিন তাকিয়ে আছি, সামনে নদী, জাহাজ যাচ্ছে। জাহাজটা একসময় মিলিয়ে গেল। তখন [পাশে] কে ছিল, মনে নেই।
ওখানে দুজন বন্ধু [ছিল আমার], ইনা বলে একজন মেয়ে ছিল, আব্বার কলিগের বোন, কিশোরী। মা গান গাইতে পারতেন বলে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই অনেক ভিড় হতো। ভিড় হতো এই জন্য যে, মা’র গান শোনার জন্য মেয়েরা আসত। মেয়েটার হারমোনিয়াম ছিল। ওই মেয়েটার ইচ্ছে ছিল গান শিখবে। ফলে সে প্রায় সারা দিন-রাতই মায়ের এখানে পড়ে থাকত। তো, ওর সাথে আমার বেশ একটা সখ্য গড়ে ওঠে, যদিও বয়সে সে আমার বড়।
রুদ্র: আপনার বয়স কত তখন?
বুলবুল: ৪৮ সালে জন্ম তো। [তখন] চার বছরের মাথায় পড়েছি আমি। সেই স্মৃতি, তো, ও [ইনা] যেটা করত...। মাঝে মাঝে মা ঘুমাতেন। একটা গাছতলা ছিল, বাড়ির মধ্যে প্রাচীর ঘেরা। ওখানে গিয়ে সে মাদুর বিছাত, খেলত। মাছ নিয়ে আমার প্রথম জীবনে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে থাকে। একদিন হলো কি, মেয়েটি ভারি মিষ্টি ছিল, শাড়ি পরা ছিল, সে যে দৌড়াত, তার চুল উড়ত, এখনো আমি আবছা আবছা মনে করতে পারি। তো, একদিন সে বলল যে, ‘চল, মাছ ধরবো।’ দরজা খুললেই পুকুরের পাকা ঘাট লাগানো। সে দুটো হাঁড়ি নিয়ে গেল, একটা হাঁড়ির মধ্যে কিছু ভাত দিল। ভাত দিয়ে সিঁড়ির মধ্য দিয়ে গিয়ে হাঁড়িটা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিল। ডুবিয়ে দেওয়ার পরে করল কী, চিংড়ি মাছ পুরো হাঁড়িতে ভরে গেল। সে সময় মাছেরও প্রাবল্য ছিল। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক খেলা হয়ে গেল। [মাছ ধরা নিয়ে] এত [মত্ত] হতাম যে, বিরক্ত হয়ে যেত মা নিজেও। মা তখন বলত যে, তুই এগুলো নিয়ে চলে যা!
যাহোক, এ সময় মা বলতেন, ‘তোর নানা আসবে। নানাকে তখন পর্যন্ত দেখা হয়নি। মা নানার অনেক গল্প বলতেন, তোর নানা এ রকম... নায়েব..., তার ঘোড়া আছে। আমি যে গান গাই, এটা আর কী গান! তার কলের গান আছে, গেলে কত রকমের বাজনা আর গান যে শুনতে পারবি!’ তো, যাহোক, নানা এলেন। মা বললেন মিষ্টি সুপারি আনতে। তার মিষ্টি সুপারি খুব পছন্দ ছিল। সেই সময় মিষ্টি সুপারি মানে রং দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে প্যাকেট করে...মা’র খুব প্রিয় ছিল। নানা এলেন। উনি আমার ডাকনাম দিয়েছিলেন বুলবুল, আদর করে ডাকতেন। উনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। নানাবাড়িতে ওটাই প্রথম যাওয়া।
একবার নানাবাড়িতে গেলাম। আমার এখনো মনে আছে, এখন যদিও ওই বাড়ি নেই... দক্ষিণ দিকে পুকুর, চারপাশে গাছে ঘেরা, দক্ষিণ পাশে মাটির ঘর টিন দেওয়া, কিন্তু খুবই সুশোভন। উনি আবার মাটি এনে, মাটির তল থেকে ডুবিয়ে এক ধরনের চীনামাটি পাওয়া যেত। একমাত্র তার ঘরেই ল্যাপ-পোঁচ থাকত। তো, ঘোড়ায় চড়লাম। কলের গানও শুনলাম। শুধু শোনা নয়, কৈবর্ত পাড়া আছে, এরা আবার মাঝেমধ্যে এসে অনুরোধ করে যেত যে, ‘নায়েব সাহেব, কলের গান শুনাইবেন আমাদের?’ তো একবার কৈবর্ত পাড়ায় গেলাম কলের গান নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে গেলাম, নানা নিয়ে গেল। এগুলোই মনে পড়ে। তারপর যেটা হলো, জাহাজে চড়া, জাহাজ দেখতাম; জাহাজের স্মৃতি আর মনে করতে পারি না। জাহাজের স্মৃতি আর নাই আসলে।
ঘটনা ঘটল যে, কিছুদিন পরে একটা টেলিগ্রাম আসল মায়ের কাছে—‘ইয়োর ফাদার ইজ নো মোর লংগার।’ মানে, নানা আর বেঁচে নাই। কী হয়েছে? ডাকাত মেরে ফেলেছে। ডাকাতরা মেরে ফেলার কারণ হলো, উনি যে নায়েবি পেয়েছেন, উনি আগে কলকাতায় চাকরি করতেন, এই নায়েবি পাওয়াটা অনেকেই পছন্দ করেনি। ফলে তারা এক ধরনের যোগসাজশ করেই কাজটা করেছে। অবশ্য ডাকাতরা ধরা পড়ার পরে এসব জানা যায়। ওরা ধরা পড়ে এভাবে যে, আমি অনেক বছর পরে জানতে পারি যদিও—দর্জির দোকানে এক পুলিশ কাপড় পছন্দ করতে গেলে কাপড়ের মধ্যে একটা বন্দুক পাওয়া যায়। পরে দেখা গেল, নানা যে বন্দুক ব্যবহার করত, এটা সেই বন্দুক। পাখি মারতে যেতেন উনি মাঝে মাঝে।
নানা মারা যাওয়ার পরে আব্বা ওখানে গিয়ে চাকরি করেন। ওই গোপালগঞ্জেই। নানি বললেন যে, ‘আমার তো আর কেউ নেই’– মা-ই ছিল তাদের একমাত্র সন্তান–‘তোর ছেলেটাকে আমার কাছে দিয়ে দে।’ …আসলে তা না। যত যা কিছু আছে, উনি আসলে ওখানে গিয়ে তো গ্রামের লোকজন, আত্মীয়স্বজন ছিলেন, মামাতো ভাই…
রুদ্র: নানাবাড়ি কই ছিল?
বুলবুল: গাজীপুরের কালীগঞ্জ। তাঁর বাড়িতে একটা বিশাল তেঁতুলগাছ ছিল। এটা আমরা বাচ্চাকাচ্চারা দেখতাম যে, ছেলে-মেয়েরা হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যেত না আরকি—এত বিশাল ছিল! হয়তো আদি থেকেই ছিল। পরে এসে বাড়ি করেছেন ওখানে। ওখানে আমার লেখাপড়া। নানি আবার নিজের ঘরের চালের জন্য নিজেই বাড়া বাড়তেন। তাঁর অভাব ছিল, তা নয়। [আমার] লেখাপড়া শুরু হলো এভাবেই: আমি বসে আছি, উনি কুলা ঝাড়ছেন, কুলা ঝাড়ার পরে দেখা যায় যে, একটা স্তর পড়ে। স্তরের মধ্যে উনি আমাকে ডেকে বলতেন, ‘আয় তো নানা, পড়ি।’ দাগ কেটে লিখতেন স্বরে অ; তো পড়াশোনা ওইভাবেই শুরু হলো।
এরপরে পাঠশালার পর্ব এলো। সঙ্গী-সাথি জুটল। এর মধ্যে ওখানে খালেক ভাই বইল্যা একজন ছিলেন; আমি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি, উনি তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র। উনি আমাকে ভাইয়ের মতো ওখানে নিয়ে যেতেন। আর ওখানে আমি অনেক ধরনের আজব আজব লোকজন দেখতাম। আমার নানার ছাত্র ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। [নানা] পড়াতেন তাঁকে। তাঁকে আমার দেখা হয়নি কোনো কারণে; একই গ্রামে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও।
যাহোক, মাছের কথা যে বললাম, মাছ যে, এখনো খাই বা দেখি [সেই স্বাদ পাই না]। ওখান থেকে আসার পরে আমরা– আমাদের গ্রামে বর্ষা আসত। বর্ষা আসলে পানি আসত। এখন তো সেই জোয়ারটা নাই। কোনো কোনো ভিটে-বাড়ি ছাপায় যাইতো। মাছের ডাক ছিল চারদিকে। তখন আমার মাকে দেখতাম যে, বড় বিছানার চাদরের মধ্যে কুঁড়া ভাত দিয়ে পানির মধ্যে ডুবায় রাখত। দেখা যাইত পুঁটি, মলা, চিংড়ি আসত। তখন টান দিয়ে তুললেই মাছ উঠে আসত।
ওই বয়সে আশপাশে মামা ছিল। একবার আমি গেলাম এক মামার সাথে—সাদেক মামা। উত্তরের গ্রাম—অনেক উত্তরে—প্রায় ছয় মাইল, সাত মাইল; তখন তো হাঁটা পথ ছাড়া কিছু ছিল না। সেখানে কাঁঠালের দিন ছিল, আমের দিন ছিল। ওদের আপ্যায়নের ঢং ছিল একটা কাঁঠাল ভাঙা নয়। মেহমান আসলে চারটা, পাঁচটা একসাথে ভাঙত। বিভিন্ন রকমের স্বাদ দেওয়া, ওই আমের দুই কোষ—খাও। বহুদিন পরে বর হয়ে সেখানে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে, সেইটা আর নাই। মানুষ আসলে এত বেড়ে গিয়েছে যে, এগুলো আর নাই।
যাহোক, আলেক ভাইয়ের সাথে আমি সেটে গেলাম। মাছের কথা যদি বলো, জোয়ারের সময় প্রথম যখন পানি আসত, এমন টানা টানছিল, এতটুকু ধান হতো, অনেক সময় পরে সন্ধ্যা লাগলেই চড়চড় আওয়াজ হতো। আওয়াজের মানে হচ্ছে যে, কইয়ের যে পোনা আছে, অসংখ্য পোনা থাকত তো, ওগুলো যখন ধানক্ষেতে আসত, তখন এ রকম চড়চড় একটা আওয়াজ হতো। কইয়ের একটা ডাক উঠত। আশপাশের লোকজন এই আওয়াজ শুনলেই বলত, ‘কই তো উঠছে রে, ল যাই...।’ মানে ভরপুর কইপোনা উঠতো আরকি। তো, আলেক ভাই ছিল মাছের ইয়ে আরকি! তো যাহোক, ওখানে আরেকটা লোক দেখলাম—বিচিত্র লোক আরকি—উনি কুইচ্যা ছাড়া খাইত না। তো, আমরা একবার দামান পাতলাম, আলেক ভাই আমাদের দলে। আমরা একটা কুইচ্যা ধরলাম, তাকে খবর দেওয়া হলো যে, ‘একটা কুইচ্যা বাজছে, খাইবেন নাকি?’ নিয়ে গেল, আমিও সাথে সাথে গেলাম। কুইচ্যাকে সবাই ঘৃণা করত। বঁটি দিয়ে মাথায় কোপ দিলে গলগলায়া রক্ত বের হতো, ছিটা এসে পড়ত গায়ের মধ্যে। আর ও বলে, ‘দেখছো, মাইনষ্যে ঘিন করে, এ রকম আছে নাকি কোনো মাছ?’ তো যাহোক, তখন ওখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ি। আব্বার চাকরি…
অভিজ্ঞতা হল কি একবার। দেখলাম যে, খুবই বিরক্তিকর অধ্যায়। কেউ পাত্তা দেয় না, নায়িকারা বিশেষ করে। আমাকে বলা হলো শাবানার ইন্টারভিউ নিয়া আসতে। তো, গেলাম। এদিকে আবার শাবানারে নিয়া গসিপ করা হইছে আগেই। তো গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। তারপরেও গেলাম। গিয়ে খুব বিনয়ের সাথে বললাম। আমি তো জানি যে, সে পাত্তা দেবে না। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, ‘আপনি প্রশ্নগুলো লিখে দিয়ে যান। আমি উত্তর দেব। লিখে রাখব আমি, এখন আমার সময় নাই।’ এরপরে আমি কয়েকটা প্রশ্ন লিখে রেখে দিয়ে আসলাম।
রুদ্র: স্কুলের নাম মনে আছে?
বুলবুল: স্কুলের নাম দক্ষিণবাগ প্রাইমারি স্কুল। থ্রি পর্যন্ত এখানে পড়ার পরেই আমার বাড়ির পথটা পরিবর্তন ঘটে। ওখান থেকে আমরা ঢাকায় আসি। ঢাকায় আব্বা একটা বাড়ি কিনেছিল। চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে পুরান ঢাকায়। হিন্দু বাড়ি ছিল। আসলাম খুব আগ্রহ নিয়ে—দালান দেখেছি, বাড়িঘর দেখিনি। ঘোড়ার গাড়িতে প্রথম ফুলবাড়ি স্টেশনে আসলাম।
রুদ্র: এটা কোন সালে?
বুলবুল: ১৯৫৭ সালে। এসে আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো, জুবিলী স্কুলে।
রুদ্র: কোন ক্লাসে ভর্তি হলেন?
বুলবুল: ক্লাস ফোরে ভর্তি হলাম। এই স্কুলেই কায়েস আহমেদকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। ওপার বাংলা কলকাতা থেকে এসেছিল সে। ওর বাবা এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে। কায়েস আহমেদ আমার সাথেই পড়ত।
আমার নানাবাড়িতে আবার বই ছিল। ওইখানে আবার রূপকথার বই পড়তে পারতাম। তারপর আবু জাফর শামসুদ্দীনের চাচাতো ভাইয়ের বোন ছিল রানিয়া—উনি পড়তেন ফাইভে। তো, নানির সাথে পড়তে গিয়ে এই যে বই ছিল ঘরে, ওইটুকু বয়সে, মানে ক্লাস ওয়ান-টুতেই গল্পের বই পড়ে ফেলতে পারতাম। আমার গলাটাও হয়তো সুন্দর ছিল বা পড়ার স্টাইল—ছেলেবেলায়। উনি [রানিয়া] ছিলেন অসামান্য চুলের অধিকারী, অসামান্য সুন্দরী। দেখা হয়নি পরে আর কোনো দিন। তো, যখন অবসর থাকতাম, স্কুলে যাইতাম, ওদের বাড়িতে গেলেই উনি বই বের করে নিয়ে আসতেন, ওনার তো নিজের বাড়িতেই বই থাকত। আর আমাকে বলতেন, ‘পড় তো।’ তখন উনি ক্লাস ফাইভে পড়তেন। আর আমি ক্লাস টু-এ পড়তাম।
তো, ঢাকায় এসে যেটা হলো যে, আমরা দখল পেলাম একটা ঘর না, দুইটা ঘর। মোট পাঁচটা ঘর ছিল, আমরা পেলাম দুইটা ঘরের দখল। বাকি তিনটা ঘরের দখল ছিল বিহারিদের ভাড়াটে। বাড়ি আমরা কিনেছি, তাদের ছাড়তে বলা হলো। কিন্তু ওরা এমন করল যে, ওরা তখন সেই সময় [আমরা বাসা নিয়েছিলাম সিংটোলা, সূত্রাপুর ডালপট্টি] পুরো গলিতে মুসলমান বলতে আমরা ছিলাম, আর সুলেমান খান বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, আর বিহারি একজন হুসেন মোল্লা। আর বাকি পুরোটা ছিল হিন্দু-অধ্যুষিত। ফলে হলো কি—আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম। আব্বা সকালে ৮টার সময় বের হয়ে অফিসে যেতেন। যাওয়ার আগে সাবধান করে যেতেন।

বুলবুল চৌধুরী © ছবি: হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
রুদ্র: আপনার বাবা তখন কিসে চাকরি করতেন?
বুলবুল: ওয়াপদা। জাহাজ কোম্পানির চাকরি তো সরকারি চাকরি। প্রথমে গেলেন ইরিগেশনে। তারপরে ওয়াপদায়। ওইভাবেই আর কি। তো, ওই বিহারি নিয়া [ঝামেলা]...। আমার নানা ছিলেন, আমার নানির আপন ভাই, উনি আবার উকিল। থাকতেন আগা সাদেক রোড। উনি বললেন যে, ‘দাঁড়াও, আমি বিহারি খেদানোর ব্যবস্থা করছি।’ খেদানোর পর আমরা পুরো বাড়িটার দখল পেয়েছিলাম।
ঢাকা আসার পরে একটা কথা মনে পড়ে। আমরা যখন আসছিলাম ঘোড়ার গাড়ি চড়ে, আমরা তো চালডালসহ অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসছিলাম। তো আসতে আসতে, আমরা নওয়াবপুর দিয়ে আসছিলাম। এখন রাস্তাঘাটগুলো বুঝি… ভিক্টোরিয়া পার্ক তখন আরও বড় ছিল। তো, এইখানে এসে কিছু গাছ দেখা গেল। পামগাছ বোধ হয়। এখনো আছে কি না, জানি না। তো, একজন বলল, ইংরেজরা এইখানে ফাঁসিতে এই সব গাছে সিপাইদের মারছে। তখন যতটুকু বুঝেছি যে, ইংরেজরা আমাদের লোকজনকেই মেরেছে। তারপর বহুদিন পর্যন্ত এমন হলো... ওই সময় থেকে একটা গোঁ ধরেছিলাম, ইংরেজরা যেহেতু এত খারাপ কাজ করেছে, তাহলে ইংরেজি ভাষাটাই শিখব না। ফলে ইংরেজি ভাষাটা কিন্তু আমার কখনো তেমন একটা আয়ত্ত করা হয়নি। পাস করে গেছি নানানভাবে। ছাত্র ভালো ছিলাম। একটু পড়লেই হতো।
তো, যাহোক, কায়েসকে নিয়ে একবার হলো কি, ঢাকায় নতুন এসেছি। শুনতাম যে, বায়ান্ন গলি তেপ্পান্ন বাজার—এই ধরনের কথাবার্তা। মাঝেমধ্যে আমরা করতাম কি, বৃহস্পতিবার হাফ স্কুল থাকত, তো আমরা সেদিন বেড়িয়ে ঢাকায় কোথায়, কোন গলি আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতাম। বেড়িয়ে পড়তাম আরকি, চেনার জন্য। তো, একদিন সদরঘাট গেলাম। সদরঘাটে একটা কামান ছিল, কামান নিয়ে একটা মজার কথা বলব...। তো একদিন গেছি, সেখানে বাঁধ ছিল, বাঁধের পানি কমে গেছে; এখন তো দোকানপাটে ভরা। সেখানে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, ‘দেখবেন নাকি মাকড়সা মেয়ে?’ আমি কায়েসকে নিয়ে ঢুকলাম। পয়সা আমার কাছে থাকত নানির দৌলতে। নানি আমাকে লুকায় লুকায় পয়সা দিত। বই কিনতাম, সেই পয়সাও সে জোগান দিত। গিয়ে ঢুকে দেখি, অনেক লোকই জড়ো হয়েছে, ‘মাকড়সা, মাকড়সা... কিছু খায় না সে, শুধু মধু খেয়ে বেঁচে থাকে!’ গিয়ে দেখি পুরো একটা মাকড়সার জাল আরকি মঞ্চের মধ্যে। আসলে পুরাই ফটকাবাজি, সেই দিনও এখনকার মতো মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা কামানো আর কি! পুরো কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে জাল কেটে মেয়েটাকে পেছনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মেয়েটা পেছন থেকে জালের মধ্য দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে আছে; তখন তো বুঝতে পারি নাই, এখন অনুভব করি। বেশ সুন্দর মেয়ে, যুবতী বলা চলে। আমি তার দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পাশে তাকিয়ে কায়েসকে খুঁজতে লাগলাম। বুঝলাম যে, সে আরও আগে হাওয়া হয়ে গেছে! সে ছিল এ রকমই—অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বসত।
যাহোক, ঢাকা এসে আমি ছবি দেখতে গেলাম—সিনেমা, রূপমহল সিনেমা হলে। সিনেমা হলে গিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে বসেছি, সিনেমার নাম মনে নেই। সিনেমার একটা দৃশ্য ছিল: স্বপ্না টাইপের কিছু মেয়ে থাকে না? কথা নেই, বার্তা নেই, একটা বাচ্চাকে এমনিই শুধু মারছে। বাংলা সিনেমা ছিল, ছবির নাম মনে নেই। তখন সুচিত্রা-উত্তমের ছবি ছিল, এদেরই সে রকমই কোনো ছবি হবে হয়তো। আমি তখন এমন রেগে গেলাম, ধরো, গ্রাম দেশে থেকেছি, আম পাড়ছি ঢিল মাইরা, কাউয়া মারছি ঢিল মাইরা, আমার রাগ হইল ওই মহিলার প্রতি—আরে! নিজের অজান্তেই নিচে ঝুঁকে ঢিল খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, এখানে ঢিল কই পাবো আরকি! যাহোক, এসব ঘোরাঘুরির মধ্যেই রূপমহলে সিনেমা দেখলাম, সন্ধ্যাবেলায় কামান দেখলাম, লালকুঠি দেখলাম।
একদিন টিচার জিজ্ঞেস করল যে, ঢাকার দর্শনীয় স্থান কী। বইয়ের মধ্যেই এসব থাকত। বইয়ের মধ্যে তো আছেই, কিন্তু তার বাইরেও তো আছে; আমি দেখেছি। রূপমহল সিনেমা হল, সদরঘাটের কামান—এগুলো বলার পরে টিচার খুব হেসে উঠলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কোথায় ভুলটা করেছি। এই ছিল আরকি…।
এরপরে যেটা হয় যে, আমার তো মাছ ধরার অভ্যাস ছিল, নেশা ছিল। আব্বার মধ্যেও ছিল, আমি সেটা আব্বার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। [আমাদের বাড়ির] পেছন দিকে কয়েকটা কলাগাছ ছিল। মাটি ছিল তখন। কোনো কিছু লাগালেই সেটা খুব প্রসার লাভ করত। মাটি এমন উর্বর ছিল যে, সেটা বলা বাহুল্য। আলীমুদ্দীন নামে গ্রামের এক লোক ছিল, যুবক শ্রেণির—সেই আমাদের সবকিছু করে দিত, বাজার-সদাই থেকে সবকিছু। মাচান দিলাম, লাউ দিলাম, শিম দিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি, এরপরে তো টাল লাগে। আমি তো কায়েসকে নিয়ে ঘুরছি, রেললাইনে ঘুরছি, দেখতাম যে, রেললাইনের পাশ দিয়ে আগাছার কোনো অন্ত নাই। আমরা মাঝেমধ্যে গিয়ে দা দিয়ে কোবায়া সেগুলো কাইট্টা নিয়া আসতাম। এগুলো দিয়ে দুই কাজই হইতো—তখন তো গ্যাসও ছিল না, খড়ির চুলা। অঢেল খড়িও হতো, মাচানও হয়ে যেত। আর মাছ ধরা হতো। আমি জাল নিয়ে যেতাম।
রুদ্র: মাছ কোথায় ধরতেন?
বুলবুল: গেন্ডারিয়া। গেন্ডারিয়া হয়ে ওই পাড়ে যে মীর হাজারীবাগ ছিল, ওই পুরাটাই গাং ছিল। গিয়ে জাল ফেললেই হতো। মূলত খলসে মাছ বেশি ছিল। সব ধরনের মাছই থাকত, তবে এই [খলসে] ধরনের মাছ বেশি থাকত। সবচেয়ে বেশি মাছ আসত ধোলাইখালের যে অংশটায় বুড়িগঙ্গার যে ব্রিজটা বেড়িয়েছে, [সেখানে]। বুড়িগঙ্গার সাথে যোগাযোগ ছিল। বর্ষা আসলেই পানি যাওয়া-আসা করত, এটা দিয়েও মাছ আসত। অফুরান মাছ আসত। যখন পানিটা কমে যেত, তখন হতো কী, জাল দিয়ে বলো, হাত দিয়ে বলো, মানুষজন মাছ ধরার জন্য নেমে পড়ত। নেমে পড়লে পানি ঘোলা হয়ে যেত। পানি ঘোলা হলে মাছ কিন্তু পানির নিচে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, ভেসে উঠত। ফলে পুরো খাল জুড়েই মাছ ধরার একটা মহা উৎসব লাগত।
ঢাকায় আসার পরেও আমি মাঝেমধ্যে গ্রামে গেছি। সেখানেও বড় বিলে মাছ ধরার জন্য যেতাম। চৈত্র মাস আসলে তো বিলের পানি শুকিয়ে যেত। এসব জায়গায় পুরোনো মাছ পাওয়া যেত—গজার, শৈল, বোয়াল। কাছি টান দিয়ে মাছ ধরতাম। আমি গেলেই আলেক ভাই এসে খবর দিয়ে যাইত, ‘কালকে কাছি টানতে যামু, যাইবা নাকি?’ গেলে আবার...যারা কাছি টানে, কেউ কাছি টানে, কেউ পলো দিয়ে মাছ ধরে... গেলে ভাগে পড়ে। অভাব তো কিছুই না, নেশা বা অভ্যাস আর কি। দেখতাম যে, দড়িতে ইট বাঁইধ্যা টানতাছে এই মাথা থেকে ঐ মাথায় ধরে, এই পাড় থেকে ওই পাড় ধরে, টানলে হয় কি, কাদা যখন নইড়া ওঠে, বড় বড় মাছ ভয় পাইয়া যায়। তখন হয় কি, ডুববার জন্য, পালাবার জন্য, মাটির নিচে ঢোকার জন্য মাছ নড়েচড়ে ওঠে, আর পেছন দিকে শিকারিরা লেগেই থাকে পলো নিয়ে। সেটা ঢুকায় দিলেই তো একটা আওয়াজ করে। এভাবেই মাছ ধরে নিয়ে আসত।
রুদ্র: [আপনার] জন্মতারিখ, স্থান?
বুলবুল: ১৬ আগস্ট, ১৯৪৮। গাজীপুরের দক্ষিণবাগ এলাকা।
রুদ্র: ঢাকায় কায়েস আহমেদের সাথে আরও স্মৃতি?
বুলবুল: কায়েসকে দেখতাম যে, টিফিন পিরিয়ডে অনেকে খেলতে নামত। ও [কায়েস] যেত না। ওর সাথে বই থাকত সব সময়। বন্ধুত্ব হওয়ার কারণ, আমিও বই পড়তাম। সে-ও দেখতাম যে, ক্লাসে বসে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ত। এইভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আর সেও ছিল আমার মতো হ্যাংলা-পাতলা। আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।
একদিন সে আমাকে নিয়ে গেল তার তাঁতীবাজারের বাসায়। তার বাবা ছিল। সেখানে গিয়ে প্রথম অঢেল বই পেলাম। সে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসত। যখনই যেত, সে সাথে করে বই নিয়ে আসত। সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম, শুকতারা বলে একটা পত্রিকা বের হতো। আরও যারা ছিল ওই সময়, ওদের বইপত্র ছিল। প্রচুর পড়াশোনা হতো।
ক্লাস এইটে উঠে আমি একবার ঘাপলায় পড়লাম। ঘাপলায় পড়লাম বলতে কি, বাড়িতে ধান বিক্রি হতো। নানার প্রচুর ধান, সম্পত্তি ছিল। মাকে দিয়ে গেছেন, আগেই বিয়ের সময়েই, মায়ের নামে। আলমারি খুলতে দেওয়া হতো আমাকে। মা আমাকে চাবি দিয়ে মাঝে মাঝে বলত, ‘যা তো, এটা নিয়ে আয়, বা সেটা নিয়ে আয়।’ আলমারি খুলে দেখি যে, তাক তাক টাকা। এইটে পড়ি তখন। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। মনে হইল আর কি, এক কাজ করলে কী হয়, এখান থেকে টাকা নিয়ে চইল্যা গেলে তো আরামসে ঘুইরা-ঘাইরা বেড়ানো যাবে! তখন কিছু টাকাপয়সা নিয়া পলাইলাম।
পলাইয়া যাব কই? আমাদের নিচে একটা ভাড়াটে থাকতেন। ওনার নাম হুসেন খান। ওনার আবার বাড়ি ছিল নরসিংদীর দিকে; নরসিংদীর দিকে কুলু পাড়া বলে একটা জায়গা ছিল, তার পাশাপাশি। উনি গল্প করতেন, কুলু পাড়ায় গেলে, ওদিকে তো গরিব লোকজন সব, তো ওরা সুন্দর ছেলে দেখলে সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সাজায় দিয়ে বিয়ে দেয়! পলায় গিয়া ভাবলাম যে, যাইগ্যা। আমি তখন গুলিস্তান আইস্যা পড়ছি। কই যামু, ঠিক করতে পারছি না। হোটেলে তো আর থাকোন যাইবো না রাতে। কাকার কথা নরসিংদী গিয়া, খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা একটা বাড়িতে লজিং মাস্টার থাকার জন্য জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন যে, ‘একটা বাড়ি আছে। লও বাবা তোমারে লইয়া যাই। সেখানে বিয়ার বয়সী কোনো মেয়ে নাই কিন্তু। দুইটা বাচ্চা মেয়ে।’ যাওয়ার পর তারা জানতে চাইলো যে, কী ব্যাপার? আমি বললাম, বাড়িতে তো সৎমা, খুব অত্যাচার। তখন তারা বলল যে, ‘ঠিক আছে, তোমাকে আমরাই পড়াশোনা করাব। তো বাবা, বাড়িতে গিয়া তোমার বইপত্র, জিনিসপত্র যা আছে, সব লইয়া আসো।’ বিকেল বেলা, রাত্রে বেলা খাইলাম, শুইলাম। ভোর রাত্রে উইঠ্যা নরসিংদী স্টেশনে আইস্যা কই যামু, দেখি যে একটা ট্রেন আইছে, ভৈরবের দিকে যাইবো, উইঠ্যা পড়লাম। ভৈরব গিয়া আবার যদি বিপদে না পড়ি, সেই জন্য স্যুটকেস, গামছা কিইন্যা... যাতে আবার কোনো লজিং পেলে শুনতে না হয় [জিনিসপত্র নিয়া আসো]... পার হয়া নদীর ওপারে গেলাম।
ওখানে গিয়ে গুদারাঘাটে চা বেচে—এমন একজনকে বললাম যে, ‘ভাই, আমি খুব বিপদে আছি, সৎমা...’ ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন উনি বললেন, ‘আইয়েন, এখানে আবু সাইয়িদ মিয়া আছেন, উনি পাটগুদামের মালিক। আইয়েন নিয়া যাই।’ উনি এমনভাবে আমাকে বরণ দিলেন যে, বলার মতো না। তার বিশাল কোম্পানি। উনি থাকেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সকালে ট্রেনে করে চলে আসেন আর সন্ধ্যার সময় চলে যান। কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়া অফুরান চলত। এদিকে ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। নতুন বছর শুরু হচ্ছে। তো, এদিকে আমার বেশ চলছিল! নানান জায়গায় ঘুরে-ফিরে জীবনযাপন চলছিল। অনেক ঘটনাই এখানে ঘটেছে। একদিন হলো কি, ভাবলাম যে, ঘুরি গিয়া অন্য কোথাও, সময় কাটে না...
ক্লাস এইটে উঠে আমি একবার ঘাপলায় পড়লাম। ঘাপলায় পড়লাম বলতে কি, বাড়িতে ধান বিক্রি হতো। নানার প্রচুর ধান, সম্পত্তি ছিল। মাকে দিয়ে গেছেন, আগেই বিয়ের সময়েই, মায়ের নামে। আলমারি খুলতে দেওয়া হতো আমাকে। মা আমাকে চাবি দিয়ে মাঝে মাঝে বলত, ‘যা তো, এটা নিয়ে আয়, বা সেটা নিয়ে আয়।’ আলমারি খুলে দেখি যে, তাক তাক টাকা। এইটে পড়ি তখন। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। মনে হইল আর কি, এক কাজ করলে কী হয়, এখান থেকে টাকা নিয়ে চইল্যা গেলে তো আরামসে ঘুইরা-ঘাইরা বেড়ানো যাবে! তখন কিছু টাকাপয়সা নিয়া পলাইলাম।
রুদ্র: কত দিন ছিলেন ওইখানে?
বুলবুল: মাস দেড়েক ছিলাম। শেষ মুহূর্তে ধরা পড়লাম এভাবে, আমি নরসিংদী আসলাম। খালি খালি আইছি আর কি, ঘরে বসে সময় কাটে না—এই জন্য আরকি। তো, স্টেশনে খাইতে বসছি, দেখি যে- আব্বা! উনি আমার হাত ধরে বললেন যে, ‘বাড়ি চল।’ নিয়ে উনি আমাকে আর কিছু বলেন নাই। বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনলাম, আমি যে পলায় গেছি, সে জন্য কবিরাজ ডাকছে। কবিরাজ নাকি মরিচ পড়া দিয়ে বলছে যে, ‘যা নরসিংদি যা, ওখানে গেলে পোলারে পাইবি।’ নরসিংদী গিয়াই আমারে পাইছে—আমি বোঝার পাইলাম না [এই] ভেটটা। সবচে মুশকিল করল কবিরাজ। সে বলল, ‘এসব দোষ কাটাইতে সাতটা হাঁস খাওয়াইবেন আস্তা!’ পুষ্করনি আছে, হাঁস আছে। সাতটা আস্তা হাঁস খাওয়ার ব্যবস্থা করল। কিছু খাইতাম, খুব গন্ধ করে। আর ভাব করতাম যে সবটাই খাইছি। একটা পোষা কুত্তা ছিল, ওরে দিয়া খাওয়াইতাম। এইভাবে খাওয়া শেষ হইতো আর কি। তখন মনে হইতো যে, কোর্সটা পুরা করলে হয়তো এত ফ্যাসাদ আর হয় না!
এসে কায়েসকে দেখি যে, নাইনে উঠে গেছে। আইস্যা দেখি যে, সে একটা গল্প লিখেছে, ‘চোর’ নামে। জীবিত কোনো লেখককে প্রথম দেখলাম আর কি। জসীমউদ্দীনের নাম শুনতাম। জসীমউদ্দীন আমার ফুফাতো বোনরে বিয়া করতে গেছিল। কিন্তু কাউকে দেখা হয়নি। আবু জাফর শামসুদ্দীনকে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা হয়নি। কায়েসকে দেখলাম যে, এ রকম গল্প লিখেছে। আমার ইচ্ছা হলো, আমি জানতে চাইলাম, লিখতে হলে আসলে কী করতে হবে। ও [কায়েস] খুব—ওই বয়সেই ভারি পণ্ডিত ছিল। বলল, ‘লিখতে হলে পড়তে হবে, জীবনকে দেখতে জানা জানতে হবে’। এই ছিল তার ভাষ্য। সেই থেকে জীবনে কী দেখছি জানি না, চলছে আর কি! পরে সে আমাকে... আমার উত্থানটা তাকে ঘিরেই।
রুদ্র: আপনি প্রথম লেখালেখি শুরু করলেন কবে থেকে?
বুলবুল: ৬৮ সালে, কায়েস আমাকে নিয়ে গেল বিউটি বোর্ডিংয়ে। সেখানে তখন কিন্তু আড্ডা হতো, সিনিয়ররা ছিল। আর নতুন প্রজন্মের হাসান [আবুল হাসান] বলো, নির্মলেন্দু গুণ বলো, কায়েস বলো, শাকের চৌধুরী মানে সমুদ্র গুপ্ত—কেউ বাদ নাই যে এখানে আসত না। লিটলম্যাগ বাংলাদেশে তখন যত বের হতো, সব আগে ওখানে আসত। তখন তো সব লিটলম্যাগ নির্ভর ছিল, দৈনিক পত্রিকা ওইভাবে ছিল না। ওখানে কায়েস একদিন নিয়া গেল। নিয়ে গিয়া পরিচয় করিয়ে দিল। দেখলাম যে, ওরা সবাই ওখানে বসে কবিতা পড়ছে, আবার মতামত দিচ্ছে—এই ধরনের পরিবেশ ছিল। তো, আমি ওদের সাথে মিশি। এর মধ্যে হাসানকে আমার বেশ ভালো লেগে গেল। উড়াইল্যা ভাব, দেখলাম যে চমৎকার। নির্মলকে দেখলাম, পরিচয় হলো। ভাবলাম যে, মানে এদের সাথে খাতির রাখতে গেলে—আমি তো এদের দলের নই, তাহলে যোগাযোগটা কেমনে চলবে?
যাহোক, প্রথমে একটা কবিতা লিখলাম আরকি। হাসান তো সারারাত ঘুরে বেড়াত। আমাদের ঘরে এসে পড়ে থাকত। কবিতার হেডিং ছিল ‘রঘুবংশী বাংলার ঘরে’। লাইন হচ্ছে, ‘রঘুবংশীয় বাংলা ঘরে/ মধ্যরাতে পিদিম জ্বলে/ রঘুবংশীয় বাড়ির ধারে/ নদী আছে, নৌকা আছে/ বংশীয় এক রূপসী মেয়ে/ সেই নদীতে গোসল করে।/ যদি বলি বংশী শোন,/ তোমার মেয়ে রূপ বিলোবে?/ বংশী বলে অর্থ পেলে,/ কেঁদে কেঁদে বাঁচতে পারি।’
মূলত, ওই সময়, এখন আমি বুঝতে পারি, এই যে, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ পড়ে ফেলেছি। ওইখানে তার বাবা মেয়েকে দিচ্ছে। মূলত এই কবিতা লিখতে গিয়ে, একটা বিষয় তো লাগে, ওইখান থেকেই আঁচড়টা লইয়া বানাইছি। হাসান কবিতাটা পড়ল, আমি ওকে কবিতাটা দিলাম। ও পড়ে বলল, “তোমার কবিতা ভালো হয়েছে। নামটা তুমি পালটে দাও। এটার নাম দাও ‘প্রাকৃত কবিতা’।” আমি তখন প্রাকৃত শব্দের অর্থও জানি না, আমি ঘাবড়ে গেলাম।
যাহোক, তারপর সে একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করল। সে তো যেখানে সেখানে বসেই লিখত। তার দুটো-তিনটে লাইন মনে আছে আমার—‘স্থিতি চাই/ স্থিতি হোক’—এই দুটো লাইনই আমার মনে আছে। দেখলাম যে, কই স্থিতি চাই, কই স্থিতি পাবো, ছাগল-পাগল ভাব, ভাবলাম যে, কবিতা বোধ হয় আর আমাকে দিয়ে হবে না!
পরে কায়েসের অনুপ্রেরণায় আমি প্রথম গল্প লিখলাম। জগন্নাথ কলেজে ঢুকলাম ৬৫ সালে। একটা গল্প লেখার প্রতিযোগিতা ছিল। রাহাত খান বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। শওকত আলীও ছিলেন। অজিত রায় ছিলেন আমাদের সময়ে। পরে ওখানে আমি ‘জোনাকির সন্নিকট কেন্দ্র’ বলে একটা গল্প লিখলাম। এটা দিলাম। আমি সেকেন্ড হইলাম। এই গল্পটাই পরে কায়েস ছাপল ছোটগল্পের কাগজে। এইভাবেই দেখলাম যে, ছাপা যখন হয়, এইভাবেই টুকটাক করে...। মূলত আমার কিন্তু গল্প লেখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমি চাইছিলাম যে, ওই সিনেমায় এমন নেশা ছিল, ছেলেবেলায় এমন করছি যে, ধরো, সিনেমা দেখে মনে হইত যে, সিনেমা বানাব এ রকম। প্রচুর সিনেমা দেখা হইত। একাই সিনেমা দেখতে চলে যাইতাম। আর টাকাটা পেতাম, ওই নানির কাছ থেকে চাইলেই পাইতাম। পয়সার অভাব হইত না, যেতাম।

বুলবুল চৌধুরী ও শেখ আবদুল হাকিম [দুজনই সদ্যপ্রয়াত লেখক] © ছবি: হামিদ কায়সারের সৌজন্যে
রুদ্র: চিত্র পরিচালক হবেন, এটা ভাবতে শুরু করলেন কবে থেকে?
বুলবুল: এটা, প্রথম আগে বললাম না যে, একবার ধরা খাইয়া গেলাম, চ্যাগা মারতে গেছি? তখন ইচ্ছাটা ডেভেলপ করল এইভাবে যে, একদিন দেখি কি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মায়ের আবার অভ্যাস ছিল সাদা চাদর পরার... সাদা চাদর ঝুলিয়ে রেখেছেন সামনে তার, আর উল্টা দিকে আছি আমি, ঘরের লাইট এসে চাদরের ওপর উল্টো দিক থেকে পড়েছে, হঠাৎ দেখি আমার ছোট ভাইটা বেড়িয়েছে। ছায়া পড়ে না? সাদা পর্দায় ওর ছায়াটা এমনভাবে পড়েছে, ছায়া পর্দা বলে না? একদম সিনেমার মতো। স্পষ্ট মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সিনেমার মতো দেখা যাচ্ছিল। পরে বাড়ির ছেলেপেলে নিয়া, ভাই আছে, আরও যারা ছিল তাদের নিয়ে—সবাই আসল যে সিনেমা বানাব। সবাই বসল উল্টা দিকে। আর পেছনের দিকে আমি কি আমদাম করলাম জানি না, কিন্তু সবাই বেশ উপভোগ করল।
বোম্বাইরা থাকত ওই সময়, বোম্বাইয়ের পুরো আধিপত্য ছিল সেখানে, মানে মুম্বাইয়ের অধিবাসী, ওই যে আগা খানের যে সম্প্রদায়। এরা আবার সবাই বেশ সুন্দর ছিল। এরা আবার জুবিলী স্কুলটা দেখেছিল। আমাকে এক বন্ধু বলল কি, আগে না আসলে, ওরা করে কি, পুরা শুয়ে পড়ে চুল ফেলে রেখে যায়! তারপর সেই চুল দেখার জন্য স্কুলের বিল্ডিংয়ে উঠলাম যে, দেয়াল ভেদ করে দেখা সম্ভব?
রুদ্র: আপনি চিত্র পরিচালক হতে চেয়ে চিত্র সাংবাদিক হয়েছিলেন, চিত্র পরিচালক হওয়ার জন্য আপনার উদ্যোগগুলো কী ছিল?
বুলবুল: ’৭১-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে চিত্র পরিচালক হওয়ার জন্য আমি একটা ছ্যাঁকা খেয়েছিলাম। ঘটনাটা বলা দরকার। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবো তখন, পাকিস্তান আমল ছিল তো... আমাদের বাসায় নিচে চোক্তাই আর্ট বলে একটা আর্ট [দোকান] ছিল। ওদের কাজ ছিল সিনেমার পোস্টার আছে না, ওই যে ব্যানারগুলো বানানো। তখন তো হাতে [আঁকা] হতো, ওখানে, বিজয়দা বলে একজন ছিলেন, ওনার সাথে খুব খাতির ছিল। ওদের হাতে স্ক্রিপ্ট থাকত; ছবি দেখে দেখে নানান অঙ্ক দিয়ে তারা ছবি এঁকে ফেলত। আমিও ওখানে থাকতাম। এখানে একদিন চোক্তাই সাহেব এসে মাকে বললেন, ‘আমার এক আত্মীয় আছে পাকিস্তানে, সিরাজ খান, ও এখানে আসবে পানের ব্যবসা করতে।’ ও এসে মাকে ধর্ম মা বানিয়ে ফেলল। একটা পারিবারিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেল। উনি এখানে এলেন, মূলত পানের ব্যবসার আড়ালে... পশ্চিম পাকিস্তানে সুবিধা করতে পারেন নাই, এখানেও তো অনেকে ছবি বানাচ্ছে উর্দু ছবি—এ রকম একটা সাইড নিয়ে কিছু একটা করতে পারেন নাকি। উনি নিজেও এখানে যুক্ত হয়ে গেলেন।
এদিকে ৬৫/৬৭ সালেই আব্বা ওয়াপদায় আমাকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। আমার চাকরি হয়ে গেল। সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত চাকরি করতাম। তারপর যেতাম সুইট হ্যাভেন। এটা একটা চায়ের রেস্টুরেন্ট, এহতেশামের রেস্টুরেন্ট। ওখানে গিয়ে একটা পর্যায়ে আমি ম্যানেজারের চাকরি পেলাম। ওখানে আসত এহতেশাম। গুলিস্তান হাউস ছিল, পাশে সুইট হ্যাভেন রিজার্ভেশন। বাইরে পাওয়া যেত ছ’আনা কাপ চা। আর এখানে মূলত জড়ো হতেন নায়ক-নায়িকারা। শাবানা... এরা সবাই যেতেন সন্ধ্যার পরে, আড্ডা দিতেন। আমি ম্যানেজারি করতাম। আমি ওইখানে এই কারণে ঢুকেছিলাম যে, ওখানে, এই জায়গায় গেলে শেখা হবে আর কি। ম্যানেজারের ওইখানে বসার কোনো জায়গা থাকত না। সবচেয়ে মুশকিল হতো, ওখানে কয়লা দিয়ে রান্না হতো। হয়তো আমি উলটা দিকে তাকাই আছি, এমন হইত যে, হিসাব করতে হইত, ম্যামো করতাম। হয়তো কয়লা আনল, টাকা দিলাম কি দিলাম না, খেয়াল নাই; হিসাব করতে গিয়া দেখি টাকা মিলে নাই! কোনো একটা জিনিস হয়তো আনতে বলছিলাম, সেটা আনে নাই, পরের মাসে গিয়া হয়তো খেয়াল হইল। এ রকম শুধু এটা না, এ রকম আরও এটা সেটা-আনতে গিয়া হিসাব গরমিল হইত।
সেটা না, সবচেয়ে বড় ঘটল যে, সিরাজ একদিন সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়া মারা গেল। ড্রাইভ দিয়েছিলেন, মাথার মধ্যে আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু আব্বা বললেন যে, এটা হতেই পারে না, তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কিছু [লাশ] দেখতে দেয় নাই। উনি চলে গেলেন এভাবে।
’৭২ সালে আমি ওয়াপদার চাকরি-বাকরি, সবকিছু ছেড়ে ‘জোনাকি’তে গিয়ে প্রুফরিডার হিসেবে ঢুকলাম। সিনেমার পত্রিকা, যেখান থেকে একটা লাইন পাওয়া যাবে নিজের যোগ্যতায়। এখানে আবার সবাই আসত—হাসান আসত, নির্মলেন্দু গুণ আসত, গল্পটল্প করতাম। কিন্তু এখানে আমি বেশি দিন থাকি নাই। পরে গেলাম ‘ঝিনুকে’র কাছে। ওটাও সিনেমা পত্রিকা ছিল। ‘ঝিনুক’, ‘চিত্রকল্প’, ‘কামনা’ও—সিনেমা পত্রিকা। রাগারাগি করলাম। উনি [সম্পাদক] ছিলেন দজ্জাল লোক আর কি। উনি করতেন কি, পত্রিকার মধ্যে গসিপ ছাপাতেন। আসির উদ্দীন আহমেদ ছিলেন ‘ঝিনুকে’র সম্পাদক। আর ‘জোনাকি’র সম্পাদক ছিলেন আব্দুল মতিন। ওনার দাপট ছিল। উনি নাটক করেও বেড়াতেন। আমজাদ হোসেনসহ সবাই এখানে আসতেন, রহমান– এরা সবাই আসতেন। এমন কেউ বাদ নেই যে এখানে আসতেন না। তো, উনি গসিপ লিখতেন। ফলে হইত কি, আমি যে সাংবাদিক হইয়া যাইতাম, আমারে ডরাইত যে, আবার ভেজাল করে নাকি! আমারে দিছিল সমস্ত ইন্টারভিউ, হাবিজাবি যা আছে—ইনডোর, আউটডোর—সবই করতাম আমি।
অভিজ্ঞতা হল কি একবার। দেখলাম যে, খুবই বিরক্তিকর অধ্যায়। কেউ পাত্তা দেয় না, নায়িকারা বিশেষ করে। আমাকে বলা হলো শাবানার ইন্টারভিউ নিয়া আসতে। তো, গেলাম। এদিকে আবার শাবানারে নিয়া গসিপ করা হইছে আগেই। তো গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। তারপরেও গেলাম। গিয়ে খুব বিনয়ের সাথে বললাম। আমি তো জানি যে, সে পাত্তা দেবে না। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, ‘আপনি প্রশ্নগুলো লিখে দিয়ে যান। আমি উত্তর দেব। লিখে রাখব আমি, এখন আমার সময় নাই।’ এরপরে আমি কয়েকটা প্রশ্ন লিখে রেখে দিয়ে আসলাম।
তারপর আবার একদিন পরে গেলাম। যাওয়ার পরে উনি খুব অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললেন, ‘ভাই, আমার তো মনে নাই কাজের ব্যস্ততায়।’ কয়, ‘পরে...পরে আসেন।’ ইতিমধ্যেই তারিখ থাকে না, তারিখের অবস্থা শেষ।
গুরুদেব, মানে আবু শাহরিয়ার ছিলেন; একুশে পদক পেয়েছিলেন, কানে শুনতেন না। আমার প্রত্যাবর্তন মূলত ওনার হাত ধরেই। আমার লেখালেখি বলেন, প্রথম বই বের হওয়া বলেন—সবকিছুতেই ওনার একটা ভূমিকা ছিল। যাহোক, গুরুদেবকে গিয়া বললাম যে, ‘বিপদে পড়ছি।’ উনি বললেন যে, ‘দেখেন, ওরা তো এমন কিছু না। নিজে প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দিয়ে দেন, শুধু যেন ওদের বিরুদ্ধে না যায়!’ এরপরে আমি ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় যে কথা হয়েছিল, সেই কথাগুলাই লেইখা দিলাম। দিয়া আর ডরে ওইদিকে যাই নাই। যাই না এই কারণে, উনি [শাবানা] দেখলেই তো কইবো যে, উনি তো আসলে এত কথা কয় নাই। ‘চিত্রালী’ আছে, ‘পূর্বাণী’ আছে, ওগুলো সব দেইখা, ওগুলোর সাথে মিল রাইখা খাড়া করায়া দিছি আর কি!
এরপরে যেটা হলো, একদিন কামাল হাবিবের সেটে গেছি, দেখি যে উনি কাজ করছেন। উনি চোখ তুইলা আমাকে দেখল হয়তো, যদিও আমার অবস্থা অনেকটা কানাউল্লাহর মতো, সব সময় চশমা পরে থাকতে হয়। তার ওপরে লাইট পড়েছে, উল্টা দিকে আর দেখা যায় না। আমি উষ্টা খেয়ে পড়ে সামনে গিয়ে খাড়ায়া দেখি—আমার সামনে দিয়ে শাবানা বেরিয়ে আসছেন! এদিকে আমার ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, আমার আজকে অবস্থা শেষ। ওনার সাথে যখন দেখা হলো, তখন দেখলাম উনি হেসে মাথাটা নত করল। আমি কোনোরকমে ওখান থেকে বেরিয়ে আসলাম, দেখলাম যে, কিছু হয়নি আর কি।
সিনেমায় আমি শেষ মাইরটা খাইলাম রাজ্জাকের কারণে। আমি রাজ্জাকের আত্মজীবনী লিখতে গিয়েছিলাম। সিরাজুল ইসলাম, মিলনও [ইমদাদুল হক মিলন] এর সাথে জড়িত ছিল। আমি একটা পত্রিকা করেছিলাম ‘চিত্রকল্প’ নামে, সিনেমার পত্রিকা। আমি, সিরাজুল ইসলাম, মিলন ছিল আরকি। আমরা তিনজনে মিলে কয়েকটা সংখ্যা বেরও করেছিলাম। এটা করেছিলাম ’৭৮ সালের দিকে, শেষের দিকে এসে। ওটা বের করতে গিয়া, গোরা সেন—রাজ্জাকের বাল্যবন্ধু বলে তখন একটা লোক ছিল। ওই পার [ইন্ডিয়া] থেকে আইসা পড়ছে। ও [গোরা সেন] ছবি পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিল। যদিও হয়নি কিছুই। ওই সময় ব্যাংক ডাকাতি হতো। জাল চেক নিয়া, সই কইরা ব্যাংক থেকে টাকা তুইলা ফেলত। এই রকম দলের একটা লোকের সাথে আমার পরিচয় হলো। ও আমাকে প্রায় প্ররোচিত করত যে, ‘একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দিয়া দেন। আপনার তো বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা আছে।’ স্বভাবতই আমি প্ররোচিত হইনি।
একদিন গোরা সেন ধরা পড়ল এগুলো করতে গিয়া। ধরা পইড়া মাইর-টাইর খাইছে, আমার নামও জড়ায় পড়ছে। ভুলেও আমি তো এসব করি নাই। মাত্র বিয়া-টিয়া করছি। যাহোক, পুলিশ সাদাপোশাকে আইসা আমাকে ধইরা-বাইন্ধা ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিছে। এর মধ্যে আর কারও খবর নাই। পরের দিন সকালে আমি যখন নামছি, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অফিসাররা সব বসছে। তাকায়া দেখি চারপাঁচটা লোক, ওই যে আড্ডা দেই না নানান রকম—মঞ্চ ছিল, যেখানে বইসা আড্ডা দেওয়া হইত, তাস খেলা হইত, লেখালেখি হইত, পত্রিকা ছিল—ওই রকম আড্ডার কয়েকটা লোক। ওরা বলছিল, ‘স্যার, এটা কারে লইয়া আসছেন? এডা হইতেই পারে না।’ ওরা ছিল ইনফর্মার, বুঝতেই পারি নাই। যাহোক, ওরাও [পুলিশ] বুঝতে পারছে। তারপর আমাকে বললেন, ‘চলে যান, কোনো অসুবিধা নাই।’
সবকিছু মিলায় আসলে, আর আমিও দেখলাম যে, সিনেমায় আসলে চালু হইতে হয়। অথচ আমি দেখলাম যে ইনভেস্টমেন্ট বা আমার যে লাজুক স্বভাব—সব মিলায়ে ঠিকমতো এটা হওয়ার না আরকি। সিনেমা থেকে সরে গেলাম এভাবে। এখন ধরো, লেখাটা শেষ পর্যন্ত… নিয়েছি। আমি না ইদানীং, অন্য অর্থে নিয়ো না, এটা বলার জন্য না, খুবই ভয় পাই, কী নিয়া কথা বলব, সামনে কে আইসা পড়ে... খুব ডাক পইড়া গেছে আমার। মানে ব্যক্তি কেন জানি মনে করে যে, আমি বিরাট লেখক। কিন্তু আমি যখন নিজের লেখা পড়ি, পড়ে দেখি যে, আমার সঞ্চয়টা কম। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার চুল বা আমার বেশভূষা– এইটাই বেশি ইয়ে করে, মানে বুঝতেছ? মানে এইটাই হয়ে যায়। কিন্তু এখন মনে হয়, আমি যখন ‘টুকা কাহিনী’ লিখেছিলাম, তখন একটা আলোচনা বেরিয়েছিল—সম্ভাবনাময় তরুণ গল্প। লিটলম্যাগে বেরিয়েছিল। যাই করি হতাশ হলেও, এখন মনে হয় যে, সম্ভাবনা আছে আমার মধ্যেও।
৬৮ সালে, কায়েস আমাকে নিয়ে গেল বিউটি বোর্ডিংয়ে। সেখানে তখন কিন্তু আড্ডা হতো, সিনিয়ররা ছিল। আর নতুন প্রজন্মের হাসান [আবুল হাসান] বলো, নির্মলেন্দু গুণ বলো, কায়েস বলো, শাকের চৌধুরী মানে সমুদ্র গুপ্ত—কেউ বাদ নাই যে এখানে আসত না। লিটলম্যাগ বাংলাদেশে তখন যত বের হতো, সব আগে ওখানে আসত। তখন তো সব লিটলম্যাগ নির্ভর ছিল, দৈনিক পত্রিকা ওইভাবে ছিল না। ওখানে কায়েস একদিন নিয়া গেল। নিয়ে গিয়া পরিচয় করিয়ে দিল। দেখলাম যে, ওরা সবাই ওখানে বসে কবিতা পড়ছে, আবার মতামত দিচ্ছে—এই ধরনের পরিবেশ ছিল। তো, আমি ওদের সাথে মিশি। এর মধ্যে হাসানকে আমার বেশ ভালো লেগে গেল। উড়াইল্যা ভাব, দেখলাম যে চমৎকার। নির্মলকে দেখলাম, পরিচয় হলো।
রুদ্র: আপনি লেখালেখিতে সিরিয়াস হলেন কবে থেকে?
বুলবুল: এ প্রসঙ্গে ধ্রুব’র [ধ্রুব এষ] নামটা বলা উচিত। আমি সবকিছু হারাতে হারাতে…আমি চাকরি করেছি কমপক্ষে গোটা তিরিশেক, কোথাও আমার তিষ্ঠানো হয়নি। ব্যবসাও, প্রেসের ব্যবসা করছি এর মধ্যে, এ কাজ করছি চার-পাঁচবার, নানাকিছু করছি। দোকানদারিও করছি—স্টেশনারি, কনফেকশনারি। যাহোক, আমি একদিন দেখলাম যে, বাংলাবাজারে আইছি– মিলনের বই, হুমায়ূনের [হুমায়ূন আহমেদ] বই– এদের বই বিক্রি হচ্ছে। আমি তখন ছাপাখানার কাজ করি। আমাকে যেহেতু অনেকেই চেনে-জানে, সবাই বেশ ছাপাটাপা দেয়, ওদের বইও ছাপিটাপি। ভালো ভালো বই ছাপা হয়। দিনে পাঁচ হাজার বই ছাপা হচ্ছে, আমি ছাপায় যাচ্ছি। তখনই আমার ইচ্ছা হইল যে, আমিও একটা বই করি। এখন কই যাই? আমি গেলাম বিদ্যা’র [বিদ্যাপ্রকাশ] কাছে।
লেখালেখিতে আমি ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে সিরিয়াস হয়েছি। ’৮৮ সালে বইটা বেরিয়েছিল। বিদ্যার কাছে গিয়া বললাম, ‘আমার একটা বই আছে—‘টুকা কাহিনী’, ইতিমধ্যে সব গল্প লেখা হয়ে গেছে। আমার ছাপাখানা আছে, আমি ছাপায় দিবোনে, কম্পোজ করে দিবোনে।’ উনি [প্রকাশক] খুব গম্ভীর হয়ে বললেন যে, ‘পয়সা দিয়ে আমি কারও বই করি না।’ এদিকে আমি পয়সা পাই, পাওনা টাকাও চাইতে যাই না, আমি লজ্জায় পইড়া গেলাম। এইদিক-ওইদিক তাকাই। পরে হঠাৎ একদিন দেখা, উনি—মুজিবর রহমান খোকা—বিদ্যাপ্রকাশের প্রকাশক বললেন যে, ‘বুলবুল ভাই, আসেন, আমি তো খেয়াল করি নাই, আপনার ‘টুকা কাহিনী’ গল্পটা আমার পড়া হয়েছে, আমি আপনার বই ছাপতে চাই। একটা বই না, আপনি আমাকে চারটা বই দেবেন।’
খুবই কাণ্ড ঘটে গেল। ‘টুকা কাহিনী’ দিলাম। তারপরে ‘কহকাহিনী’ করলাম, কে জানি কাভার করল। তারপর ধ্রুবরে দেখলাম যে, ও এত কাভার করে, তো ওর কাছে আসলাম। চারটা বইয়ের মধ্যে তিনটা… ‘পাপপুণ্যি’ বলে একটা বইয়ের কাভার, বই নিয়ে ওখানে গেলাম। ও তখন হোস্টেলে থাকে। ‘পাপপুণ্যি’ বইয়ের বর্ণনা দিলাম। বলল, ‘আসেন।’ ওর এখন যে স্বভাব হইসে আউলাপনা! ওখানে গিয়া পাইলাম একদিন, কাভার করল। ছবি দেখাইলো।
কাভারটা হচ্ছে তোমার, ‘পাপপুণ্যি’ বইয়ের কাভার হচ্ছে—একটা মেয়ে, ন্যুডি আসলে তার ড্রয়িংটা, বাঁ হাতের উপরে কাত হয়ে মেয়েটা মাথাটা রেখেছে, ন্যুড হয়ে গিয়া পিছন দিকে ব্যাক কাভারে পা দুটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আর পায়ের কাছে চাঁদ। আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম যে, আমি তো লেখা লিখেছি একটা কিছু। আমি বললাম যে, ‘ধ্রুব, চাঁদ তো, আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা... চাঁদ তো কপালে থাকে!’ আমি বললাম, ‘আপনি যে চাঁদ পায়ের কাছে দিছেন?’ উনি বললেন যে, ‘বুলবুল ভাই, এ রকম মেয়ের পায়ের কাছেই চাঁদ থাকে।’ খুবই থমকে গেলাম। বাসায় গিয়া দেখি, সর্বনাশ! ‘পাপপুণ্যি’র যে গল্প লিখছি, দেখি যে নায়িকা চাঁদের মতো! চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু হয়া ওঠে নাই। কাটাকাটি করছি, এখনো ‘পাপপুণ্যি’ পইড়া আছে; এখনো মনে করি যে, এটা আবার করব আর কি। বিষয়টা ছিল আরকি। ওই আসলে পরে ঝুঁকে গেলাম আরকি।
আমার সে [ধ্রুব] বাসায় নিয়া যাইত। নিয়া রাখত বাসায়। নানান বিড়ম্বনা দিয়েছি। থাকার একটা ঘর দিয়েছিল। কাগজ-কলম দিত। খাবার দিত। বলতেন যে, ‘লেখো।’ এইভাবে যাত্রা শুরু হলো।
দ্বিতীয় পর্ব পড়ুন► আবুল হাসানের মৃত্যু আমোকে কাঁদিয়েছে!