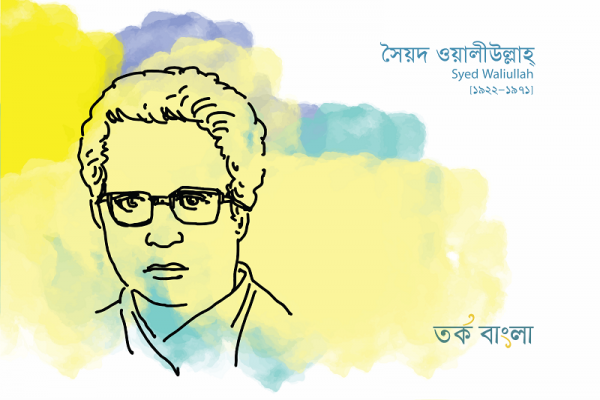
ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাসে আধুনিকায়নের মুসিবত
১
সময়কালের দিক থেকে ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খাঁটি পূর্ববঙ্গের লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস লালসালু ছাপা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে; কিন্তু লেখা হয়েছে আরো দু-এক বছর আগে। তৃতীয় ও শেষ বাংলা উপন্যাস কাঁদো নদী কাঁদো প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তার মানেই হল, তিনি এমন এক কাল-পরিসরে উপন্যাসচর্চা করেছেন, যখন কলকাতার সাথে ঢাকার একটা ভৌগোলিক বিচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু এ ভূখণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই।
ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর আধুনিক ধারণাসকল পরীক্ষা করেছেন পূর্ব বাংলার ঘোরতর গ্রামীণ জীবনে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণভাবে তাঁর জীবনদৃষ্টির বিভিন্ন মাত্রার সাথে গ্রামীণ জীবনের রীতিমতো বিরোধ আছে। কারণ, জীবন সম্পর্কে ওসব সিদ্ধান্ত মানুষ অগ্রসর নাগরিক জীবন থেকেই পেয়েছে। ওয়ালীউল্লাহ্র নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল—এমন সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর গ্রামলিপ্ততা ব্যাখ্যা করা সমীচীন হবে না। বাংলাদেশের সাপেক্ষে তাঁকে নগরবাসীই বলতে হবে। তাঁর রচনায়ও নগরজীবন উপস্থাপনার সার্থক নজির আছে। নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার জীবন ও বাস্তবতার সামগ্রিক উপস্থাপনার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর গ্রামলিপ্ততার কারণ।
আধুনিক জমানায় পশ্চিম বাংলার সাথে পূর্ব বাংলার বিকাশধারার গভীর পার্থক্য আছে। বিস্তারে না গিয়ে বলা যাক, কলকাতা যে অর্থে অনেক দূর পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে, ঢাকা সে অর্থে অতটা করে না। গত দু-তিন দশকের আগের অন্তত দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পূর্ব বাংলা আসলে এক বিস্তৃত গ্রামীণ কৃষকসমাজ। তার পরিচয় আছে গ্রামীণ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাপনায়, মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাধিক্যে এবং মুসলমান ধর্মীয় এলিটদের সমাজব্যবস্থাপনায়, নদী ও সবুজ-কবলিত পললভূমির বিন্যাসে। ওয়ালীউল্লাহ্র লেখায় এ পরিচয়ের নিখুঁত বিবরণী নাই, যেমন আছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখায়। কারণ, বাস্তবের সার্বিক উপস্থাপনা তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু নিজের বক্তব্যগত লক্ষ্য হাসিলের জন্য যে প্রেক্ষাপট বা পটভূমি তিনি এঁকেছেন, তাতে পূর্ব বাংলার নিপুণতম উপস্থাপনা আছে। ওয়ালীউল্লাহ্ বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার কথাশিল্পী।
এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কথাশিল্পীও বটে। ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তান আন্দোলন প্রজন্মের মানুষ। ওই আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। জিন্নাহর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। কথাটার তাৎপর্য এই যে, উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সংকট এবং বিশেষত পশ্চাৎপদ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংকট মোচনের জন্য তিনি দেশভাগকে জরুরি মনে করতেন। এ চিন্তার সাহিত্যিক প্রতিফলন দেখি তাঁর রচনাসমগ্রে। তিনি বিরামহীন বলে গেছেন বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর কথা, এঁকে গেছেন পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র। এই বাঙালি মুসলমান আবার বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার। তার প্রমাণ মিলবে গদ্যের চাল ও শব্দ নির্বাচনে এবং বিশেষভাবে নদীমাতৃক বাংলার রূপাঙ্কনে।
ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর আধুনিকতা। তিনি পাকিস্তান প্রকল্পের সাথে আধুনিকায়নের প্রকল্পের কোনো বিরোধ দেখেন নাই। ওই ফ্রেমের মধ্যেই পূর্ব বাংলার মানুষের জীবন নিয়ে আধুনিক সাহিত্য করা, এবং একই সাথে জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়নের প্রস্তাব উত্থাপন করা তিনি সম্ভবপর মনে করতেন। অপশ্চিমা দুনিয়া বিশেষত উপনিবেশিত অঞ্চলে আধুনিকতার প্রতি বরাবরই প্রকট মোহ ছিল। এখনো আছে। কারণে-অকারণে জীবনাচার আর শিল্পসাহিত্যের নানা চর্চাকে আধুনিকতার মোড়কে মূল্যবান করার বা ভাবার রেওয়াজ এসব অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের গরিব অঞ্চলে আধুনিকতা চর্চার আরেকটা ধরন আছে। পশ্চিমে বিকশিত ধারণাগুলোর অনুকরণমূলক ব্যবহারের কালে অপ্রস্তুত অনুসৃতি নানারকম ‘আধুনিক’ সঙ তৈয়ার করে। বলে রাখা দরকার, তত্ত্বীয়ভাবে হুবহু অনুকরণ অসম্ভব। কিন্তু অপরিচয়জনিত বিকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওয়ালীউল্লাহ্ এই দুই রকমের চর্চা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর আধুনিকতা মোড়ক বা লেবেল ছিল না। তিনি অপ্রস্তুতও ছিলেন না। পশ্চিমা আধুনিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম আসলে সেই শিক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক উদ্ভাসন।
একদিকে তিনি পূর্ব বাংলার ‘অনাধুনিক’ জনপদ ও জনগোষ্ঠীকে নিয়ে খাঁটি পশ্চিমা আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপন্যাস রচনা করছিলেন, অন্যদিকে আবার সে একই প্রক্রিয়ায় এই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়নের পথ-নির্দেশও করছিলেন। আমরা এ লেখায় খুব ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে এ আধুনিকায়নের এক মুসিবতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। বলে রাখা দরকার, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়নের ধারণার দিক থেকে সমসাময়িক বা পরের প্রজন্মের অন্য লেখকদের মনোভাব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। সেদিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্র এ দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা এখানকার প্রতিনিধিত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি।
কারণে-অকারণে জীবনাচার আর শিল্পসাহিত্যের নানা চর্চাকে আধুনিকতার মোড়কে মূল্যবান করার বা ভাবার রেওয়াজ এসব অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের গরিব অঞ্চলে আধুনিকতা চর্চার আরেকটা ধরন আছে। পশ্চিমে বিকশিত ধারণাগুলোর অনুকরণমূলক ব্যবহারের কালে অপ্রস্তুত অনুসৃতি নানারকম ‘আধুনিক’ সঙ তৈয়ার করে...
২
লালসালুর যুবকটির নাম আক্কাস। তাকে আমরা উপন্যাসে একবারই খুব সামান্য সময়ের জন্য দেখি। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান হিসাবে মজিদের যে-অসংখ্য প্রতিপক্ষ লেখক ও পাঠকের আনুকূল্য পেয়েছে, আক্কাস তার একজন। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে সে খুবই গৌণ। তবু আমরা এ লেখায় তাকেই চয়ন করলাম, কারণ যে ধরনের তিন যুবককে নিয়ে আমাদের কারবার, লালসালু উপন্যাসে সেরকম চরিত্র বলতে ওই এক আক্কাসই আছে।
আক্কাস বহুদিন বিদেশে ছিল। তার আগে, শোনা যায়, করিমগঞ্জের স্কুলে সে পড়াশোনা করেছে কিছুদিন। আবার পাটের আড়তে বা তামাকের আড়তে কাজ করে কিছু পয়সাও জমিয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। গ্রামে ফেরার পর সে কারণেই তার লাট-বেলাটের মতো ভাব। তার বাবা মোদাব্বের মিয়া ছেলে ফিরে আসায় খুশি হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে থিতু করে দিতে পারলে বাকি জীবনটা তসবি টিপে পার করা যাবে। বিয়ের প্রসঙ্গটা সামনে আসল কেন? মোদাব্বের মিয়া আক্কাসকে বিয়ে দেবার তাগিদ বোধ করেছিল ছেলের মতিগতি দেখে। ছোটবেলা থেকেই আক্কাস কেমন যেন ‘উচক্কা ধরনের’ ছেলে। কিন্তু এবার গ্রামে ফেরার পর থেকে সে নাকি গ্রামের মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে সুখের কথা, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাই তার বাবাসহ মুরুব্বিরা তার ব্যাপারে পুরা নিরাশ হয় নাই। তারা ভেবেছিল, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা খানিক গরম হয়েছে। দুদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।
কিন্তু আক্কাস গ্রামে স্কুল খোলার পরিকল্পনা করল। সে বলে বেড়াতে লাগল, স্কুলে না পড়লে মুসলমানদের মুক্তি নাই। এ কথাও সে বাইরে থাকার কালে শিখে এসেছে। মুরুব্বিরা তার এ উদ্যোগকে নিজের সাথে সাথে আরো অনেকের মাথা গরম বানানোর আয়োজন হিসাবেই দেখতে লাগল। তারাও শিক্ষার মর্ম বোঝে। এবং সে জন্য গ্রামে যথেষ্ট উদ্যোগও এর মধ্যে নেয়া হয়েছে। দু-দুটো মক্তব বসানো হয়েছে। কাজেই শিক্ষার প্রতি এ গ্রামে অবহেলার কোনো মনোভাব আছে, সে কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আক্কাস এসব যুক্তির ধার ধারে না। সে চাঁদা তোলার চেষ্টা করল। স্কুল করার জন্য সরকারের সাহায্য চেয়ে আবেদন পাঠানোর ব্যবস্থা করল।
এ অবস্থায় মজিদ আবির্ভূত হল রঙ্গমঞ্চে। ডাকা হয় বিচারসভা। সেখানে প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে মজিদ অকস্মাৎ আক্কাসকে তার বিখ্যাত প্রশ্নটি করে: ‘তোমার দাড়ি কই মিঞা?’ অপ্রসঙ্গকে প্রসঙ্গের কেন্দ্র করে তোলা সে প্রশ্ন থেকে আক্কাস আর বেরুতে পারে নাই। স্কুল প্রসঙ্গ পুরাপুরি ভেস্তে যায়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, গ্রামে একটা পাকা মসজিদ হবে।
লালসালু উপন্যাসের আক্কাসপর্ব এখানেই শেষ হয়। আমাদের বর্তমান আলাপের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আক্কাসকে যদি আমরা আধুনিকায়নের একজন দূত হিসাবে ধরি, তাহলে প্রশ্ন জাগে, তার রূপ বা স্বরূপ কী? একবার অন্তত সভায় ইংরেজি পড়ার কথা ওঠে। উপস্থিত সবাই একমত হয়, ইংরেজি শেখার ফলেই আক্কাসের এই অধোগতি। মুসলমান সমাজ একটা সময়ে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে নারাজ হয়েছিল—ইতিহাসের এটুকু সূত্র এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ওই গ্রামের মানুষদেরকে আমরা ওই নারাজ জনগোষ্ঠীর অংশ হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারি, যারা আধুনিকতার ছোঁয়া এড়িয়ে নিজেদের ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে চায়। এই পুরা ধারণাটা লালসালু উপন্যাসে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা এখানে কোনো কথা তুলব না। শুধু আধুনিকায়নের দূত হিসাবে আক্কাসের বাস্তবতা সংক্ষেপে পরীক্ষা করব।
আক্কাসের জাগতিক-মানসিক উন্নতির সাথে ওই গ্রামের কারো কোনো যোগ ছিল না। আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, তার চিন্তা ও চেতনা সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত। এমনকি পরেও সে গ্রামে তার কোনো সমর্থক জোগাড় করতে পারে নাই। লক্ষণ দেখে মনে হয়, সে সেরকম চেষ্টাও করে নাই, এবং তার মত-মতো উন্নতি করতে গেলে অন্যদের মানসিক সমর্থন দরকার—এরকম কোনো ভাবনাও তার ছিল না। লালসালুর পাঠকেরা ব্যতিক্রমহীনভাবে এ বাবদ মজিদকে দোষারোপ করেই আক্কাসের কাহিনি পাঠ করেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেউ তোলে নাই, ওই বিচারসভায় আক্কাসের পক্ষে কথা বলার মতো আর একজন লোকও কেন ছিল না। যদি না-ই থাকে, তাহলে আক্কাসের উদ্যোগের-যে একটা গভীর ও সর্বাত্মক জনবিচ্ছিন্নতা আছে, তা তো কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। উদ্যোগ যতই মহৎ আর আধুনিক হোক, জনগোষ্ঠীর সম্মতি ব্যতিত তার বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব? আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তাই আমরা পূর্ব বাংলার আধুনিকায়নের এক প্রতীকী উদ্যোগ হিসাবে পড়তে পারি, যেখানে স্থানীয় মাটি ও মানুষের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ধ্যান-ধারণা সম্মতির তোয়াক্কা না করে উড়ে এসে জুড়ে বসার আয়োজন করেছে। পদ্ধতির দিক থেকে এ সীমাবদ্ধতা কাটানোর কোনো চিন্তা ও চেষ্টা কোনো পক্ষে দেখা যায় নাই। আক্কাসের তরফে তো নয়ই, লেখককে যদি একটা পক্ষ ধরি, তাহলে তাঁর তরফেও নয়।
লালসালুর পাঠকেরা ব্যতিক্রমহীনভাবে এ বাবদ মজিদকে দোষারোপ করেই আক্কাসের কাহিনি পাঠ করেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেউ তোলে নাই, ওই বিচারসভায় আক্কাসের পক্ষে কথা বলার মতো আর একজন লোকও কেন ছিল না। যদি না-ই থাকে, তাহলে আক্কাসের উদ্যোগের-যে একটা গভীর ও সর্বাত্মক জনবিচ্ছিন্নতা আছে, তা তো কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়...
৩
চাঁদের অমাবস্যার সামাজিক পরিস্থিতি লালসালুর তুলনায় অনেক উন্নত। সেখানে শিক্ষিত ও দেশ-বিদেশ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষদের দেখতে পাই। স্কুল দেখি। আর স্কুলের আবহে পড়াশোনার চর্চাও দেখি। কিন্তু পরিবর্তিত এ পরিস্থিতি আধুনিকায়নের দিক থেকে অবস্থার বিশেষ উন্নতি নির্দেশ করে না। আমরা এখানে দেখব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজের আধুনিকায়নের প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করেছেন, এবং কেবল ইংরেজি বা অপরাপর শিক্ষার মধ্যে সীমিত না করে সচেতন হওয়া আর সেই সচেতনতাজনিত দায়িত্বশীলতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।
চাঁদের অমাবস্যার যুবক শিক্ষক কিভাবে এরকম চৈতন্য আর দায়িত্বশীলতায় উপনীত হয়েছে, তা খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু তা যে পশ্চিমাগত, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুত, পশ্চিমে উৎপাদিত সংজ্ঞা ও মনুষ্যোচিত গুণের তালিকাই তাকে চালিত করেছে। একটি উদাহরণ দিই। মৃত মাঝি-বউয়ের হত্যাকারী হিসাবে কাদের কোনোভাবে ক্ষমা পেতে পারে কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসায় আরেফ আলীর সবচেয়ে বড় নির্ভরতা ছিল ‘প্রেম’ নামক ব্যক্তিগত সম্পর্কের এক প্যাটার্ন। এখন, পূর্বদেশীয় সামাজিক তথা সামষ্টিক সম্পর্কের যে-কোনো বিবেচনাতেই বিবাহিত এই দুই নরনারীর প্রেম ‘অবৈধ’ এবং ‘অযৌক্তিক’। এমনকি আরেফ আলীও জানে, যে-সমাজে তার বসবাস এবং যে-সামষ্টিক জীবনবিধিতে বসে সে নৈতিকতার এক মহাবয়ানের রিহার্সেল দিচ্ছে, সেখানে এই রীতির প্রেম-ভালোবাসা একটা অচলিত ধারণা। সতর্ক ওয়ালীউল্লাহ্ যুবক শিক্ষকের মুখে প্রেমের বদলে ‘মায়ামহব্বত’ কথাটি বসিয়ে বাস্তবতার প্রাথমিক সূত্র রক্ষা করেছেন; আর প্রসঙ্গটি উত্থাপনের সময় তার মুখে ও ভঙ্গিতে লজ্জার রক্তিমাভা এঁকে দিয়ে বুঝিয়েছেন, মানবিক সম্পর্কের যে-ছকের উপর ভিত্তি করে সে জীবন-মৃত্যুর দায় বহনে সম্মত, সেই ছকটিতে সে নিজেই অভ্যস্ত নয়। বস্তুত পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নানা উত্তুঙ্গ মুহূর্তে তাত্ত্বিক-দার্শনিকভাবে নর-নারীর প্রেম মানবিক গুণ হিসাবে বিশিষ্ট মূল্য পেয়েছিল। তার সঙ্গে তুলনীয় কোনো সমরূপ বাস্তবতা আরেফ আলীর চারপাশে ছিল না। তবু-যে সে এই বস্তুতে এতটা দৃঢ় ইমান এনেছিল তার কারণ ‘মানুষ’ সম্পর্কিত এক বিশ্বজনীন ধারণা, যে-ধারণা পশ্চিমা হলেও তার ভঙ্গিটি বিশ্বজনীন, আর ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যই তার ভিত্তি।
এ উপন্যাসের ন্যারেটিভ কৌশল আর মননশীলতা অসাধারণ। যুবক শিক্ষক যেভাবে সমস্যাকে উপলব্ধি করে আর যে-পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তাতে এক বিন্দু ফাঁক নাই। ফাঁকি নাই। ন্যারেটিভ কৌশলগুলো ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারলে বোঝা যায়, কী নিরাসক্ত যুক্তির হিসাব-করা সিঁড়ি বেয়ে সে পৌঁছে যায় শেষ ধাপে! সমস্যা সাকুল্যে দুটো। এক. এই প্রাণবান যুবার পশ্চিমে পবিত্র মক্কা-সোনার মদিনা, উত্তরে ভারতমাতার পুণ্যধাম, আর পুবে পুরানা সভ্যতার কী বিপুল সম্ভার! এই বিশাল ভূমি, বিপুল জীবন আর দীর্ঘ ইতিহাসের একটা শ্লোকও এই গ্রহিষ্ণু তরুণকে আলোড়িত করল না! অন্যসব বিকল্প নির্মমভাবে পায়ে দলে সে নিঃসংশয়ে অবলম্বন করল পশ্চিমা পন্থা। দুই. পশ্চিমা কলাতেই তার ষোল আনা ইমান। কিন্তু সেই কলার সংজ্ঞায়ন সে করে নাই; কিভাবে এই মহিমা সে অর্জন করল তার এক বর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই। তার মানেই হল, মানব-অভিজ্ঞতার এক সর্বজনীন সংজ্ঞা মেনে নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ কথা সাজিয়েছেন। এ সংজ্ঞাগুলো উৎপাদিত হয়েছিল পশ্চিমে।
ওই সংজ্ঞাগুলোর বরাতেই সে অনায়াসে বাতিল করে দিল চারপাশের সম্ভাব্য সহায়ক শক্তিগুলোকে। দিতে বাধ্য হল। কারণ, তার আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়ের ধারণার সাথে ওদের কোনো মিল-ঝিল নাই। স্কুলের ধর্মশিক্ষক, দরবেশ বলে কথিত কাদের, আর তার আশ্রয়দাতা বড় সাহেব এভাবেই তার যাত্রাপথ থেকে একে একে ছিটকে পড়ল। তার আশ্রয় হল অন্ধকার কারাগারের নিঃসঙ্গ মোকাম। এ ঘটনার গভীর সব তাৎপর্য আছে। আমরা সেগুলোর কোনোটাকেই বাতিল করছি না। কিন্তু প্রশ্ন তুলতে চাই, যুবক শিক্ষক নিজের মন ও মর্ম অন্য কারো মধ্যে সঞ্চারিত করার কোনো উদ্যোগ-আয়োজন করেছিল কি? সে নিজে কিভাবে এই বিরূপ পরিবেশে গুণগুলো আত্মসাৎ করল, সে প্রশ্ন তো আছেই। কিন্তু সেটাকে যদি মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ বা সম্ভাবনা হিসাবে ব্যাখ্যা করি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে। তার মতো না হোক, কাছাকাছি মনের কোনো মানুষের হদিশও কিন্তু আমরা এ উপন্যাসে পাই না। তার মানেই হল, স্বভাবে ও পরিস্থিতিতে যতই আলাদা হোক, তার নিঃসঙ্গতাও আসলে অন্যভাবে আক্কাসের মতোই। তার প্রকল্পকে আধুনিকায়নের প্রকল্প হিসাবে না ধরার কোনো কারণ দেখি না। সেক্ষেত্রে এ প্রকল্পেও আরোপণমূলকতার মুসিবত থেকেই গেল। যাদের নিয়ে কারবার, তাদের সম্মতি উৎপাদনের কোনো চেষ্টা-তদবির দেখা গেল না। কাজেই আরেফ আলীর অভিযানও একদিক থেকে শুভকামনার মতো। ঠিক বাস্তবে ক্রিয়াশীল হওয়ার মতো কোনো উদ্যোগ নয়।
চাঁদের অমাবস্যার যুবক শিক্ষক কিভাবে এরকম চৈতন্য আর দায়িত্বশীলতায় উপনীত হয়েছে, তা খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু তা যে পশ্চিমাগত, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুত, পশ্চিমে উৎপাদিত সংজ্ঞা ও মনুষ্যোচিত গুণের তালিকাই তাকে চালিত করেছে। একটি উদাহরণ দিই। মৃত মাঝি-বউয়ের হত্যাকারী হিসাবে কাদের কোনোভাবে ক্ষমা পেতে পারে কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসায় আরেফ আলীর সবচেয়ে বড় নির্ভরতা ছিল ‘প্রেম’ নামক ব্যক্তিগত সম্পর্কের এক প্যাটার্ন...
৪
কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসের কুমুরডাঙাকে প্রতীক বা রূপক হিসাবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অঞ্চলটা যেভাবে নদীতে ছেয়ে আছে, তাতে কারো যদি নদীমাতৃক বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে, দোষের কিছু নাই। জায়গাটা গত শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের মফস্বল শহরের মতো করে সাজানো হয়েছে। সেখানে আমাদের নায়ক মুহাম্মদ মুস্তফা কাজ করে হাকিম হিসাবে। গরিবের পোলা হাকিম হয়েছে। জীবনটাকে তার চুষে-পিষে উপভোগ করার কথা। কিন্তু বেচারা কী এক অনুমেয় অথচ রহস্যময় কারণে ভূতের ভয়ে আক্রান্ত হয়। শেষতক নিজেকে কিছুতেই সামলাতে না পেরে ঝুলে পড়ে উদ্বন্ধনে। এরকম ঝুলে-পড়া আরেক হাকিম চরিত্র আমরা দেখেছি ওয়ালীউল্লাহ্র বিখ্যাত তরঙ্গভঙ্গ নাটকে। তবে তার পরিণতির একটা দার্শনিক অর্থ ছিল। মুহাম্মদ মুস্তফার ক্ষেত্রে তার দিক থেকে সেটা বলা মুশকিল।
মুহাম্মদ মুস্তফা শুধু গরিবের ছেলে নয়, গরিবির মধ্যেও একটা উৎকট আবহে সে মানুষ হয়েছে। তার বাবার যে-পরিচয় লেখক দিয়েছেন, অথবা পরিচয় দেবার জন্য যেসব ঘটনা বেছে নিয়েছেন, তাতে খুব সুষ্ঠু আবহের আভাস মেলে না। যে করেই হোক, মুস্তফা নিজের চেষ্টায় সে পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলতে পেরেছে। আসলে পেরেছে কি? একটা ছোট্ট যোগসূত্র দানবের মতো বিশাল রূপ নিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে গেছে ভিতরে-বাইরে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মেয়েটির নাম রেখেছেন খোদেজা। আরবদেশীয় জনৈক খোদেজা এক যুবকের তুমুল প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, আর পূর্ববঙ্গীয় খোদেজা মুহাম্মদ মুস্তফার জন্য ডেকে আনল মৃত্যু—এ ধরনের কোনো দূরাভাষ কি এ নামকরণের কালে ওয়ালীউল্লাহ্র মনে ছিল? জানার কোনো উপায় নাই। আমাদের জন্য তা খুব দরকারিও নয়। তবে দেখতেই পাচ্ছি, একেবারেই অনিচ্ছায় খোদেজা নিজের জীবন দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবন দেয়ার কারণ হয়ে উঠল।
মুস্তফার মধ্যে আক্কাসের মতো কিংবা আরেফ আলীর মতো আধুনিকায়নের কোনো উদ্যোগ-আয়োজন দেখি না। কিন্তু তার নিজের উত্থানকে আমরা বে-এলেম গ্রামীণ জনপদের এক ধরনের আধুনিকায়ন হিসাবে পড়তে পারি। আগের দুজনের সাথে তার এক জায়গায় মিল ষোল আনা। তারও সঙ্গী-সাথী বিশেষ দেখা যায় নাই। নিজের পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনপদেও নয়, কুমুরডাঙার কর্মস্থলেও নয়। এই নিঃসঙ্গতাকে কি পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবেশ থেকে ক্বচিৎ বেড়ে ওঠা দুই-একটা শিক্ষিত যুবকের নগরবাসী হওয়ার মধ্য দিয়ে আগের জীবনের সাথে বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন হিসাবে পড়া যায়? হুবহু পড়ার দরকার নাই। বিশেষত মুস্তফার ক্ষেত্রে দেখছি, তাকে তার পূর্বতন জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত রেশ একেবারে ছেড়ে যায় নাই। বলতে পারি, চারপাশের সাথে সঙ্গতিহীন তার নিঃসঙ্গ যাত্রাই তার বিনাশের কারণ হয়েছে।
৫
ওয়ালীউল্লাহ্র তিনটি উপন্যাসের এই তিনটি চরিত্রের কর্মকাণ্ড ও পরিণতি বাংলাদেশ অঞ্চলের আধুনিকায়নের এক গভীর মুসিবতের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখানকার আধুনিকায়নের উদ্যোগ-আয়োজন এবং ধারণাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরোপণমূলক। জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তর সাক্ষ্য ও অংশগ্রহণের কোনো চিন্তা এসব আয়োজনে দেখা যায় না। তত্ত্বীয়ভাবেও নয়, পদ্ধতিগতভাবেও নয়। কাজেই আধুনিকায়নের প্রকল্পগুলো কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। আর সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক জনগোষ্ঠী দেশের বিপুল অধিকাংশ মানুষের পশ্চাৎপদতা নিয়ে বিরামহীন গালিগালাজ করে গেছে। শিখা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড এ ধরনের আধুনিকায়ন-চেষ্টার প্রথম বড় ও সমন্বিত উদ্যোগ। মার্কসবাদী তৎপরতাও এর মধ্যেই পড়বে। তৃতীয় ধারাকে বলতে পারি সেক্যুলার ও উদারনীতিবাদী প্রচারণা। প্রতিটিই প্রায় একই ধরনের আরোপণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে আজ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এ ধারার বড় কোনো বদল ঘটে নাই। আধুনিকায়নের মুসিবতও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে কমে নাই।
তুলনায় ওয়ালীউল্লাহ্ আসলে তাঁর আরোপণমূলকতা এবং পশ্চিম-নির্ভরতা সত্ত্বেও এ প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি সতর্কতা দেখিয়েছেন। লালসালুর আক্কাস, চাঁদের অমাবস্যার আরেফ আলী এবং কাঁদো নদী কাঁদ’র মুস্তফাকে বাংলাদেশের তিন প্রজন্মের গ্রামীণ মধ্যবিত্ত হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তিনজনই আসলে নিজ নিজ প্রকল্পে ব্যর্থ হয়েছে। মতাদর্শিকভাবে ওয়ালীউল্লাহ্ এদেরই পক্ষাবলম্বী; কিন্তু বাস্তবতা হল, বিপুল অধিকাংশ মানুষের সাথে এতটা দূরত্বে থেকে কোনো প্রকল্প সার্থক হতে পারে না। বাস্তবতার সীমা গভীরভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ এভাবে নিজের প্রকল্পকেই বিসর্জন দিলেন, বলা যায়, বাস্তবের অনুরোধে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন। বাংলাদেশের বাস্তববাদী আর মার্কসবাদী লেখকদের সমধর্মী চরিত্রের সাথে তুলনা করলেই বোঝা যাবে, ওই লেখকদের রোমান্টিসিজমের বিপরীতে ওয়ালীউল্লাহ্ কী গভীরভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতা অঙ্কন করতে পেরেছেন। ওই সীমাবদ্ধতা-যে তাঁর অনেক পরের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যর্থ হচ্ছেন, তা হয়তো বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুব সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

ঐসময়ের পূর্ব বাংলার সমাজবাস্তবতার জন্য আক্কাস জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, ওয়ালীউল্লাহর লালসালু উপন্যাসে এটা একটা মুসিবত মনে হয়েছে আপনার কাছে। ধরুন,আক্কাস একবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজপতিদের আদর্শগত রোষানলে পড়লে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেটা অতিক্রম কতোটা সম্ভব হতো? আমার মনে হয়, জনগণকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব অবশ্যই আছে, সাথে রাজনৈতিক পাঠের একটা ব্যাপার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে,ফলে একবিংশ শতাব্দীতেও আক্কাসের মতো মানুষের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু হয়!
মেজবাহ উদ্দিন
জুন ০২, ২০২১ ০০:২৭

মোহাম্মদ আজমের সাহিত্য পাঠের মধ্যে একটা রাজনীতি আছে। তাঁর নিজের সেই রাজনীতি বোধের প্রতিফলন থাকে তাঁর লেখায়। সর্বদা তাঁর রাজনীতি বোধ আমাকে স্বস্তি দেয় না; তা সত্ত্বেও আমাকে তিনি ভাবিয়ে তুলতে পারেন। ফলে তাঁর লেখা আমি সাগ্রহে পড়ি। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের মতোই এটিও নতুন প্রশ্ন তোলার সামর্থে্যর কারণে আমাকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলাদেশের লেখকদের উপন্যাসগুলোর অধিকাংশই আধুনিক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এ প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের উপন্যাসকাররা তাঁদের উপন্যাসে মূলত সমাজের ছবিই এঁকেছেন। খুব সামান্য যে দু-এক জন ব্যতিক্রম রয়েছেন তার মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পড়েন। মোহাম্মদ আজম সেই ওয়ালীউল্লাহ-র আধুনিকতারও সাধারণ এক সমস্যা আবিস্কার করেছেন। তার মানে কি এই যে, বাংলাদেশের সমাজে ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর পরের তিরিশ চল্লিশ বছরের ঔপন্যাসিকেরা যথার্থ ব্যক্তিকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে পারেননি? আর এর কারণ কি বাংলাদেশের সমাজে ব্যক্তির সামাজিক ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠা? আর ব্যক্তির এই গড়ে না ওঠার পেছনের কারণও কি ব্যক্তির সামাজিক ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠা? আশা করি মোহাম্মদ আজমের পরবর্তী কোনো প্রবন্ধে এর এক রকম উত্তর পাব।
আহমাদ মাযহার
জুন ০২, ২০২১ ০৮:২৭


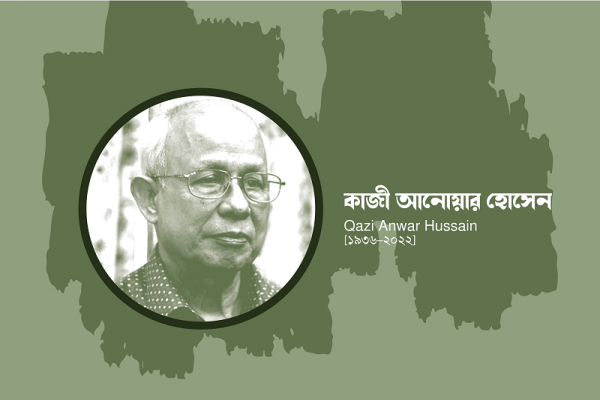
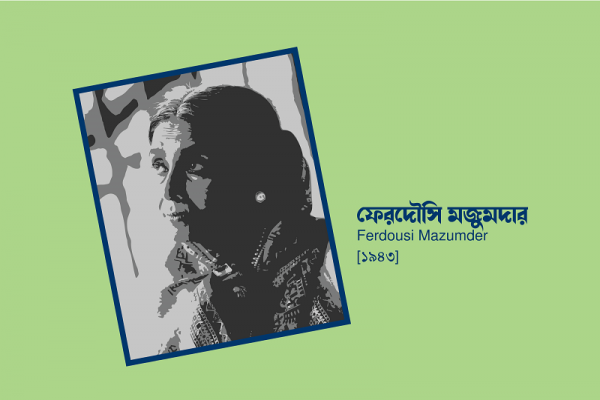
Extraordinary!
Md mustafizur rahman
জুন ০১, ২০২১ ১৬:০৬