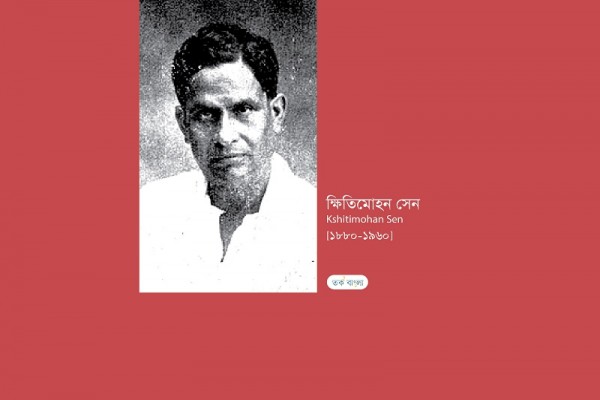
অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিতে মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন
১৯৪১ সালে অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেন যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা করতেন, তখন তাঁদের বাড়ি ছিল ঢাকার পুরোনো ও ঐতিহাসিক অঞ্চল ওয়ারীতে। এবং তাঁর বাবা-মা ঢাকায় খুবই আনন্দে ছিলেন, তিনি ও তাঁর বোন মঞ্জুও তাই। তিনি তখন সেন্ট গ্রেগরিজ-এর ছাত্র। যদিও সেন্ট গ্রেগরিজ-এর কড়া পরিবেশ তাঁর পছন্দ ছিল না। এবং বিদ্যালয়ে তার ফলও খুব খারাপ ছিল। তবু তিনি ও তাঁর বোন মঞ্জু তাঁদের ঢাকার বাড়িটা খুব পছন্দ করতেন। এমতাবস্থায় কেন তাঁকে তাঁর মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে থাকতে পাঠানো হলো?
এর পেছনে কারণ ছিল দুটি।
তখন পর্যন্ত প্রধান কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে জাপানি সেনারা বার্মা দখল করে নেওয়ার পর তাঁর বাবা-মা তাঁকে দাদু-দিদিমার সঙ্গে থাকার জন্য ও সেখানকার স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যদিও তাঁর বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, যাতে তিনি সেন্ট গ্রেগরিজ-এ লেখাপড়া চালিয়ে যান। কারণ, যেসব দিক থেকে লেখাপড়ার মান বিচার করা হয়, সেসব দিক থেকেই এই স্কুল খুবই বিশিষ্ট ছিল। তবে মি. সেন ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে জাপানি সেনারা কলকাতা আর ঢাকায় দুটো শহরেই বোমা ফেলবে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের মতো প্রত্যন্ত জায়গার খোঁজ তারা রাখবে না। অন্যদিকে অমর্ত্য সেনের মা অমিতা চাইতেন, তাঁর ছেলে যেন তাঁর মতো শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করে। অমর্ত্য সেনের মা অমিতা কেবল শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন তা-ই নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্যগুলোতে নিয়মিত মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অদ্ভুতভাবে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি একেবারে গোঁ ধরে বসেন। কিন্তু তাঁর বাবা যেহেতু চাইতেন না, ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে শান্তিনিকেতনে দাদু-দিদিমার সঙ্গে থাকুক, তাই তাঁর যাওয়াটা হচ্ছিল না। তবে যুদ্ধ তাঁর মায়ের এই চাওয়াটাকে সুগম করে দিয়েছিল। যে কারণে তাঁর মতে, তিনি শান্তিনিকেতনের মতো একটি অসামান্য প্রগতিশীল স্কুলে পড়তে পেয়েছিলেন, যেখানে ‘এটাই করতে হবে’, ‘অন্য কিছু করা যাবে না’ ‘খবরদার’ বলে কিছু ছিল না। সেন্ট গ্রেগরিজ-এ জীবনে ‘শাইন’ করতে হবে বলে যে চাপের মধ্যে থাকতে হতো, এখানে সে চাপ উধাও। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় তাঁর স্কুলের দিনগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই সম্পূর্ণ আলাদা, নতুন ধরনের স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
এখানে যেভাবে পড়ানো হতো, তার মধ্যে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সারা পৃথিবীর নানা দেশ ও তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে হতো। প্রতিযোগিতাভিত্তিক উৎকর্ষের বদলে শান্তিনিকেতনের এই স্কুলে জোর দেওয়া হতো ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু করে তোলার ওপর। বস্তুত পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট ও ফার্স্ট, সেকেন্ড হওয়ার মতো ব্যাপারগুলোকে নিরুৎসাহিত করা হতো। শান্তিনিকেতনের তালাচাবি মুক্ত লাইব্রেরির রাশি রাশি বইগুলো ঘাঁটতে তাঁর দারুণ লাগত। মূলত ভালো রেজাল্টের চিন্তা করতে হবে না, এটা তাঁকে একধরনের প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। এবং অতি অবশ্যই ছিল দাদু ক্ষিতিমোহন সেনের সান্নিধ্য।
১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদার সিতিকণ্ঠ সিংহ রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথকে একটি জমি দান করেছিলেন। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই জমি দান করার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেবেন্দ্রনাথকে এমন একটা জায়গা দেওয়া, যেখানে বসে তিনি চিন্তা ও ধ্যান করবেন। তবে দেবেন্দ্রনাথ এই জমি নিয়ে বিশেষ কিছু করেননি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নেন, ওই জমিতে তিনি স্কুল তৈরি করবেন। এবং ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন বিদ্যাকেন্দ্র বিশ্বভারতী। যার লক্ষ্য বিশ্বের জ্ঞানচর্চা। রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, তাতে বহুপরিচিত মানুষ এবং বন্ধুবান্ধবের উপযুক্ত সাহায্য পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে সে সময়ে বহু ক্ষেত্রের বহুগুণী মানুষ রবীন্দ্রনাথের টানেই তাঁর ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই অর্থে দেখতে গেলে ভারতের মাপকাঠিতেও এখানকার শিক্ষকেরা অনেকটাই স্বল্প বেতনে কাজ করতেন। তাঁরা এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে, তাঁর চিন্তাভাবনায় সহমত হয়ে। এই দলটায় দেশ-বিদেশের অনেক স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন, সিলভাঁ লেভি, চার্লস অ্যান্ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়ারসন ও তান-উইন-শান এবং লেনার্ড এলমহার্স্ট। এ ছাড়া ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের মতো পণ্ডিত ও নন্দলাল বসুর মতো চিত্রশিল্পী। যিনি চিত্রশিল্পী ছাড়াও ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষক।
নতুন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে রবীন্দ্রনাথ কেন ক্ষিতিমোহন সেনকে যুক্ত করতে এত উৎসাহী হয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনের কথা শুনেছিলেন তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী কালীমোহন ঘোষের কাছ থেকে। কালীমোহন রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়াও গ্রামীণ পুনর্গঠন ও সংস্কারকাজে যুক্ত ছিলেন। কালীমোহনের কাছে ক্ষিতিমোহনের কথা শোনার পর তিনি নিজেই তাঁর সম্বন্ধে আর একটু খবরাখবর নিলেন। ক্ষিতিমোহন সেনের বিদ্যাচর্চার বিস্তৃতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণির সঙ্গে গভীর একত্ববাদের কথা জানার পর তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছিলেন, ‘তিনি যদিও প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, এই ঔদার্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেছেন। হিন্দু ধর্মকে যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ করে অপমানিত করেন, এঁর দৃষ্টান্ত হয়তো তাদের প্রভাবিত করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার পক্ষে তিনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।’
১৯০৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ক্ষিতিমোহনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন ‘আমার একজন সহযোগী ভীষণ প্রয়োজন’ এবং ক্ষিতিমোহনের দ্বিধার কথা জেনে এটাও জুড়ে দেন ‘আশা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না’। তবে ক্ষিতিমোহনকে একটা বড় সংসারের ব্যয়ভার বইতে হতো। যার মধ্যে কেবল তাঁর নিজের সন্তান নয়, তাঁর মৃত বড় ভাইয়ের দুই পুত্রও ছিলেন। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে মাইনেও খুব কম ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে দেশীয় রাজ্য চাম্বার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে একটা ভালো চাকরিও শুরু করেছিলেন। সেখানকার রাজা ভূরি সিং-এর সঙ্গে তাঁর খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। সেখানে নিয়মিত যে ভালো বেতন পেতেন, সেটা ত্যাগ করতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর লেগে রইলেন ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনে আনার জন্য, এবং এই আশ্বাসও দিলেন যে তাঁর সংসার প্রতিপালন করার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করবেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনে আসতে রাজি করাতে পেরেছিলেন। এবং ক্ষিতিমোহন এখানে ৫০ বছরের বেশি সুখী ও ফলবান সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনই উল্টোটাও ঘটেছিল। তিনিও রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।
ক্ষিতিমোহন বারানসীর কুইনস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তবে তিনি অনেক বেশি সময় কাটাতেন বারানসীর সংস্কৃত শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী চতুষ্পাঠীগুলোতে। অনেক পরে তিনি শাস্ত্রীয় বিদ্যার সংরক্ষণ ও প্রসারে তখনো খুবই জীবন্ত এই কেন্দ্রগুলোর ভূমিকার কথা এবং আধুনিকতার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বিলুপ্তির ট্র্যাজেডির কথা লিখেছিলেন। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি বহু কাঙ্ক্ষিত ‘পণ্ডিত’ উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। তবে সাহিত্য এবং ধর্ম সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের ক্রমশ বেড়ে চলা কৌতূহল তাকে প্রগতিবাদী করে তুলেছিল। যা একজন রক্ষণশীল হিন্দু হিসেবে ক্ষিতিমোহনের পিতা ভুবনমোহনকে একটু ব্যথিত করেছিল। ভুবনমোহনের আশঙ্কা ছিল ক্ষিতিমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস হয়তো বা পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে উঠবে এবং তা যাতে না হয়, সে জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ক্ষিতিমোহনের চিন্তাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথে। তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু ভক্তি সাহিত্য এবং মুসলমান সুফি সাধকের কবিতা ও সঙ্গীতে। এ জন্য তিনি ফারসিও শেখেন তাঁর দাদা, ফারসিতে সুপণ্ডিত অবনীমোহনের কাছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ক্ষিতিমোহন কবীর পন্থায় দীক্ষা নেবেন বলে স্থির করেন। কবীরের বহুত্ববাদী সাধনার ধারায় উদারভাবে মিলেমিশে ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাব। আর এই সংমিশ্রণ থেকে উৎসারিত অপরূপ সব গান ও কবিতা বহু শতাব্দী ধরে চর্চিত হয়ে আসছে। কবীরপন্থীদের দলে যোগ দেওয়া নিতান্তই আনুষ্ঠানিক একটি ঘটনা, আসলে এই ধারার ঔদার্যের ছায়ায় তিনি স্বাধীনভাবে নিজের অগ্রাধিকার স্থির করবেন। কবীর পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি এক মুসলমান পরিবারের জন্মেছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই ভাব ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে ধনসম্পদ গ্রহণ করেছেন। [মনে করা হয়ে থাকে যে কবীরের জন্ম ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এটা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।]
ভুবনমোহন যে পুত্রের এই দীক্ষা অনুমোদন করতেন না, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে ক্ষিতিমোহন এই ঘটনা নিয়ে পরিহাসের ছলে লিখেছিলেন, ‘আচার রক্ষার জন্য চারিদিকে কঠোর ব্যবস্থা কিন্তু তাহারই মধ্যে আমার জীবন বিধাতা হাসিয়াছিলেন। আচারের রাজ্যে বিপদ দেখা দিল কিন্তু তাহা ইংরাজের তরফ হইতে নহে’। ক্ষিতিমোহনের বদলাতে থাকা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের অগ্রাধিকারগুলোও পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। ১৮৯৭ সালে চাম্বা যাওয়ার ১০ বছর আগে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি কবীর, দাদু এবং এদের মতো হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের অন্যান্য সাধকদের কবিতা ও গান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা প্রান্তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যে এলাকাটি তিনি ঘুরেছিলেন সেটি আয়তনে বিশাল; কারণ, কবীর ও অন্যান্য সন্তদের অনুগামীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতে নানা প্রান্তে। এইসব ঘোরাঘুরি এবং সেগুলো বিস্তারিতভাবে লিখে রাখার কাজে ক্ষিতিমোহনকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। ক্ষিতিমোহনের সহকর্মী এবং পারিবারিক বন্ধু বিখ্যাত বাঙালি লেখক ও পন্ডিত সৈয়দ মুসতবা আলী জানিয়েছেন, ‘শাস্ত্রবিশারদরা যে বৈজ্ঞানিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করে থাকেন, ক্ষিতিমোহন সেই নিষ্ঠার সঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত গ্রামীণ গাথাগুলিকে পড়তেন এবং বিশ্লেষণ করতেন।’
ক্ষিতিমোহনের প্রাচীন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমী ধরনের নিবিড় পরিচয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় নিয়ে আসতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আশ্রমে থাকাকালীন তাঁর লেখা বেশ কিছু বই প্রাচীন শাস্ত্রগুলোর এত দিন পর্যন্ত চলে আসা ভাষ্যগুলোর জায়গায় উদার পাঠের দরজা খুলে দেয়। তাঁর লেখার মধ্যে এমন সব বিষয় গুরুত্ব পায়, যেগুলোর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় কীভাবে ভারতীয় সমাজে নানা সামাজিক অন্যায় এবং জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য চলে এসেছে, এবং প্রাচীন ধর্মীয় ও শাস্ত্র গ্রন্থগুলোর বিকৃত পাঠ থেকে এই সব অন্যায়ের সমর্থন জোগাড় করা হয়েছে। তিনি প্রাচীন রচনাগুলোর একটি পূর্ণতর পাঠের মাধ্যমে এই কুপ্রথাগুলোর প্রকৃত স্বরূপটা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

অমর্ত্য সেনের মতে, তিনি বিশ্বাস করতেন এসব সামাজিক অন্যায্যতা যদি শাস্ত্র থেকে সত্যি সত্যি অনুমোদন পেতও, তাহলেও ক্ষিতিমোহন এগুলো সমর্থন করতে না। এ নিয়ে মি. সেন কয়েকবার তাঁর দাদুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। এবং তিনি নাতনির সঙ্গে এ বিষয়ে অমত করতেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতেন, ‘এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে এই সব অন্যায় শাস্ত্রগুলোর নিম্নমানের ব্যাখ্যা, বিকৃত পাঠ আর কিছু অংশের পক্ষপাতদুষ্টভাবে বেছে নেওয়া পাঠ থেকে সমর্থন পেয়েছে।’ সামাজিক অন্যায়গুলো যে কেবল শাস্ত্রের বিকৃত পাঠ থেকেই উদ্ভূত নয়, এই বাস্তব স্বীকার করে নিয়েও তিনি মনে করতেন, এইসব অপব্যাখ্যা সংশোধন করার একটা দায় থেকেই যায়। তাঁর বহু পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা করে লেখা বই জাতিভেদ-এ তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীরা সমাজের যে স্তরবিন্যাস করেছেন সেটির শাস্ত্রীয় ভিত্তি কতটা দুর্বল। ভারতের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতটা স্বাধীন ছিলেন এবং ধীরে ধীরে মধ্যযুগে ও সমকালীন ভারতে কীভাবে সেই স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নারী বইতে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ভারতের সংস্কৃতি বইতে নানা বিষয়ের সঙ্গে তিনি এটাও দেখিয়েছেন, কীভাবে হিন্দু শাস্ত্রের নির্মাণে ধর্ম, জাতি, শ্রেণি, গোষ্ঠী, লিঙ্গনির্বিশেষে নানা উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। এসব রচনা তাঁর শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা অনুযায়ী ক্ষিতিমোহন আশ্রমের সংস্কৃতচর্চায় পরম্পরাগত সেকেলে রক্ষণশীলতা বেশ খানিকটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষিতিমোহন যে তাঁর প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রবিষয়ক ধারণা এবং একই সঙ্গে লোকায়িত ধর্ম, বিশেষ করে গ্রামীণ কবিতা ও সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রতীতি এত বিস্তৃত করে তুলতে সাহায্য করবেন, তা রবীন্দ্রনাথ আশা করেননি। এর পেছনে ছিল কৈশোর থেকে কবীর থেকে শুরু করে এই ধারার ঐতিহ্য নিয়ে ক্ষিতিমোহনের পড়াশোনা ও সংগ্রহ, যা বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহে ক্ষিতিমোহন কবীর, দাদু এবং অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গ্রামীণ কবীর রচনা সংকলন ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে শুরু করেন।
কবীরকে নিয়ে ক্ষিতিমোহনের কাজটা ছিল, পাঁচশো বছর আগেকার এই রচনাগুলো কবীরপন্থী সাধক ও কবিদের মুখে মুখে প্রচলিত হতে হতে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী পদগুলো সংগ্রহ করা। তাঁর চার খণ্ডের কবিরের রচনা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০-১১তে, তিনি আশ্রমে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। ক্ষিতিমোহন হিন্দুধর্মের ধ্বংসাত্মক দিক এর পরিবর্তে সৃজনশীল দিকটি, বিশেষত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে নির্মিত উদার ও সহনশীল ভাষ্যই যে কেবল রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে গ্রামীণ সাধকদের আপাতসরল বক্তব্যর মধ্যে প্রচ্ছন্ন পরিশীলনের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ভক্তি আন্দোলন আর ইসলামি সুফি ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুর মতো এই প্রাচীন কিন্তু জীবন্ত কবিতাগুলোর অসাধারণ সারল্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ক্ষিতিমোহনের সংকলন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ইভলিন আন্ডারহিল-এর সহায়তায় ইংরেজিতে ওয়ান হান্ড্রেড পয়েমস অব কবীর প্রকাশ করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দুই বছর পরে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থ। ক্ষিতিমোহনের সংকলনের ভিত্তিতে এজরা পাউন্ড কবীরের ইংরেজি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর করা কয়েকটি তরজমা প্রকাশিত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ণতর সংকলনটি প্রকাশ করে উঠতে পারেননি।
কোনো কোনো সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, ক্ষিতিমোহন কবীরের যে অনুবাদ করেছেন, তা সব সময়ে অন্য যেসব সংস্করণ পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে হুবহু মেলে না কেন? মূলত কবিরের রচনার একাধিক পাঠ তো পাওয়া যায়। তা নিয়ে অবাক হওয়ার কারণ নেই। কবি নিজে কিছু লিখে যাননি, এবং সংগ্রহকারীর ভূমিকায় ক্ষিতিমোহনের মনে হয়েছিল যে সমকালে যে রচনাগুলো যেভাবে মুখে মুখে প্রচলিত বা গীত হচ্ছে, সেগুলো সেভাবেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। আগের সংগ্রাহকেরা ভিন্ন কোনো পাঠ, যা সম্ভবত তাঁদের সময়ের মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল, সেগুলোকেই কোনো না কোনো সময়ে লিখে রেখেছেন। বহু শতাব্দী আগের এক মৌখিক ধারার কবীর রচনার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যাচ্ছে এটা খুব বিস্ময়কর নয়। বরং মৌখিক ধারার একাধিক পাঠ থাকাটাই প্রত্যাশিত। তবে ক্ষিতিমোহন মনে করতেন, বেশির ভাগ সংগ্রাহক চলমান অনুশীলনের জীবন্ত ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে, মুদ্রিত বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শুধু এই নয় যে এই সময়ে কবিরের গানের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, এটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্ষিতিমোহন ধারাবাহিকভাবে সেই সব পাঠকে গুরুত্ব দিয়েছেন যেগুলো এখনো বহু ক্ষেত্রে সমাজের একেবারে নিচতলায় কবিরের অনুগামীদের মুখে মুখে ঘোরে, এবং যে সংস্করণগুলো তিনি নিজ কানে শুনেছিলেন। গবেষণা পদ্ধতির নিরিখে ক্ষিতিমোহনের চর্চার সঙ্গে এখন যাকে ‘নিম্নবর্গের চর্চা’ বা ‘সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ’ বলা হয়, তার অনেক সাযুজ্য আছে। সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের প্রতি অভিজাতদের পক্ষপাতদুষ্ট অবহেলার কারণে অনেক সময় সংগ্রাহকদের তথ্য-উপাত্তে অসঙ্গতি দেখা যায়।
ক্ষিতিমোহন মনে করতেন, কবীর, দাদু এবং এদের সমগোত্রীয়দের সৃষ্টিশীলতা বুঝতে হলে, এভাবেই দেখতে হবে। কারণ, তাঁরা মুখে মুখেই রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মধ্যবর্তিতায় বিদেশে আরও অনেক বুদ্ধিজীবীও এই পদ্ধতি পছন্দ করেছেন। যেমন ফরাসি লেখক রম্যাঁ রলাঁ। কবীর, দাদু এবং বাউলদের রচিত মৌখিক সাহিত্যে ক্ষিতিমোহনের উৎসাহের কারণ কী? এর একটা কারণ হলো ভারতের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারটি যেভাবে অভিজাতদের পক্ষপাতে অবহেলিত হয়ে এসেছে, সেই অবিচার দূর করার ইচ্ছা। অন্য কারণটা হলো, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ইতিহাস নিয়ে তার গভীর ঔৎসুক্য। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। সর্বোপরি ১৯৪০-এ চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার পরিবেশে প্রকাশিত হয়েছিল তার উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থ, 'ভারতের হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা'।
ভারতে অসন্তোষ ও হিংসা ছড়াতে, এবং ধর্মীয় বিভাজন পোক্ত করতে মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের একটা বিরাট ভূমিকা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি যেহেতু বাঙালি সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমান যোগাযোগের ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করতেন, তাই হিন্দু ইতিহাসবিদগণ মোগল শাসনের শেষ পর্যায়ে, বিশেষত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের ‘সাম্প্রদায়ি চরিত্র’ নিয়ে যেসব কঠোর সমালোচনায় মেতেছিলেন, তার এক শতক পরে ক্ষিতিমোহন সেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে ‘কল্পিত ইতিহাস’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি চল্লিশের সেই সংঘাতময় সময়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন, ঔরঙ্গজেবের ঘনিষ্ঠ বৃত্ত এবং রাজসভায় বহুসংখ্যক হিন্দু ছিল।
‘ভারতের হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা’ বইয়ে তিনি যে কেবল সাম্প্রদায়িক হিংসার সংগঠিত প্ররোচনার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন তাই নয়, অভিজাত বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু ও মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ইতিহাস রচনাকে যে অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন, তার বিরোধিতা করেছিলেন। এই রচনাতে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আদান-প্রদান কতটা ব্যাপক এবং সৃজনশীল ছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এতে তিনি আরও দেখিয়েছেন ভারতের বড় ধর্মগুলোকে অনতিক্রম্য জলরাশিতে ঘেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসেবে দেখলে, বা আরও খারাপভাবে দুই যুদ্ধরত শত্রুভাবাপন্ন দ্বীপ হিসেবে দেখলে, ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস কতখানি হারিয়ে যাবে! না না, সাম্প্রদায়িক হিন্দু তাত্ত্বিক দাবির বিপরীতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন বুঝিয়েছিলেন ইসলামি সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রভাবে হিন্দুধর্ম উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।
১৯৬১ সালে পেঙ্গুইন বুকস প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে বহুবার পুনর্মুদ্রিত তাঁর হিন্দুইজম ইংরেজি বইতেও এই ভিন্নধর্মী তত্ত্বই জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। যে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন দৌহিত্র অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেন বলেন, ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে যখন ক্ষিতিমোহন বলেন যে তিনি এ রকম একটা বই লিখছেন, যেটা সংক্ষিপ্ত এবং সবার পড়ার যোগ্য হবে। এবং পেঙ্গুইন এটা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে আগ্রহী। তখন অমর্ত্য সেন একটু অবাকই হয়েছিলেন! অবাক হওয়ার কারণ এটা নয় যে, তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল তাঁর দাদুর পাণ্ডিত্য নিয়ে বরং তিনি অবাক হয়েছিলেন এ জন্য যে, ক্ষিতিমোহন শিক্ষিত হয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি শিক্ষার কেন্দ্র বারানসীতে। বাংলা, হিন্দি ও গুজরাটিতে তাঁর দক্ষতা থাকলেও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সীমিত। এ ক্ষেত্রে তিনি ভেবেছিলেন যে পেঙ্গুইন থেকে কেন ইংরেজিতে বইটা লিখতে অনুরোধ করা হলো? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্ষিতিমোহন অমর্ত্যকে পেঙ্গুইনের সঙ্গে তাঁর চিঠি চালাচালি দেখালেন। চিঠিতে তিনি দেখলেন যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব ইস্টার্ন রিজিয়নস অ্যান্ড এথিকস এবং পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ক্ষিতিমোহনের পাণ্ডিত্যের কথা মনে রেখে পেঙ্গুইনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর একটা বই প্রকাশের জন্য।
একই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণন তাদের এ কথা বলেছিলেন, ক্ষিতিমোহন যেহেতু বাংলা বা হিন্দি কিংবা সংস্কৃতে লিখবেন, তারা যেন একজন অনুবাদক ঠিক করে ফেলে। ক্ষিতিমোহনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলে৷ তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়োগ করেন। কিন্তু সম্পাদনাগত জটিলতার কারণে বইটা প্রকাশিত হচ্ছিল না। পরে ১৯৫০-এর শেষের দিকে অমর্ত্য সেন কেমব্রিজে থাকাকালীন একদিন পেঙ্গুইনকে জিজ্ঞেস করলেন যে আসলে ব্যাপারটা কী? ওরা তখন তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব দিল যে অমর্ত্য সেন বইটার বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের দায়িত্ব নিতে পারেন কি না? তখন অমর্ত্য তাঁর দাদুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সময় পার হয়ে যাওয়ায় তিনি বইটির কিছু পরিমার্জন করতে চাইলেন। এভাবেই অমর্ত্য সেন ক্ষিতিমোহনের বাংলা রচনার ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের ওপর ইংরেজিতে একটি গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বইটির ইংরেজি অনুবাদের কাজ; পাশাপাশি সম্পাদনার কাজ চলাকালীন ১৯৬০ সালে অল্পদিনের অসুস্থতায় ক্ষিতিমোহন সেন মৃত্যুবরণ করেন।
অমর্ত্য সেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জগৎ কুটির-এ তাঁর দাদু পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তবে ক্ষিতিমোহন সেনের গবেষণার যে প্রেক্ষাপটটা নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন, তা হলো, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে কিভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ক্ষিতিমোহনের গবেষণায় হিন্দু ধর্মের ধ্বংসাত্মক দিক এর পরিবর্তে সৃজনশীল দিকটি, বিশেষত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মমত গুলির সঙ্গে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে নির্মিত উদার ও সহনশীল ভাষ্য যেমন ছিল, তেমনি তিনি মনে করতেন, ইসলামী সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রভাবে হিন্দুধর্ম উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল।
তথ্যসূত্র
১. অমর্ত্য সেন, জগৎ কুটির; বাংলা সংস্করণ ও সম্পাদনা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, কুমার রাণা, সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স(২০২১), কলকাতা ।
২. প্রণতি মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ; বাংলা আকাদেমি (১৯৯৯), পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩।
৩. সৈয়দ মুজতবা আলী; আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন উদ্ধৃত প্রণতি মুখোপাধ্যায় 'ক্ষিতিমোহন সেন অর্ধশতাব্দী শান্তিনিকেতন', বাংলা আকাদেমি (১৯৯৯), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।



