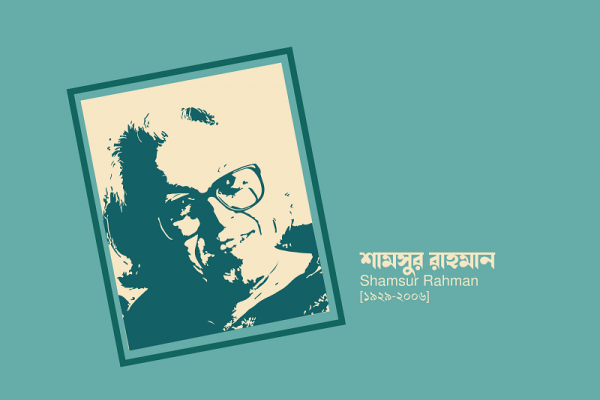রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে মনস্তত্ত্ব
এ কথা বলা বাহুল্য হবে না—আজও ছোটগল্পের একচ্ছত্র অধিপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর ‘গল্পগুচ্ছ’ যেন মহাসমুদ্র, যেখানে নানা রকম মণি-মুক্তার সন্ধান মেলে।
রবীন্দ্রগল্পের মূল উপাদান মানুষ-প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন, নাগরিক জীবন, অতিপ্রাকৃত ঘটনা, রাজনীতি, মনস্তাত্ত্বিক দিক। গল্পের কেন্দ্রে যেহেতু মানুষের বসতি, তাই তার চাওয়া-পাওয়া, না-পাওয়ার বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা, সাংসারিক জটিলতা বহুবিধ বিষয়ের সাক্ষাৎ ঘটেছে রবীন্দ্রগল্পে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পে মনস্তত্ত্বের সন্ধান মেলে বিশেষভাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘ভিখারিনী’।
‘ভিখারিনী’ গল্পের প্রধান চরিত্র কমল। কিন্তু কমলকে ঘিরে তার মায়ের আহাজারিই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। নিছক ট্র্যাজেডির অবতারণা করেছেন শেষমেশ। কমলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কমল ভালোবাসত অমরসিংহকে। কিন্তু কাহিনির শুরুতে অমরসিংহ চলে যায় যুদ্ধে। এদিকে, নিয়তির পরিহাসে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটে কমল ও তার মায়ের। একসময় ভিক্ষা করার সময় কমলকে অপহরণ করে দস্যুরা। মুক্তিপণ দিয়ে তার মা মুক্ত করে আনেন। কিন্তু মুক্তিপণের টাকা জোগাড় করতে মাকে যেতে হয় মোহনলালের কাছেই। এই মোহনলাল একসময়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু এবার যখন সাহায্য চাইতে এলেন কমলের মা, তখন সুযোগ বুঝে বিয়ের শর্তে টাকা দেয়। এ যেন বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে কুমিরের কাছে প্রাণ সঁপে দেওয়া। সব মিলিয়ে গোদের ওপর বিষফোড়া! কমলকে মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল করে ফেলে এসব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা! স্বামীর বাড়ি থেকে মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বারংবার প্রেমিক অমর সিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে কমল। কিন্তু নিয়তির লিখনে তা-ও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কমলের জীবনে উঠে এসেছে মানসিক দ্বন্দ্বের বিচিত্র দিক। এখানে একটু উদাহরণ দেওয়া যাক,
[...]অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, ‘আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন অধিকারে! তাঁহাকে ভালোবাসিবো কোন অধিকারে! আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!১
সাদাচোখে মনে হতেই পারে কমলের প্রচণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা কিন্তু এত শুধু অভিমানের ছোঁয়া, যেখানে প্রচ্ছন্ন আছে প্রচণ্ড প্রেমিকহৃদয়! মনের গহিনে নিজেকে প্রবোধদানের অসামান্য ইচ্ছে, যা দিয়ে সে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেছে! কমল মরে গিয়ে নিজের দুঃখের অবসান করেছে কিন্তু থেকে গেছে তার মায়ের নীরব হৃদয়ভার!
পুরো গল্প পাঠশেষে একটি জিজ্ঞাসাই বড় হয়ে উঠবে, সমাজের নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসা কঠিন? এত প্রেম থাকার পরও শেষমেশ কেন মিলন হলো না অমর-কমলের! এ প্রেমেও সামাজিক বন্ধনটা দৃঢ় হয়ে ওঠেনি? দস্যুদের হাত থেকে বাঁচতে মায়ের অঙ্গীকার রক্ষায় মোহনলালকে বিয়ে করে কমল সামাজিকভাবে প্রথাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু হৃদয়! সে তো নিয়ম-নীতি-প্রথার ঊর্ধ্বে! সেখানে সে থেকেছে শূন্য। প্রথাগত ভিক্ষাবৃত্তি ছাপিয়ে তাই এ গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে হৃদয়বৃত্তি! যার স্বীকৃতি চেয়েছে অমরসিংহের কাছে কিন্তু প্রত্যাখ্যানই তার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। ‘বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল। অভিমানিনী কত দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর যে বাল্যসখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেলো, অমর কেন উপেক্ষা করিলো। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই।’২ অমরের কাছে হৃদয়ের প্রাপ্তি যখন সামাজিক বন্ধনের কাছে হেরে গেছে, তখন কমলের মৃত্যুই যেন প্রাপ্য!
১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘ঘাটের কথা’। রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই গল্পে। কুসুম গ্রাম্যবালিকা। দুরন্ত শৈশবে যখন তার খেলার বয়স। ওই সময়ে তার কাঁধে চাপে বিয়ে নামের সামাজিক বন্ধন। মাত্র আট বছর বয়সে কুসুম বিধবা হয়। স্বামী বিদেশে চাকরিরত ছিল। তাই পত্রযোগেই আসে বৈধব্যের সংবাদ। আট বছর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছে, গায়ের গয়না ছেড়ে আবার দেশে গঙ্গার ধারে ফিরতে হয় বৈধব্যের ছাপে! বাল্যবয়সে কুসুমের মনে যে প্রলেপ পড়ে তা তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে বারংবার।
নিজেকে গুটিয়ে নেয় পৃথিবীর তাবৎ স্বাভাবিক কর্মযজ্ঞ থেকে। যে কুসুম একসময় দুরন্তপনায় মাতিয়ে রেখেছিল ঘাটপাড়-গ্রাম, কথকরূপী ঘাট আজ কুসুমের মধ্যে খুঁজে ফেরে শূন্যতা। তার উচ্ছলতায় ভাটা পড়েছে। নিত্যঘাটের সঙ্গে মিতালি গড়ে ওঠা কুসুম আজ অর্ধমৃত। সামাজিক আচার-নিয়মে রুদ্ধ তার গতি।
বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন ভরিয়া ওঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিলো। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। [...] এমন করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেলো, গাঁয়ের লোক কেহ জানিতেই পারিল না।’৩
কুসুমের জীবনে যে পরিবর্তন, তা দৈহিক অপেক্ষা মানসিক। মনের কোণে জমে থাকা কষ্টই তাকে দায়িত্ববোধ বুঝতে সক্ষম করেছে। অল্প বয়সে নির্মম পরিহাস তার বয়সকে তিন গুণ করেছে!
হাঠৎ গ্রামের মন্দিরে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি এক নবীন সন্ন্যাসী শিবমন্দিরে আশ্রয় নেয়। সন্ন্যাসীকে দেখতে প্রতিদিন ভিড় বাড়াতে থাকে। আশপাশের গ্রাম থেকেও সন্ন্যাসীকে দেখার জন্য লোকসমাগম হয়। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি, সেখান থেকেও অনেক মেয়ে আসে। এসব নারীর মাধ্যমে অনেকটা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যায়, এই সন্ন্যাসী চাটুজ্জেদের বাড়ির ছোট দাদাবাবু! কুসুমের স্বামীর চেহারার সঙ্গে মিল রয়েছে। সবার সঙ্গে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হলেও শুরুর দিকে কুসুমের সঙ্গে হয় না। একদিন কুসুমও সাক্ষাৎ পায় তার। দুজনের মধ্যে এই প্রথম দৃষ্টিবিনিময়।
[...] ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তে তাদের উভয়ের দেখা হইলো। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইলো যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল! মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।
সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার নাম কী?’
কুসুম কহিল, ‘আমার নাম কুসুম।’
সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।’৪
এরপর থেকে নিত্যই মন্দিরে এসে সন্ন্যাসীর পদধূলি নেওয়ার পাশাপাশি শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনত কুসুম। সন্ন্যাসী তাকে যা বলত, বিনাবাক্যে কুসুম তা পালন করত। কিন্তু এই পালন কি শুধু কুসুমের ধর্মভক্তি! না, সেটা গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন স্পষ্টভাবে। কুসুমের অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষাই তাকে ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর প্রতি সমর্পিত করেছে। কিন্তু কুসুম নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করতে চেয়েছে সর্বদা। যা কথকরূপী ঘাটের বর্ণনায় উঠে এসেছে। কিছুদিন থেকে কুসুম আর ঘাটের সান্নিধ্যে আসে না। কুসুমের মনের আবেগ তাকে বিচলিত করলেও তার আত্মদমন দেখতে পাই সর্বত্র। সামাজিক প্রথার জটাজালে বিদ্ধ কুসুম। বিধবার প্রেম গর্হিত। তাকে আর যা-ই হোক জীবন সাজাতে নেই। কিন্তু হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রেম তাকে চঞ্চল করে তোলে।
রবীন্দ্রনাথের বহুল পঠিত ও আলোচিত গল্প ‘পোস্টমাস্টার’। গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় মেলে। গল্পের প্রথমেই দেখতে পাই, কলকাতা থেকে এক পোস্টমাস্টার উলাপুর গ্রামে আসে। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যা হয়, কলকাতা থেকে গণ্ডগ্রামে এসে পোস্টমাস্টারেরও একই হাল হলো। বেতন কম। তাই পোস্টমাস্টারের শনির দশা যেন কাটতেই চায় না।
পোস্টমাস্টারকে কষ্টেসৃষ্টে রান্না করে খেতে হয়। গ্রাম্য একটি অনাথ বালিকা খাওয়ার বিনিময়ে ঘরের বাকি কাজগুলো করে দেয়। মেয়েটির নাম রতন, বয়স বারো-তেরো বছর। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে রতনের একতরফা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেখানে পোস্টমাস্টারের হৃদয়ের কোনোই সংযোগ থাকে না। কিন্তু রতন যে তাকে কতটা আপনার ভাবে, তা গল্পের প্রথম থেকে শেষাবধি প্রকাশিত হয়েছে।
যে সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিত ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।’৫
রতনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও মনের অলক্ষ্যে গড়ে ওঠা হৃদয়বৃত্তির কোনো মূল্য ছিল না শহর থেকে আসা পোস্টমাস্টারের কাছে। বাপ-মা মরা রতন যাকে একমাত্র আশ্রয় ভেবে নিত্যদিন মনের গহিনে স্বপ্নের জাল বুনেছে, তা নিমেষেই থমকে যায় পোস্টমাস্টারের উলাপুর ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে। কিন্তু এই বালিকা রতনই একসময় পোস্টমাস্টারের সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছিল। অসুস্থ পোস্টমাস্টার রোগশয্যায় যখন আপনজনের কাউকে পাশে প্রত্যাশা করেছিল, ওই সময় রতন আর বালিকা থাকে না। তার পরম স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে বিনিদ্র রজনী শিয়রে জেগে থেকে সুস্থ করে তোলে পোস্টমাস্টারকে। কিন্তু পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়েই উলাপুর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে রতন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুসর্বস্বের নামমাত্র! তার মত-পথ কোনোটাই রুদ্ধ করতে পারেনি পোস্টমাস্টারকে। এমনকি তাকে সঙ্গে নেওয়ার কথা অনুরোধও অযাচিত আবদারের মতোই পোস্টমাস্টার উড়িয়ে দেয়। হৃদয়ের সংযোগ যেখানে ন্যূনতম স্পর্শ করে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে? পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, সে কী করে হবে।’৬
ব্যাপারটা বালিকা রতনের ঠিক বোধে আসে না কিন্তু সচেতন পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে—রবীন্দ্রনাথ এখানে শ্রেণিসচেতন! তিনি উচ্চশ্রেণির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির মিলনকে এড়িয়ে গেছেন। ‘ঘাটের কথা’ গল্পে যেমন কুসুম ও সন্ন্যাসীর মিলন সম্ভব হয়নি, তেমনি ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পেও পোস্টমাস্টার ও রতনের মিলন হয়নি। রতনের শ্রেণি পোস্টমাস্টার থেকে ভিন্ন। তাই পোস্টমাস্টার কল্পনায় করতে পারে না রতনকে তার সঙ্গে নেবে বা তার প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতিশীল হবে। উলাপুর ছাড়াতে গিয়ে তার মনের গহিনে কোথাও আমরা রতনের প্রতি হৃদয়ের উষ্ণ অনুভব পায় না। যেটুকু পায় তাকে আর যায় বলা যাক আত্মিক টান বলে না, খনিকের হৃদয়াবেগ মাত্র। গল্পের খানিক উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।
যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে, এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।৭
একদিকে পোস্টমাস্টার অন্যদিকে রতন। দুজনের মনের গতিবেগ ভিন্নমাত্রায় প্রবাহিত! পোস্টমাস্টার নিতান্ত তুচ্ছ দর্শনের অবতারণা করে হৃদয়কে নিবৃত্ত রেখেছে, যদিও গল্পের কোথাও তার পক্ষ থেকে কোনো ভালোবাসার আবহ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু রতনের একতরফা হৃদয়ের টান তাকে মর্মাহত করেছে। তাই প্রচণ্ড অভিমান তার ভেতর জমা করেছে। পোস্টমাস্টার তার চাকরির শেষ টাকাটুকু যখন রতনকে দিতে চায়, তখন রতনের করুণ আর্তি পাঠক হৃদয়কে বিগলিত করে। পোস্টমাস্টারের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ আসে। কেন সে অনাথা বালিকাকে সঙ্গে নিতে পারল না! কী সেই প্রশ্নের উত্তর! আলোচনার মাঝভাগেই বলেছি, এ যেন উচ্চশ্রেণির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথ নিজেও জমিদার শ্রেণির ছিলেন। তাই মনের কোনো এক কোণে জমিয়ে রাখা ইচ্ছেই হয়তো গল্পে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে! রতনের ভাগ্যে জুটেছে সামাজিক প্রভেদ ও পোস্টঅফিসের চারিদিকে অশ্রুজলে সিক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না অনাথিনী বালিকার।
‘জীবিত ও মৃত’ একটি পরিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র কাদম্বিনী। রাণীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুর মৃত ছোট ভাইয়ের বউ সে। শ্বশুর ও পিতৃকুলে তার নিজের বলতে কেউই ছিল না। শারদাশংকরের ছোট ছেলেটি কাদম্বিনীর চোখের মণি। একদিন হঠাৎ কাদম্বিনীর হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশি ঝামেলা এড়াতে জমিদারের চারজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যায়। কাকতালীয়ভাবে কাদম্বিনীর হৃদক্রিয়া আবারও সচল হয়। শুরু হয় কাদম্বিনীর জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের লড়াই। প্রথম পর্যায়ে সে ছিল বিধবা। তারপরও সমাজ ও প্রথার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে অন্যের সন্তান বুকে করে নিজের দুঃখমোচনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় তার জীবন-জটিলতা। শশ্মান থেকে কাদম্বিনী সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতার জন্য বাড়ি ফিরতে পারেনি। সে চলে গেছে ছোটবেলার সখী যোগমায়ার কাছে।
দুই সখীর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধানে শুরু হয় গল্পের নাটকীয়তা। কাদম্বিনীর চালচলন স্বাভাবিক নয়। সে ছোটবেলার সখী ও সাধারণ মানুষ থেকে সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। পৃথিবীতে নিজের অবস্থান নিয়ে তার মধ্যে দ্বিধা কাজ করেছে! সে কি আসলেই মৃত! তার সদুত্তর সে পায় না! ঘুমের মধ্যেও সে চমকে উঠে ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বের হয়ে যায়! হৃদয়কোণে জমে থাকা ভয় তাকে সবার থেকে দূরে নিয়ে গেছে! ঝড়-জলে ভিজে যখন শ্মশান থেকে গায়ে কাদা-জল মাখা নিয়ে বের হয়, তখন গ্রাম্য পথিকের জিজ্ঞাসায় মনে হয়, সত্যি সে পৃথিবীতে আছে! কিন্তু মনের ধন্দ থেকেই যায়! সে ধন্দ যোগমায়ার বাড়িতে উপস্থিত হলেও বারংবার তাকে দগ্ধ করতে দেখা গেছে। যোগমায়ার স্বামী শ্রীপতিচরণবাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ যখন ঘটে, তখনো তাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখা যায়।
কাদম্বিনীর মধ্যে একদিকে অবদমনের প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে মনের ধন্দ তাকে জীবনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলেছে! কাদম্বিনী সবার মাঝে থেকেও নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা! হঠাৎ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যে মৃত্যু নামক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, সে মৃত্যু তো দৈহিক। কিন্তু কাদম্বিনী কি আদৌ জীবিত ছিল? প্রাণ থাকলেই কি মানুষ জীবিত থাকে! তার মনের যে ক্রিয়া সমাজ-সংসারের কাছে কি রুদ্ধ হয়নি? বিধবা হয়ে পুত্র-কন্যা-মাতা-পিতাহীন জীবন তাকে কতটা প্রশান্তি দিয়েছিল? মৃত্যুই তার জন্য উত্তম ছিল না? জীবনের তাবৎ প্রশ্ন এখানে অসমীচীন নয়। এ জীবনক্রিয়া বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থেকে কাদম্বিনীর জীবনযন্ত্রণাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন! কাদম্বিনীর হৃদয়াকুতি পাঠকের মনকে বিগলিত করে। সে যখন বলে, ‘কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই, ওগো আমি তবে কোথায় যাইব।’৮
পৃথিবীর অপরূপ শোভা কাদম্বিনীকে স্পর্শ করতে পারেনি! জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব তাকে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটাতে বাধ্য করেছে! সবার কাছে অগ্রহণযোগ্যতা তাকে মানসিকভাবে দ্বিধান্বিত করেছে। শেষ পর্যন্ত কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করলো যে সে মরে নাই! একথার মধ্যে একদিকে তার বেঁচে থাকার আকুতি অন্যদিকে তার প্রতি ঘটে যাওয়া সমাজের অন্যায় আচরণকে প্রমাণিত করেছে। সে যে বেঁচে থেকেও সমাজের চোখে মৃত, তা প্রতিপদেই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কাদম্বিনী হৃদক্রিয়া বন্ধের মাধ্যমে যার সমাপ্তি ঘটেছে।
‘মুক্তির উপায়’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৮ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এটি আপাদমস্তক একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। এই গল্পের দুটি প্লট। প্রথম পর্যায়ে ফকির চাঁদ ও হৈমবতী। দ্বিতীয় পর্বে নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের ছেলে মাখনলালের কাহিনি। গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক ও হাস্যরসাত্মক কাহিনির আড়ালে জীবনের অমোঘ যাতনার রূপায়ণ করা হয়েছে। যদিও গল্পে হাস্যরস এসেছে, তবু এখানে মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে দৃশ্যমান। ফকির চাঁদ বাল্যকাল থেকেই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বৃদ্ধ সমাজে তাকে বেমানান দেখাত না। কারণ, সে সর্বদা গম্ভীর থাকত। দেহের গঠনও গম্ভীর করে তুলেছিল। ফকির চাঁদের স্ত্রী হৈমবতী। অল্প বয়স। তার মন পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকলেও ফকির চাঁদ তাকে আধ্যাত্মিক করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। হৈমবতীর কৌতূহলী মন বারবার বঙ্কিমের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ প্রাণ খুঁজেছে। হৈমবতী ও ফকির চাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। সংসারে সদস্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে আর্থিক অনটন। ফকির চাঁদের জীবন ক্রমে জটিল হয়ে ওঠে। আর্থিক সচ্ছলতা আনতে চাকরির উদ্দেশ্যে বের হলেও হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। একদিন হঠাৎ গৌতম বুদ্ধের মতো সংসারত্যাগী হয় ফকির চাঁদ।
পিতার তাড়নায় এতোবড় গম্ভীর প্রকৃতির ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন সে মনে করিল, ‘বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।’ এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।’৯
একদিকে ফকির চাঁদের গৃহত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে মাখনলালের গৃহত্যাগের কাহিনি। দুই কাহিনির সূত্রপাত আলাদা হলেও ঘটনা গিয়ে মিশেছে একটি জায়গায়। মাখনলালের দুই স্ত্রী। উভয়ে মিলে মাখনলালকে সাতটি মেয়ে ও একটি ছেলে উপহার দিয়েছে। কিন্তু সাংসারিক শান্তির বদলে নিত্যদিন ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। বিরক্ত হয়ে একদিন মাখনলালও নিজ ঘর ছাড়ে। এদিকে ফকির চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে নবগ্রামে উপস্থিত হয়। তৈরি হয় নাটকীয়তা। জটিলতার রেশ যেন কিছুতেই কাটে না। মাখনলালের পিতা ষষ্ঠীচরণ সন্তানের নিরুদ্দেশকে কেন্দ্র করে জীবনকে যখন ওষ্ঠাগত করে তুলেছে, তখন সেখানে ফকিরের আবির্ভাব। এই ফকিরকেই নিজের ছেলে দাবি করে যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করে তোলে। মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে নিজের স্ত্রী, বাবা কীভাবে স্বামী-সন্তানকে চিনল না! সন্তান যত দিন পরেই ঘরে ফিরুক, তাকে কি চেনা যাবে না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পের প্লট তৈরি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে পাঠককেও দ্বিধায় ফেলেছেন! ফকিরকে মাখনলাল ভেবে তাকে ষষ্ঠীচরণের পরিবার টানাহেঁচড়া করেছে। সাংসারিক জটিলতার কারণে ঘর ত্যাগ করলেও সমাজ তো ত্যাগ করতে পারেনি। নিজের বোনা জালে নিজেই জড়িয়েছে।
ফকির ও মাখনলালের সাংসারিক দ্বন্দ্ব মেটাতে গিয়ে নতুনভাবে আবারও উভয়ে গোলকধাঁধায় পড়ে! ফকির চাঁদ যখন মাখনলালের বাড়িতে উপস্থিত হয়, যদিও উপস্থিতিটা অনাকাঙ্ক্ষিত, তবু নাটকীয় ঘটনার একপর্যায়ে বোঝা যায় ফকির চাঁদ হৈমবতীর ভাইয়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে ঘিরে মাখনলালের দুই স্ত্রী-সন্তানেরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত। শেষমেশ মাখনের দর্শনে সব রহস্যের জাল ছেঁড়ে। গল্পটি হাস্যরসে ভরপুর হলেও মানবমন কীভাবে প্রতিনয়ত বিক্ষিপ্ত হয়, তার নিদর্শনের কোনোই ঘাটতি নেই। ফকির চাঁদ ও মাখনলালের মুক্তির কোনো উপায় রবীন্দ্রনাথ বাতলে দেননি। সাংসারিক জটিলতা, স্ত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, নিরুদ্দেশ হওয়া। কিন্তু জীবনের ঘূর্ণিপাকে এসে আবারও পরিবারেই নিজেদের সমর্পণ করেছে।
রবীন্দ্রনাথের প্রথম সারির গল্প ‘একরাত্রি’। এটি সাধনা পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পের কথকই একরাত্রির কেন্দ্রীয় চরিত্র। কথক ও সুরবালার বাল্যপ্রেমকে কেন্দ্র করে কাহিনির সূত্রপাত। যদিও এই সম্পর্ককে প্রেম না বলে শৈশবের অপরিণত খুনসুঁটিই বলা চলে। সুরবালাকে কেন্দ্র করে নায়কের প্রভুত্ব যেন সমগ্র গল্পেই বিদ্যমান। নায়কের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। কথক কলকাতার কলেজে পড়াকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। একসময় দেশোদ্ধারে প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না। সভায় বক্তৃতা, লিফলেট বিলি করা, চাঁদা তোলার জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ানো, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করা, সভাস্থলে গিয়ে বেঞ্চি চৌকি সাজানোসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেকে মাটসীনি গারিবালডি করে তুলতে সদা জাগরূক কথক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীতির চেয়ে জীবনসংগ্রামের পাল্লা ভারী হওয়ায় অচিরেই সংসারের হাল ধরতে হয়। কলকাতায় থাকাকালে শৈশবের সঙ্গী সুরবালার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু কথকের অতিরিক্ত স্বদেশপ্রীতি ও বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞা তাকে এ কাজে নিবৃত্ত করে। যেই সুরবালার প্রতি একসময় প্রভুত্ব করত, তাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছে! একদিকে নায়কের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা, অন্যদিকে সুরবালার প্রতি প্রকৃত প্রেমের অভাব! সুরবালার সঙ্গে ছোটবেলা বউ-বউ খেলাটায় সীমাবদ্ধ ছিল। গল্পের কোথাও সুরবালার জন্য তার টান লক্ষ করা যায় না।
দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনেবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।১০
সুরবালার সঙ্গে নায়কের মানসিকভাবে সম্পৃক্ততা ছিল না। তাই সুরবালার বিবাহের খবর সূর্যের আলোর মতোই স্বাভাবিক। নোয়াখালী বিভাগের একটি ছোট শহরে এনট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের পদে নিযুক্ত হলে সুরবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নায়কের। সুরবালার স্বামী রামলোচন সরকারি উকিল। রামলোচনের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ ঘটে, তখন সুরবালা পর্দার আড়ালেই থেকেছে। নায়কের প্রতি গভীর অভিমান, ক্ষোভই যেন এই অন্তরাল! জীবনের স্বপ্ন যাকে নিয়ে বুনেছিল আট থেকে আঠারো পর্যন্ত, সেই নায়কই তাকে অবলীলায় দূরে ঠেলে দিয়েছে। সুরবালার প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ তার মধ্যে কাজ করেনি। হতে পারে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রবল ঝোঁক সেই সঙ্গে সুরবালার প্রতি অনাগ্রহ। পর্দার আড়ালে সুরবালার চুড়ির শব্দ তাকে সামান্য বিচলিত করলেও সেখানে মনের লেশমাত্র সংযোগ ছিল না।
অবচেতন মনে সুরবালাকে প্রত্যাশা করলেও সেখানে প্রেমের স্পর্শ ছিল না। গল্পের নায়কের মনের কোনো চঞ্চলতাই দেখা যায় না। বরং বারবার তার নিজের জীবনই প্রধান হয়ে উঠেছে। এমনকি ঝড়ের রাতে দুজনে একই পাড়ে আশ্রয় নিলেও তাদের মনের কথা গোপনেই প্রবাহিত হতে থাকে। যেই সুরবালা শিশুকালে কথকের আপনার ছিল, এত কাছে থেকেও তার আর নায়কের মধ্যে একপৃথিবী দূরত্ব। সুরবালার নারীস্বভাব এবং কথকের প্রেমহীন সত্তা—দুটো এক বিন্দুতে মিশে নিকটও তাদের দূরের বাসিন্দা করেছে। অবচেতনে তাই সুরবালার সুখ কামনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিজের অপরাধবোধ হয়তো খানিক ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল।
সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অন্তত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।’১১
মনের মধ্যে উদারতার সৃষ্টি হলেও সে নিজের অবচেতন মনের পাপবোধের ফল মাত্র। তাই প্রকৃতির ঝড় থামলেও কথকের মনের কোথায় যেন ঝড়ের বেগ কমে না!
‘মধ্যবর্তিনী’ গল্পটি জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি পরিবারের দ্বন্দ্বমুখর দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গল্পটির প্লট গড়ে উঠেছে। গল্পের মূল কাহিনি নিবারণ ও হরসুন্দরীকে ঘিরে। নিবারণ ও হরসুন্দরী স্বামী-স্ত্রী। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ঘাটতি না থাকলেও জীবনের কিছু অপ্রাপ্তি দুজনের মাঝে দেয়াল তুলে দেয়। বিবাহিত জীবনের বহুদিন পার করলেও সন্তান আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। ফলে হরসুন্দরীর মধ্যে বাড়তে থাকে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। ভালোবাসার সেই ধনকে স্বামীকে উপহার দিতে তাই স্বেচ্ছানির্বাসনে যায়। যার করুণ পরিণতির শিকার শৈলবালা। ছোটখাটো একটি মেয়ের সঙ্গে নিবারণের বিয়ে দিয়ে তার অপূর্ণ বাসনাকে বাস্তব করে তুলতে চায় হরসুন্দরী। কিন্তু নিবারণ যখন শৈলবালাকে কাছে টেনে না নেয়, তখন হরসুন্দরীই তাকে চাপ প্রয়োগ করেছে। যখন নিবারণের শৈলবালার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ, ঠিক তখন হরসুন্দরীর মনের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পায়। সে নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। খুঁজে ফেলে স্বামীর হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা। তাই শৈলবালাকে যত কাছে টানতে থাকে নিবারণ, হরসুন্দরী তত দূরে সরে যায়! যেই দূরত্ব আপাতদৃষ্টে মনের হলেও নিতান্তই তা অভিমানের—ক্ষোভের! যেই হরসুন্দরী একসময় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে উঠেপড়ে লেগেছিল, সেই ব্যক্তিই শৈলবালার সঙ্গে কড়ি খেলায় ব্যস্ত দেখে চক্ষু চড়কগাছ!
শৈলবালার সঙ্গে স্বামীর প্রেমকে কেন্দ্র করে হরসুন্দরীর হৃদয়ে পাড় ভাঙা কষ্ট দেখা দিয়েছে। জীবনের তীরে এসে নোঙর না ভেড়ানোর কষ্ট তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বালিকা বধূকে কেন্দ্র করে নিবারণের প্রেম তার চোখে অসহনীয়। দুই শিশু মিলে বিশ্বজগতে খেলা করার আহবান জানিয়ে হরসুন্দরী সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেষ্টা করেছে। হরসুন্দরীর দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নারী জাতি সবার ভাগ দিলেও স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে পারে না। হরসুন্দরীর মধ্যেও আবহমান বাঙালি বধূর চিরন্তন রূপ ফুটে উঠেছে। বাঙালি রমণী পৃথিবীর শত দুঃখ সহ্য করলেও স্বামীকে আগলে রাখতে চায় পরম মমতায়। নিজের আক্ষেপ, দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে মানসিকভাবে। শৈলবালার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পথের কাঁটা দূর হয়। কিন্তু স্বামীকে বহুদিন পর আপনার করে পেলেও হৃদয়বৃত্তি কাছে হেরে যায় হর। নিবারণ আর হরসুন্দরীর মাঝে জাগরূক থাকে শৈলবালার মুখ।
হরসুন্দরীর মধ্যে আবহমান বাঙালি রূপ বিদ্যমান। সন্তান না হওয়ার কারণে স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দিলেও মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। হয়তো হরসুন্দরীর আশা ছিল, স্বামীকে বিয়ে দিলেও তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা-প্রেমে ভাটা পড়বে না। কিন্তু অল্পবয়সী শৈলবালার উচ্ছলতা নিবারণকে এতটাই মুগ্ধ করে যে হরসুন্দরীর সঙ্গে এত দিনের সংসারজীবন ভুলতে বসে। জীবন জটিলতার একপর্যায়ে শৈলবালার মৃত্যু হলেও মনের দ্বন্দ্বের মৃত্যু ঘটেনি!
[...] ‘মধ্যবর্তিনীতেও মনস্তত্ত্বের জটিল জাল আছে। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে অসুস্থ স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুরোধ জানাচ্ছে। [...] মধ্যবর্তিনীতে দ্বিতীয় পত্নী শৈলর মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তিনী হয়েই সে বেঁচে রইলো—অনস্তিত্ব অস্তিত্বের অসামান্য প্রয়োগ।১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ গল্পটি ‘সাধনা’ পত্রিকার ১৩০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে বিন্ধ্যবাসিনী ও তার স্বামী অনাথবন্ধুকে কেন্দ্র করে। ঘরজামাই অনাথ নিজেকে ‘অতি পণ্ডিত’ ভাবে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দেয় না। এরপর কলেজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্ত্রীকে বোঝায়, তার জন্য ‘এ পরীক্ষা নয়’। সে এত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যে, তাকে কলেজের পরীক্ষায় পাস দিতে হবে। বিন্ধ্যাও স্বামীর কথায় আস্থা রাখে, স্বামীর যুক্তিকেই ‘ধ্রুব’ জ্ঞান করে। তার স্বামী আর দশটা পুরুষের চেয়ে ভিন্ন, সেটা যেন বিন্ধ্যও আত্মায় লালন করে।
এদিকে অনাথের মধ্যে দেখা দেয় অতি দাম্ভিকতা। একদিকে স্বামীর প্রচণ্ড ধূর্ত স্বভাব, অন্যদিকে স্ত্রীর পতিপরায়ণ-স্বভাব গল্পকে দিয়েছে জটিল মনস্তত্ত্বের ভিন্নমাত্রা। অনাথবন্ধু সরলা স্ত্রীকে পেয়ে ইচ্ছের দাস বানিয়ে রাখে। ঘরজামাই থেকেও স্ত্রীর সঙ্গে আচরণে প্রভুত্ব দেখানোর ক্ষেত্রে কোনো কমতি নেই। আর বিন্ধ্যবাসিনীকে স্বামীর সেই প্রভুত্ব বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে দেখা যায়। বিন্ধ্য আবহমান বাংলার নারীর মানসিকতার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নারীর এই বলয় থেকে তাকে বের করে আনেননি বরং পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে নিপীড়িত-নির্যাতিতের প্রতিভূ হিসেবেই তৈরি করেছেন। স্বামীর শত প্রবঞ্চনা-গঞ্জনার বিরুদ্ধে মুখ খোলে না বিন্ধ্য। উল্টো স্বামীকে ঈশ্বর জ্ঞান করে তার পূজায় নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখে। বিন্ধ্যর এই পতিভক্তি যতটা ভালোবাসার, তার চেয়েও বেশি মেরুদণ্ডহীন, পশ্চাদপদ মানসিকতার প্রকাশ। নারী-পুরুষের প্রভুত্ব শিকার করে সেখানে যুক্তি-বুদ্ধি কিছুরই উপস্থিতি থাকে না।
পুরুষ সমাজ তাদের সুবিধার জন্য নারীকে নানা শৃঙ্খল পরিয়ে বশ করে রেখেছে। নারীও পতিব্রতা সাজতে গিয়ে সব ধরনের নির্যাতন-অন্যায়কে হাসিমুখে মেনে নেয়। অনাথ যখন শ্বশুরবাড়ির টাকা চুরি করে বিলাত চলে যায়, তখন সেই চুরির দায় বিন্ধ্য নিজের কাঁধে নেয়। কিন্তু কেন? এর জবাব খুঁজতে গেলে, পাওয়া যাবে, সেখানে ভালোবাসার টান যতটা, তারও বেশি নারীর মানসিকতার বৃত্তকে ভাঙতে না পারার ব্যর্থতা। শত সমস্যার সম্মুখীন হলেও নারী তার স্বামীর সম্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় না। এর কারণ শৈশব থেকেই নারীর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় স্বামীর মুখে মুখে কথা বলতে নেই! উচ্চস্বরে হাসতে নেই, নিজের ভাগ বুঝে নিতে নেই। বাবা-ভাই-স্বামীর কথাই শিরোধার্য। তারা পরিবারের কর্তা। তাই তাদের গাইডলাইনের বাইরে গেলেই বিপদ। যদি যুক্তির কথা হয়, তা-ও নারী সেখানে চুপ থাকবে; এমন মানসিকতা লালন করে নারীরা। তেমনি বিন্ধ্যার মানসিকতা। সেও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারীর জীবনকে গড়ে তোলা ছকের বাইরের যেতে পারে না। যেতেও চায়নি। বিন্ধ্যের কাছে স্বামী দেবতুল্য। সেখানে পাপ-পঙ্কিলতার ছোঁয়া থাকতে পারে বলে মানতে পারে না বিন্ধ্য। এখানে বিন্ধ্যর সারল্যই তার জন্য বিনাশ ডেকে আনে।
অনাথ তো টাকা চুরি করে বিলাতে চলে গেল কিন্তু একবারও বিন্ধ্যর জীবনে কী ঘটবে, সে কথা মনেও আনেনি। অন্ধ ভালোবাসার কারণে স্বামীর শত অপরাধ অবলীলায় ক্ষমা করে দিয়েছে, যার সুযোগ গ্রহণ করেছে অনাথ। বিলেত থেকে ফিরে আবার বিন্ধ্যর বাবার সম্পত্তি করায়ত্ত করার চেষ্টা করেছে।
এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সমক্ষে উন্নতমস্তকে গৌরবের আসনে আরহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।১৩
অনাথ এতটাই ধূর্ত যে বিলাতি নারীকে বিয়ে করলেও বিন্ধ্য সে সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারেনি বা চায়নিও। কারণ তার কাছে অনাথবন্ধু প্রভু। আর প্রভুর শুধু দাসত্ব করা যায়। প্রশ্ন তোলা জায়েজ না। যে কারণে বিন্ধ্য পতিসেবায় ব্যস্ত থাকলেও পতির স্খলন সম্পর্কে খোঁজ নেয়নি। শেষ পর্যন্ত স্বামীর মুখোশ খুলে গেলেও বিন্ধ্য নিজের অবস্থান থেকে নড়ে না। সে বরং নিয়তির হাতেই নিজেকে সমর্পণ করে। এমনকি কখনো আত্ম-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয় না। ঠিক-বেঠিক সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন তোলে না। এ ক্ষেত্রে বিন্ধ্যকে যতটা দোষ দেওয়া চলে, তার চেয়ে বেশি আঙুল তুলতে হয় সমাজব্যবস্থার দিকে। কেন নারীকে পুরুষতন্ত্রের দাসিতে পরিণত করা হয়! কেন নারীকে তার যৌক্তিক দাবি নিয়ে দাঁড়াতে দেয় না। পরিবারগুলো কেন নারীকে ‘প্রথম ঘরই ঘর, প্রথম বরই বর’ ভাবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে? কেন নারীর মনে সেঁটে দেওয়া হয়, ‘বেনারসি পরে স্বামীর ঘরে যেতে হয়, কাফনের কাপড় পরে বের হতে হয়!’
প্রায়শ্চিত্ত গল্পের নায়িকা ‘বিন্ধ্য’র সমস্যা আবহমান নারীর সমস্যা। তাদেরই জীবনচেতনার প্রতীক সে। খোদ রবীন্দ্রনাথও নারীকে নিগড় থেকে মুক্তি দিতে চাননি। তার মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কবোধ দেননি। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিক প্রতিবেদনের মতো শুধু সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেননি। তাই গল্পটি শেষ পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীকে কোনো স্বপ্ন দেখায় না। বরং পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে নারীর জীবনগাথাকে প্রকাশ করে।
‘বিচারক’ গল্পটির কেন্দ্রে অবস্থান করেছে ক্ষীরোদা ও জজ মোহিতমোহন দত্ত। প্রথম থেকে শেষাবধি ক্ষীরোদার উপস্থিতি থাকলেও এই গল্পের মূলে রয়েছে মোহিতলাল। তাকে কেন্দ্র করে গল্পটি শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির রূপ নিয়েছে। বিগত যৌবনা, অসহায়, নিপীড়নের শিকার ক্ষীরোদা। পরিবার ও সমাজের কেউ তাকে স্বাভাবিক জীবনে সাহায্য করেনি, এমনকি যেসব পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তারাও তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেছে। যৌবনের প্রান্তসীমায় ক্ষীরোদা উপস্থিত হয়ে যাকে ঘিরে স্বপ্ন বুনেছিল, সে প্রণয়ীও তাকে নিঃস্ব করে রাতের অন্ধকারে পলায়ন করেছে। এমনকি সন্তানের প্রতি কোনো কর্তব্য পালন করেনি তার প্রণয়ী! একদিকে সন্তানের ক্ষুধার জ্বালা, অন্যদিকে বখাটেদের উৎপাত ক্ষীরোদাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। নিজের সম্ভ্রম ও বাচ্চার ক্ষুধার তাড়না না মেটাতে পেরে সহজ সমাধান হিসেবে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। যে বিভীষিকার বলি হয়েছে তিন বৎসরের দুগ্ধজাত শিশু!
যৌবনে ক্ষীরোদা দেহোপজীবিনী থাকলেও মোহিতমোহনের প্রেম তাকে সঠিক জীবনের সন্ধান দেয়। কিন্তু মোহিতমোহন ক্ষীরোদার পরিচয় পেয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছে। ক্ষীরোদা ও মোহিতমোহনের মাঝে ব্যবধান জাত-পাতের। যে দ্বন্দ্ব ভেঙে মোহিতমোহনকে বের করে আনেননি রবীন্দ্রনাথ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এলিট শ্রেণির প্রতিনিধি। যে কারণে তিনি চাননি স্বশ্রেণিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে! তাই ক্ষীরোদার সঙ্গে মোহিতমোহনের প্রণয়কে পরিণয়ে আবদ্ধ করেননি। বরং তিনি আড়ালেই এর মীমাংসা করেছেন! রবীন্দ্রনাথ নিজের ওপর কখনোই দায় রাখতে চাননি। এ জন্যই তার ‘ঘাটের কথা’, ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে জাত-পাতকে দূরে রেখে সাধারণ্যে চরিত্রগুলোতে এমন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন পাঠকের কথা বলার সুযোগ না থাকে।
ঘাটের কথার কুসুম সন্ন্যাসীর প্রেমে পড়ে, যার প্রণয় দেখালেও পরিণতি মৃত্যু। আবার পোস্টমাস্টারে রতন বালিকা। সেখানেও বয়সের ব্যবধান। ‘বিচারক’ গল্পে ক্ষীরোদা দেহোপজীবিনী। রবীন্দ্রনাথ মননে যে আদর্শকে লালন করেছেন, তাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সমাজের বলয় ভাঙতে চাননি। ক্ষীরোদা যে পূর্ব প্রণয়ী আসায় কূপে ঝাঁপ দিল, সেখানে তিনটি বিষয় কাজ করতে পারে। প্রথমত, মোহিতমোহনের দেবতুল্য প্রেম দ্বিতীয়ত, ক্ষুধায় সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে না পারা। তৃতীয়ত, সন্তানের পরিচয়হীনতা। এই তিন বৃত্ত ক্ষীরোদার জীবনকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে, যেখানে ঘি ঢেলেছে সাবেক প্রণয়ী! গল্পের কোথাও রবীন্দ্রনাথ শিশুর পিতৃপরিচয় তুলে ধরেননি বা পাঠকের সামনে আনতেও চাননি। রবীন্দ্রনাথ অতি লজ্জাপরায়ণ সুপুরুষ ছিলেন। তাই তিনি গল্পের মূল ব্যাখ্যা পাঠককে আকারে-ইঙ্গিতেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। নীরব থেকেছেন চরিত্রগুলোর সঠিক বিকাশে। মোহিতমোহনের আদালতের অভিযুক্ত ক্ষীরোদা। আসামি প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ক্ষীরোদার কিন্তু যার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, সেখানে ট্র্যাজেডির রূপায়ণ গল্পটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। একটি আংটি, যাকে কেন্দ্র করে মোহিতমোহনের স্মৃতির পাতা খুলে যায়।
[...] মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।
মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।১৪
মোহিতমোহনের মনে ফাঁসির আসামির প্রতি কৌতূহল জন্মেছে ঠিকই, তখনই আবিষ্কার করে এ তারই প্রণয়ী। যাকে একসময় ছেড়ে এসেছে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচতে। যদিও মোহিতমোহন নিজেও একাধিক নারীতে আসক্ত ছিল। কিন্তু এখানে চরিত্রের চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে শ্রেণিচেতনার যার সঙ্গে আপস করেননি খোদ রবীন্দ্রনাথও। যদি তাই পারতেন তবে ক্ষীরোদার সঠিক জীবনের দিশাকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে মোহিতমোহনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেন। তা না করে তিনি হৃদয়ের চেয়ে আভিজাত্যবোধে আটকে গেছেন।
তথ্যসূত্র
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, ‘ভিখারিনী’, বিশ্বভারতী, ৯৬/এন মহারানি ইন্দিরা রানী রোড। কলকাতা ৬০। প্রকাশকাল: পুনর্মুদ্রণ- ১৪২৪। পৃ. ৮৪৮
২। তদেব, পৃ. ৮৪৭
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, ‘ঘাটের কথা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৯৬/এন মহারানি ইন্দিরা রানী রোড। কলকাতা ৬০। প্রকাশকাল: পুনর্মুদ্রণ- ১৪২৪। পৃ. ৩
৪। তদেব, ‘ঘাটের কথা’। পৃ. ৫
৫। তদেব, পৃ. ১৮
৬। তদেব। পৃ. ২০
৭। তদেব, পোস্টমাস্টার। পৃ. ২০
৮। তদেব। পৃ. ৯৫
৯। তদেব, ‘মুক্তির উপায়’। পৃ. ৬৪
১০। তদেব, ‘একরাত্রি’। পৃ. ৭৭
১১। তদেব। পৃ.৮০
১২। হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত সাহিত্য-প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-সাহিত্য, প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রকাশকাল: ২০১৪। পৃ.৭৬০
১৩। তদেব। পৃ. ২৩২
১৪। তদেব। পৃ. ২৩৯