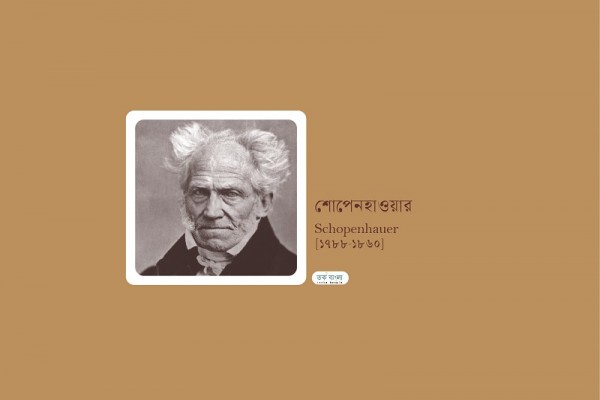ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
তিনি কিংবদন্তি। তিনি ইতিহাসের সন্তান। বলছি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথা। সদ্য লোকান্তরিত হয়েছেন যিনি। ওই নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির গর্ব ও গৌরবের অধ্যায়। বায়ান্নর অমর একুশের ‘সিগনেচার সং’ ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানের রচয়িতা তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’র পর বাঙালির কণ্ঠে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে এই গান। হবে ভবিষ্যতেও, যত দিন বিশ্ব ভূগোলে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা থাকবে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় বাঙালিকে-তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বার উন্মোচনের সুযোগ করে দেয়। বাঙালি নিজের অধিকার ও তার সামষ্টিক শক্তিকে শনাক্ত করে, যার সঙ্গে যোগ হয় ইতিহাসবোধ ও বৌদ্ধিক মানুষের সম্মিলিত প্রত্যয়। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন এবং নানা ঘটন-অঘটন, চড়াই-উতরাই, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ঐতিহাসিক মুহূর্তসমূহের পরম্পরায় বাঙালির জীবনে আসে ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।
স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য অনিবার্য এক যুদ্ধ। যে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাঙালি গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়, তারও রয়েছে নিজস্ব দেশ-মানচিত্র ও লাল-সবুজের পতাকা। বাঙালি এই বার্তায় উচ্চকিত করে যে, পৃথিবী নামক গ্রহে তার ভূগোল ও ভগবান নিজস্ব আবিরে আঁকা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদগাতা যেমন সে, তেমনই ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের প্রতিষ্ঠাতাও সে।
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই একমাত্র উদাহরণ—সরাসরি যুদ্ধ করে জন্মভূমি শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন করার। এসব অর্জনের নেপথ্যে যে শক্তি বাঙালির জীবনে বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে, সেই শক্তির নাম বায়ান্নর একুশে। আটপৌরে বাঙালিকে—সোঁদা মাটির গন্ধ মেখে বেড়ে ওঠা নদীমাতৃক এ জাতিকে দীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ের পথ পরিক্রমা পেরিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে যে ইতিহাস, তার নাম একুশে ফেব্রুয়ারি। এই একুশে ফেব্রুয়ারি জন্ম দিয়েছে অনেক কিংবদন্তির। যাদের মধ্যে অন্যতম হলো আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। তাঁর লেখা কবিতা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ পরবর্তীকালে গানে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে একুশের চেতনা ও ইতিহাসের অনবদ্য এক দলিল।
একুশ মানে যেমন মাথা নত না করা। একুশ মানে যেমন শহীদ রফিক-শফিক-বরকত-জব্বার, বাঙালির শ্রদ্ধা ও আবেগের শহীদ মিনার। ঠিক তেমনি একুশ মানে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অমর কবিতা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।’ একটি জাতির সম্মিলিত আবেগ ও চেতনার সঙ্গে একজন ব্যক্তির সৃষ্টি যখন একাকার ও অভিন্ন হয়ে ওঠে, তিনি তখন হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি। তাঁর সৃষ্টি তখন হয়ে ওঠে কিংবদন্তিতুল্য। এ কারণেই লেখার শুরুতেই তাঁকে কিংবদন্তি আখ্যায় ও ইতিহাসের সন্তান অভিধায় সম্মানীয় করা হয়েছে। যা তাঁর প্রাপ্যও বটে। তাঁকে সম্মানিত করে আমরা গৌরবান্বিত হই। জাতির পাওনা মেটায়। ঋণমুক্ত হওয়ার অপার সুযোগ নিই।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জীবন ও কর্মের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব শুধু একবার নয়, একাধিকবার তিনি ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণের ভেতর দিয়ে যাওয়ার অসীম গর্ব ও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। একুশের চেতনায় যে বাঙালি ঘটনাপরম্পরায় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়ে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করেছে। বাঙালির সেই ঐতিহাসিক দিনগুলোতেও তিনি ইতিহাসের দায় মেটানোর সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে নিবেদন করেছেন সম্পূর্ণরূপে
ইতিহাস আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে সন্তান জ্ঞানে সম্মান ও সমীহের সঙ্গে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি, প্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার ওপর পক্ষপাত প্রদর্শন করেছে যৌবনের ঊষালগ্নেই, যখন তিনি কেবলই উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র, বয়স সবেমাত্র আঠারো। তারপর ইহাজাগতিকায় তিনি ছিলেন সাত দশকজুড়ে। কিন্তু কিংবদন্তি-ইতিহাসের সন্তানের যখন ইতিহাস নিরপেক্ষ-নির্মোহ কর্মের হদিশ পাওয়া দুরুহ ও দুষ্কর হয়, আতশী কাচেও মেলে না তেমন কোনো স্বাক্ষর। তখন এই প্রশ্ন ওঠা সংগত ও যৌক্তিক হয়ে ওঠে যে, ইতিহাসের সন্তান হয়েও তিনি ইতিহাসের প্রতি তেমনভাবে—সদর্থক অর্থে যথাযথ দায় ও দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করেছেন, ইতিহাসের পথিক না হয়ে হেঁটেছেন জনতুষ্টির পথে, আবদ্ধ হয়েছেন সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে, সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বর না হয়ে—হয়েছেন বিশেষ শ্রেণি বা গোত্রের, নিজের পরিচয়কে সীমিত করে এনেছেন একক কোনো ক্যানভাসে, ব্যানারে। অথচ ইতিহাস তাঁকে হাতছানি দেয়নি শুধু, বরপুত্র হিসেবে কৈশোরক পেরোনো বয়সেই করেছেন বরণ ও স্মরণীয় হয়ে ওঠার পথ ও পাথেয়।
অমর একুশের—মহান ভাষা আন্দোলনের কিংবদন্তি ও ইতিহাসের সন্তান কেন সেদিকে না গিয়ে বেছে নিলেন সহজ ও সাধারণের পথ, সেই প্রশ্ন জারি রাখা জরুরি। মনে হতে পারে, নিজেদের প্রত্যাশার জায়গা থেকে হয়তো তাঁর কাছে এমনতর চাওয়া—আকাঙ্ক্ষার ডালি বিছানো। একথা দায় নিয়েই বলা যায় যে, সমগ্র জাতির প্রত্যাশা ছিল, তিনি হয়ে উঠুন সমগ্রের প্রতিভূ-জাতির বৌদ্ধিক অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু-সংকটে, সংগ্রামে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে অন্যতম একজন দিকনির্দেশক-বিবেকের বাতিঘর। ইতিহাসও নিশ্চয় তেমনটাই চেয়েছিল, আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছিল গভীর মমতায়-পরম যত্নে। কিন্তু সেই আহবান-ইতিহাসের অন্তর্গত আর্তি-হৃদয়ের বারতা তিনি শুনতে পাননি, কিংবা বুঝতে চাননি, ইতিহাসের ভেতরের সুষুপ্ত বাসনা-তাঁকে ঘিরে লালিত্য ইচ্ছাসমূহ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঐতিহাসিক এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতির ভাগ্যাকাশে—সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাদপ্রদীপে হাজির হন এক-একজন মহানায়ক। এঁরা জাতিকে দেখান সত্য ও সুন্দরের আলোকমালা, যার মধ্য দিয়ে কল্যাণ হয় বৃহত্তর মানুষের—সমগ্র জাতির। আমরা সেই মহানায়কের পায়ের আওয়াজ পেলেও, সদর্থক অর্থে পায়নি মহানায়কোচিত যথানুগ ভূমিকা। প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা চাপা পড়েছে ধূলি বিছানো দৈনিকের উল্লম্ফনে। নীরবে-নিভৃতে কেঁদেছে জাতি—কারণ তাঁর সূর্যসন্তান পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে আলো ছড়ায়নি। এক্ষণে শরণ নিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্তের দপ্তরের। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন: ‘‘সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন। বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলে মনুষ্য লিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আর একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় করিতেছে, ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘‘এ কিসের দোকান?’’ বালকেরা বলিল, বাঙ্গালা সাহিত্য’’।– বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজে জড়ানো কতকগুলি অপক্ক কদলী।’’ [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সং, পৃ. ৯০]
কলাম লেখার ক্ষমতাকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী যেহেতু অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং সবার মাঝে প্রভাবক শক্তিরূপে বিরাজিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর কলামকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েও যদি সমগ্র জাতির আয়নায় অবলোকন করা হয়, বুদ্ধিজীবীর মানদণ্ডে বিচার ও বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে কি প্রাপ্তির খেরোখাতায় কেবলই প্রশ্নের জন্ম হয়?
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তখনো মহাত্মা গান্ধী হয়ে উঠতে ঢের দেরি। সেই সময় তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানও করছেন না। সদ্য ব্যারিস্টারি পাস করে থিতু হওয়ার চেষ্টা করছেন আজকের দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানেই ট্রেন ভ্রমণরত অবস্থায় শিকার হন মারাত্মক এক বর্ণবাদের। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে ফেরায় জন্মভূমি ভারতে, তারপর একের পর এক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে, যুঝাযুঝির দীর্ঘ বৈতরণী পাড়ি দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন অবিভক্ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা, মহাত্মা, বাপুজি। এবং পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি। স্বাধীনতার পর হলেন ভারত রাষ্ট্রের জাতির জনক। স্বাধীন ভারতেও তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল, আমরা সকলেই কমবেশি জানি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে থেকেও তিনি কোনো কোনো সিদ্ধান্তে যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—তার মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতের প্রকৃত শক্তি। সদ্য স্বাধীন ভারতে তিনি অনশনও করেছেন একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার লক্ষ্যে। এই যে আমৃত্যু লড়াই জারি রাখা, এটাই তো একজন মহানায়কের প্রকৃত স্বরূপ, ইতিহাসের সন্তানের যথাযথ ভূমিকা পালন, একজন কিংবদন্তির দেশ ও জাতির জন্য সর্বোচ্চ নিবেদনের মহোত্তম সব দৃষ্টান্ত, কুর্নিশজাগানিয়া উদাহরণ। মহাত্মা গান্ধীকে ইতিহাস প্রথমে মুখোমুখি করে বড় রকমের তিক্ত অভিজ্ঞতার, তারপর সেই অভিজ্ঞতা নানারূপে—নানা পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে আসে বারবার, তবুও তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে পিছপা হননি, বৃন্তচ্যুত হননি ক্ষণিকের জন্য।
কিন্তু একজন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী যৌবনের ঊষালগ্নেই ইতিহাসের সন্তান হয়েও ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরেননি। ইতিহাসের মহোত্তর পথে উৎসর্গ করেননি নিজেকে। এটা কি কেবলই ধন্ধের জায়গা? যেখানে প্রশ্ন থাকলেও নেই সন্তোষজনক কোনো উত্তর কিংবা জুতসই ফায়সালা। তালাশ করলে, টর্চ মেরে ঠাহর করার চেষ্টা করলে কেবলই মেলে ধূলি ধূসর জায়গা। হাজের নাজেল হয় তর্ক-প্রতর্ক এবং গৎবাঁধা যুক্তি আর মুখস্থ কিছু তত্ত্ব এবং বিতর্কের তুবড়ি ছোটানো কিছু শব্দ ও উদ্ধৃতি চয়নের বাহাদুরি। সংগত কারণে করোটিতে এই প্রশ্ন উথলিয়ে ওঠে বারবার-সহস্রবার। বাঙালি মুসলমানের এটাই কি প্রকৃত প্রতিভা, চিরকালীন ললাট লিখন?
সার্কাসের ঘোড়া দাবড়ানো দিয়ে আর যাই-ই হোক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয় না, প্রতিষ্ঠিত হয় না মানবমুক্তির গণতন্ত্র এবং আকাঙ্ক্ষার কল্যাণরাষ্ট্র। অথচ সার্কাসের ঘোড়া দাবড়ানোর মেহনতই করে গেলেন ইতিহাসের সন্তানেরা—জনতুষ্টিকে মনে করলেন সর্বোচ্চ অর্জন আর একজীবনের মহোত্তম পাওয়া।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জীবন ও কর্মের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব শুধু একবার নয়, একাধিকবার তিনি ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণের ভেতর দিয়ে যাওয়ার অসীম গর্ব ও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। একুশের চেতনায় যে বাঙালি ঘটনাপরম্পরায় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়ে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করেছে। বাঙালির সেই ঐতিহাসিক দিনগুলোতেও তিনি ইতিহাসের দায় মেটানোর সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে নিবেদন করেছেন সম্পূর্ণরূপে। একুশের কিংবদন্তি নিজেই শরিক হচ্ছেন জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের লড়াইয়ে। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘জয় বাংলা’র নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারও আগে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে স্বীকৃত ‘ছয় দফা’ কর্মসূচির পুরোটা প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত সান্ধ্য দৈনিক ‘আওয়াজ’-এ। তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসকের সকল প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে স্বাধীনতার প্রাক পর্বের দিনগুলোতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা শুধু বিস্ময়কর নয়, জাতির প্রয়োজনে-দেশমাতৃকার সংকটে একজন দেশপ্রেমিকের ঝুঁকি নেওয়ার সর্বোচ্চ উদাহরণ। যা আমাদেরকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ করে—শ্রদ্ধায় সাষ্টাঙ্গ আনত ও বিনম্র করে তোলে। সর্বোপরি আমাদেরকে অহঙ্কৃত করে, গর্ব ও গৌরবের মহিমা ও মর্যাদা দেয়।
এক্ষণে মনে পড়ে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কবিতা, ‘স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/ কে বাঁচিতে চায়?/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিব পায় হে,/ কে পরিবে পায়?
দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য পরাধীন দেশের বৌদ্ধিক মানুষের যে সাধনা ও বাসনা থাকে, বাঙালিরও তেমনটাই ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সেই অবস্থান ও ভূমিকা হয়ে পড়ে প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও স্বাধীন দেশের নাগরিকেরা ভালো করেই ওয়াকিবহাল, ‘স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।’ এই প্রত্যয়ের প্রতীতিতে খামতি ছিল কি? দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশগুলোর দিকে লক্ষ করলে ওই প্রশ্নের হ্যাঁ-বাচক উত্তরই দেখা মিলবে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও এ ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ বৈকি। এই দেখায় ‘বাংলাদেশ’ নামক ভূখণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ, আমাদের প্রিয় দেশটি সিকি শতাব্দীর মধ্যে দুবার স্বাধীনতা অর্জনের সৌভাগ্য পেয়েছে। পৃথিবী নামক গ্রহে এ রকম নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। সেই বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন যথাযথ বাস্তবায়িত হয় না, অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে, ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়তেই থাকে কেবলই, তখন প্রশ্ন ওঠে আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর যদি না হয়, তাহলে পাল্টা প্রশ্ন এসে হই হাজের-নাজেল। কাদের জন্য এই ব্যর্থতা? এককথায় বলা যায়, সকলের জন্য। স্বাধীনতা অর্জনে আমরা পারদর্শী হলেও, প্রশিক্ষিত এক সামরিক বাহিনীকে আমরা পরাজিত করতে সক্ষম হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কেন ঈশান কোণের কালো মেঘ দূর করা সম্ভব হলো না—স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দ সময় পরও আমরা কেন মৌলিক অধিকারের জায়গাগুলোতে চোরাবালিতে আটকে আছি তা নিয়ে শুধু রাজনীতি নয়—শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতেও সবিশেষ আলোচনা হওয়া জরুরি? আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে যারা সংহত করেছিল, দেশপ্রেমের চেতনায় যারা রাঙায়িত করেছিল পুরো জাতিকে। যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বৃহত্তর মানুষের কল্যাণার্থে—একটা সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে। যাদের অমর একুশের শহীদ রফিকের রক্তাক্ত লাশ দেখে মনে হয়েছিল নিজেরই আপন ভাই। সেই চেতনায় যিনি লিখেছিলেন ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। সেই চেতনা থেকে কি এই জাতির মহোত্তর মানুষগুলো দূরে সরে গিয়েছিলেন? আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং তাঁর মতো ইতিহাসের সন্তানেরা কি ইতিহাসের দায় মেটানোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সংশপ্তকের যে ভূমিকা পালন প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ছিল, তা করতে কার্পণ্য করেছেন। স্বেচ্ছায় হেঁটে গিয়েছেন জনতুষ্টির পথে। সদ্য লোকান্তরিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জীবন ও কর্মের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই চিত্রই দেখা যায় যে, জনতুষ্টির সহজ পথকেই আরাধ্য জ্ঞান করেছেন তিনি।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সাংবাদিক-সাহিত্যিক ছিলেন। এই দুই মৌল প্রতিভারই রয়েছে বৌদ্ধিক অবস্থান ও দায়। তিনি একুশের কবিতার স্রষ্টা, পরে যেটি প্রথমে আব্দুল লতিফ ও পরে আলতাফ মাহমুদের সুরে গীত হয়ে জয় করেছে বাঙালির চিত্ত। একুশের এই ‘সিগনেচার সং’ শুধু বাংলা ভাষায় নয়, আরও নানা ভাষায়—কমপক্ষে ২৫টিতে অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশ্বের দেশে দেশে গীত হয়।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর গীতিকার হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি হলেও তিনি ছিলেন মূলত কথাসাহিত্যিক। লিখেছেন গল্প ও উপন্যাস, রয়েছে এসবের বেশ কিছু বই। কিন্তু শেষাবধি তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন কলাম লেখকরূপে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তাঁর এই পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠলেও পূর্ববর্তী সময়েও তিনি লিখেছেন বেশ কিছু কলাম।
তিনি যেহেতু ছিলেন পেশায় সাংবাদিক এবং নেশায় সাহিত্যিক। ফলে, তাঁর কলাম ছিল সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রতিভার যৌথ স্ফুরণ। যাতে সাংবাদিকের সূক্ষ্ণ দৃষ্টির পাশাপাশি ছিল সাহিত্যিকের স্বাদু গদ্যের সংযোগ। এ কারণে কলাম লেখাকে তিনি যে মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এ দেশে এ রকম নজির তুলনারহিত। কলাম লেখাতেও যে শিল্পের ছোঁয়া, তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞের অভিমত ও যুক্তির নানামাত্রা জারি থাকতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি।
দৈনিকের পাতায় তাঁর কলাম পড়ার জন্য রীতিমতো অপেক্ষার প্রহর গুনত একনিষ্ঠ কলাম পাঠকেরা। সেদিন পত্রিকার প্রচারসংখ্যাও বেড়ে যেত। পত্রিকা কর্তৃপক্ষও বিষয়টা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিল। এ কারণে তাঁর কলাম প্রকাশের দিনে পত্রিকার ছাপার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হতো। পক্ষে-বিপক্ষে শক্তিশালী এক পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল তাঁর কলামকে ঘিরে। তিনি যুক্তি দিয়ে এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতেন যে, যারা এই যুক্তির সঙ্গে একমত হতে ছিল অপারগ, তারা পর্যন্ত ওই যুক্তির শক্তিতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। তিনি শুধু যুক্তি উপস্থাপনেই অনন্য ছিলেন, এমন নয়, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটাতেও পারঙ্গম ছিলেন অবিশ্বাস্যরূপে—অসম্ভব রকমে। স্মৃতিশক্তি ছিল সাধারণ মানুষের গড়পড়তার বাইরে। দেখা-শোনা-জানা ও পড়ার কোনো কিছুই তিনি ভুলে যেতেন না। যাকে বলে ফটোকপি মেমোরি, তিনি ছিলেন তার সাক্ষাৎ উদাহরণ। চাহিবামাত্র স্মৃতি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নাম-সন তারিখসহ পুরো গল্পই হাজির করতে পারতেন সার্কাসের রিং মাস্টারের মতো। ফলে, তাঁর কলাম পড়ার অর্থই হলো, ইতিহাসের আলপথ দিয়ে দীর্ঘ এক অভিজ্ঞতার পথ পাড়ি দেওয়া ইতিহাসের অলিগলিতে জিরিয়ে আসা। তিনি যুক্তির প্রসাদগুণে যেকোনো বিষয়ে নিজের অবস্থানকে শক্ত ও অপ্রতিহত করতে পারতেন। পাঠককে বুঁদ করে রাখার সম্মোহনী শক্তি ছিল হাতের তালুর ন্যায় চেনা-জানা ও সবিশেষ করায়ত্ত। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর এই প্রতিভা শুধু বিস্ময়কর নয়, তারিফযোগ্যও বটে। তিনি শাণিত যুক্তির নৈপুণ্যে বিপক্ষ-মতের মানুষকেও সম্মোহিত করতে পারতেন।
আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি এই প্রতিভাকে, লেখালেখির শক্তিকে অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে বৃহত্তর মানুষের পক্ষে কাজে লাগাতে পারেননি। এ ব্যাপারের সচেষ্ট ছিলেন, একথা বলাও দুরূহ। একুশের চেতনা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মৌল যে ভিত্তি, তা পূর্ণাঙ্গরূপে আজও বাস্তবায়িত না হওয়া নিয়ে তাঁর লেখালেখিতে কোনো আক্ষেপ-পরামর্শ কিংবা দিকনির্দেশনা মেলেনি, এ ব্যাপারে তিনি কখনো সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।
একথা তো সর্বাংশেই সত্য। এ দেশে একুশের চেতনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে একথা যেমন সত্য। এর পাশাপাশি এই সত্যও ক্রমশ প্রকটিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশে বাংলা ভাষাপ্রীতি ক্রমশ কমছে, ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাও ক্রমশ লঘু হয়ে আসছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার কেবল কাগজে-কলমেই বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা এখনো অবাধ গতায়াতের জায়গা করে উঠতে পারেনি। বাংলা ভাষাবিষয়ক সেমিনারেও ইংরেজির তুবড়ি ছোটানো মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলা মাধ্যম ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি-ব্যক্তিগত সকল প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তিপর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যাবহার শুধু লঘু নয়, অনেকাংশেই উপেক্ষার শিকার হচ্ছে। একুশ মানে মাথা নত না করা। অথচ সেই একুশের চেতনাবাহী জাতিই এখন সর্বস্তরে মাথা নত করতে করতে মাথাকেই শূন্য করে তুলেছে। এসব নিয়ে অমর একুশের কিংবদন্তির কোনো হেলদোল দৃশ্যমান হয়নি। তাঁর লেখালেখিতেও এসব নিয়ে সেই অর্থে কোনো আক্ষেপ ছিল না। অথচ রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার—কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্য করা সুযোগ তাঁর ছিল। এই সুযোগ তিনি কেন কাজে লাগাননি, সে এক ধোঁয়াশার জায়গা বটে।
একুশের চেতনা, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন সদর্থক অর্থে সোচ্চার হননি, ঠিক তেমনই হননি মুক্তিযুদ্ধের মৌলভিত্তিসমূহ বাস্তবায়নে। হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সতত আপসহীন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই জাতি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলের বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছিলেন—সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া নিয়ে একজন বুদ্ধিজীবীর যে ভূমিকা পালন করার দরকার ছিল, সেই ভূমিকা তিনি পালন করেননি।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আমাদের কালের শুধু নয়, চার প্রজন্মের কাছে মহীরুহতুল্য মহান মানুষ। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ধর্মে যখন দেখি, তখন সেই মহীরুহতে ছায়া পড়ে, মহীরুহকে দেখায় না মহীরুহের মতো। এবং না দেখাটায় জাতীর জন্য বেদনার, দেশের জন্য সবিশেষ দুঃখের। এই দুঃখ-বেদনাকে আমরা যদি নিয়তি হিসেবে মেনে নিই, তাহলে আমাদের জন্য আরও দুঃখ আরও বেদনা অপেক্ষা করছে। এবং অচিরেই সেটা আরও দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেবে
একথা সর্বাংশে সত্য যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, যা বাস্তবায়িত হয়নি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে আজও। উপরন্তু আগের চেয়ে ধনী-গরিবের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। কথা ছিল দেশটা হবে সব মানুষের। আদতে দেশটা হয়েছে শাসক চক্র এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বৃত্তাবদ্ধ মানুষদের। এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জায়গায় গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পাকিস্তান আমলের বাইশ পরিবারের জায়গায় কয়েক লাখ পরিবারের হাতে আটকে রয়েছে দেশের সকল অর্থ। কথা ছিল রাষ্ট্র ও তার শাসকেরা সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, কিন্তু বাস্তবে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কিছুসংখ্যক মানুষের। নিরাপত্তাহীনতায় সাধারণ মানুষের ললাট লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসকেরা এখন আর জনগণের ভৃত্যের ভূমিকা পালন করে না, জনগণকে উঠতে বসতে শাসনের নামে অন্যায় অত্যাচার চালায়। কথা ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গঠন করা হবে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া হবে, কিন্তু এসবের কিছুই হয়নি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে রাষ্ট্রের অবস্থান শুধু করুণ নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত মেরুতে। এই অবস্থার জন্য শুধু কি রাজনীতিবিদেরাই দায়ী। নাকি রাজনীতিবিদদের এই আকাঙ্ক্ষায় শিল্প-সাহিত্যের মানুষেরা অনেক বেশি সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে? স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ের লেখক-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সম্পাদকদের যে ভূমিকা, সেই ঐশ্বর্যময় ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশে কেবল পাঠ করা সম্ভব হয়েছে, বাস্তবে দেখার সুযোগ হয়নি। বিশেষ করে নব্বই-পরবর্তী সময়ে। হাতে গোনা দুই একজন বাদে সকলেই ঝাঁকের কৈ হয়ে সমবেত হয়েছে দলজীবিতায়, বুদ্ধিজীবিতায় নয়। এসব নিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর দুঃখ ছিল, কিন্তু সেই দুঃখকে তিনি সংশোধনের শক্তি হিসেবে ব্যাবহার করেননি, একজন বড় মাপের শিল্পীর কাছে যে প্রত্যাশাটা থাকে সব থেকে বেশি। সৈয়দ শামসুল হককে দেওয়া সাক্ষাৎকারের এ প্রসঙ্গ এসেছে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে। তিনি বলেছেন: ‘আমি তো বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, তাঁর কন্যা শেখ হাসিনাকেও দেখেছি। শেখ হাসিনার অসাধারণ অর্জন। দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর মতো রাজনৈতিক নেত্রী এখনো নেই। তা সত্ত্বেও বলব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যিনি প্রথম জীবনে মুসলিম লীগ করা মানুষ এবং গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন নেতা, তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বোধটা আমাকে অবাক করেছে। সেখানে শেখ হাসিনা পৌঁছাতে পারেননি। এটা আমার একটা বড় দুঃখ। ভাবো একবার, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা উঠল, তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, কোনো সোনার গয়না নয়, বেলি ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে হবে। সব শেষে যেটা করেছিলেন, কেউ ব্যারিস্টার লিখতে পারবে না—উকিল থেকে মুহুরি ক্লাস পর্যন্ত সবাই অ্যাডভোকেট। এটা ছিল তাঁর সামাজিক সাম্যের বোধ। তাঁর পরে আর কারও মধ্যে—না তাঁর পরিবার থেকে, না তাঁর রাজনৈতিক দল থেকে—সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার আর দেখা যায়নি। আমরা এতটা পিছিয়ে গেলাম কেন?’
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মতো বুদ্ধিজীবীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। কারণ, উনাদের সক্ষমতা ছিল আকাশচুম্বী। যৌবনের প্রারম্ভে যার অমর একুশের শহীদ রফিকের রক্তাক্ত শরীর দেখে মনে হয়েছিল নিজেরই আপন ভাই। তিনি কেন দেশ ও জাতির দুঃখ-কষ্টে আহত হলেন না? কেন মনে করলেন না জনগণের এই অপ্রাপ্তি, এই বেদনা তাঁর নিজেরই অপ্রাপ্তি—বেদনা কিংবা তাঁর সন্তানের সঙ্গেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রশাসকেরা অন্যায় করছে অনিয়ম করছে। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করলেন না। বৃহত্তর মানুষকে-রাষ্ট্রের সর্ববিধ কল্যাণকে দূরে ঠেলে দিলেন বেছে নিলেন জনতুষ্টি-গোত্রতুষ্টি-দলতুষ্টির পথ, এই ধন্ধ যাওয়ার নয় কোনো কিছুতেই। তর্ক হাজির করে কিছু যুক্তি হয়তো দেওয়া যায়। বলা যায়, বয়স-শরীর-অসুখ বিসুখের কথা। দোহাই দেয়া যায় সংসারের-স্বজনের-সন্তানের-দারিদ্র্যের-বেকারত্বের অভিশাপের-অনিশ্চিত জীবনের- আর্থিক ও সামাজিকী নিরাপত্তাহীনতার। কিন্তু তাতে বুদ্ধিজীবীর ধর্মকে যে উপেক্ষা করা হয়, তাকে আমলে নিচ্ছি কি আমরা?
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন: ‘প্রথমত, আমার একটা ধারণা ছিল, আমি একজন বড় সাহিত্যিক হব। কিন্তু হতে পারিনি। কারণ, আর্থিক টানাপোড়েন। বিয়ে করার পর যখন দেখলাম, গল্প লিখে প্রকাশকের কাছে গেলে ১০০ টাকা দেয়, তাও আবার ১০০ দিন ঘুরিয়ে। এতে সংসার চলে না। কিন্তু খবরের কাগজে রাজনৈতিক কলাম লিখলে মাসে ৪০০ টাকা আসে। ওই যে ঝুঁকে পড়লাম, এরপর আর ফেরা হয়নি। এরপর আবার বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেলাম। তখন তো রাজনৈতিক লেখার খোরাক আরও বেশি করে পেতাম। তিনিও মাঝেমধ্যে ফরমাশ দিতেন—এটা লেখো, ওটা লেখো। সেই কারণে সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন আমার সফল হয়নি। দ্বিতীয়ত, আমার ধারণা ছিল, যেকোনো কারণেই হোক, বাংলাদেশ একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে—হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। কারণ, উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের বিশেষত্বই ছিল মিশ্র সংস্কৃতি, পলি মাটিসমৃদ্ধ সাগরবিধৌত দেশ। এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃতি আরব-পারস্য-টার্কিশ-পর্তুগিজ—সব সংস্কৃতির একটা মিলন-মোহনা মনে করতাম দেশটাকে। তাই ভাবতাম, এ দেশটা আর যা-ই হোক, কখনো সাম্প্রদায়িক হবে না। সুতরাং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে যখন স্বাধীনতার ডাক দিলেন, আমি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি। মৃত্যুর মুখোমুখিও হয়েছি, কিন্তু ভয় পাইনি। আমি এর আগেও বলেছি—তুমি একমত হওনি—আমার সেই আশাটা পূরণ হয়নি। আমার তো মনে হয়, পাকিস্তান আমলে আমরা যতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছি।’
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আমাদের কালের শুধু নয়, চার প্রজন্মের কাছে মহীরুহতুল্য মহান মানুষ। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ধর্মে যখন দেখি, তখন সেই মহীরুহতে ছায়া পড়ে, মহীরুহকে দেখায় না মহীরুহের মতো। এবং না দেখাটায় জাতীর জন্য বেদনার, দেশের জন্য সবিশেষ দুঃখের। এই দুঃখ-বেদনাকে আমরা যদি নিয়তি হিসেবে মেনে নিই, তাহলে আমাদের জন্য আরও দুঃখ আরও বেদনা অপেক্ষা করছে। এবং অচিরেই সেটা আরও দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেবে। কোনো জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর এবং বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান দেশ ও জাতির প্রশ্নে যদি এ রকম হয়, তাহলে তার চেয়ে অনুশোচনার আর কী হতে পারে? সৈয়দ শামসুল হককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী নিজেই বলেছিলেন, ‘আমি একজন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। আমি এ কথা বলব না যে, আমি একজন সৎ মানুষ ছিলাম কিংবা অসৎ মানুষ ছিলাম। আমি আঁদ্রে জিদের সেই কথাটা বিশ্বাস করি, আমি যা, তার জন্য আমি নিন্দিত হতে রাজি আছি; আমি যা নই, তার জন্য আমি প্রশংসিত হতে রাজি নই।’
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অবদানকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা জরুরি, সমধিক জরুরি; এই প্রশ্নও জারি রাখা যে, কেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর দায় মেটালেন না। বুদ্ধিজীবীর যে প্রকৃত ধর্ম, সেই ধর্ম পালন করলেন না। এই প্রশ্ন জারি রেখে এই ভূমিকা কার্যকারণ তালাশপূর্বক এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা যদি সেখান থেকে শিক্ষা নেন এবং পালন করেন বুদ্ধিজীবীর দায় ও দায়িত্ব, তবেই দুঃখ ঘুচবে বাংলাদেশের এবং তখনই সার্থক হবে এই গীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’।