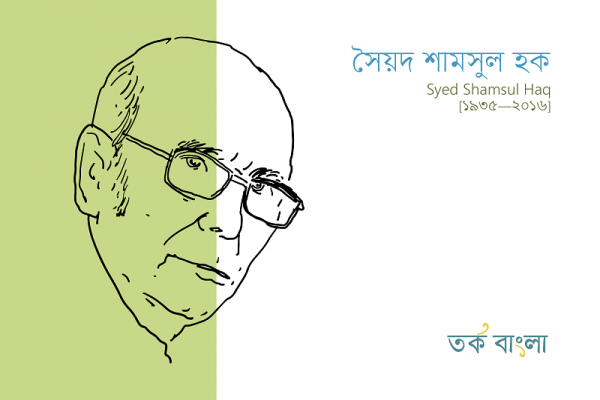
পলাতক জীবন একটা ধাক্কার মত লাগল
সৈয়দ শামসুল হকের সাথে পরিচয় ১৯৮০ সালের শুরুতে দীর্ঘ প্রবাস জীবনের শেষে আমার দেশে ফিরে আসার পর। এর আগে দূর থেকে তাকে দেখেছি, সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ তেমন হয়নি। পরিচয় অবশ্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ১৯৯০ সালের সূচনা লগ্নে লন্ডনে বিবিসিতে কাজ করার সময় থেকে। হক ভাই ৭০ দশকে বেশ বড় সময় ধরে বিবিসিতে কর্মরত ছিলেন। ফলে বিবিসি বাংলার সাথে জড়িত সকলেই তার পরিচিত এবং কাছের মানুষ। সেই সূত্রে লন্ডনে আসা হলে বিবিসিতে তিনি অবশ্যই চলে আসতেন। হক ভাইকে নিয়ে জমজমাট আসর বসে যেত বুশ হাউসের ভূতলের পানশালায়। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম হক ভাইয়ের কথা, যেসব আসরে উপস্থিত থাকতেন শফিক রেহমান, নুরুল ইসলাম, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুর রহমান এবং বিবিসি বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজন।
লন্ডনে স্বল্পকালীন অবস্থানে সময় করে আমাদের বাসায়ও তিনি এসেছিলেন কয়েকবার। মনে পড়ে, ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে আমাদের নবজাতক কন্যাকে দেখার জন্য এক বিকেলে হক ভাই উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের গৃহে। চার মাস বয়সী আমাদের কন্যাকে গুরুজনতুল্য হক ভাই স্নেহের সাথে কোলে তুলে নিয়ে হঠাৎ করেই যেন মহাদুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। বারবার আমাদের কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, ওর মাথা মনে হচ্ছে একটু বাকা এবং এজন্য মনে হয় আমাদের দ্রুতই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ। আমার স্ত্রী হেসে হক ভাইকে শান্ত করে বলেছিল, সদ্য জন্ম নেয়া শিশুদের মাথা এরকম কিছুটা বাঁকাই হয়ে থাকে এবং চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। মানুষ হিসেবে তিনি যে কতটা আন্তরিক-উষ্ণ হৃদয়ের আধিকারী ছিলেন, আমাদের জীবনের এই ছোট্ট ঘটনা মনে হয় সেই পরিচয় দেয়।
বিবিসির পাট চুকিয়ে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আমরা জাপান চলে আসি। জাপানেও যে হক ভাইয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে যাব তা আমি ভাবিনি। ১৯৯৯ সালের শেষদিকে একদিন হঠাৎ জাপানে সেই সময়ের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জামিল মজিদ আমাকে টেলিফোন করেন। তিনি বলেছিলেন যে সৈয়দ শামসুল হক আমার খোঁজ করছেন! খুবই অবাক এবং একই সাথে অসম্ভব আনন্দিত হয়েছিলাম। সেই বার্তা পেয়ে সেদিন সন্ধ্যায় বিলম্ব না করে আমি উপস্থিত হই যে হোটেলে হক ভাই অবস্থান করছিলেন সেখানে। সেবার তাঁর সাথে আরও ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সচিব এবং কবি মনজুরে মওলা। তাঁরা জাপানে এসেছিলেন গোতো অপটিক্স নামের জাপানি এক কোম্পানির আমন্ত্রণে, যে কোম্পানি বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল। তখনই জানতে পারি সৈয়দ শামসুল হক নভো থিয়েটারে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের জন্য বঙ্গবন্ধুর উপর ৩৬০ ডিগ্রিতে দেখানো হবে সেরকম একটি তথ্যচিত্র তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন। হক ভাই সেদিন আমাকে বলেছিলেন, দেখা হয়ে ভালোই হল, কেননা পরদিন তাঁদের দেশে ফিরে যেতে হবে। তবে ছবির কাজের জন্য আরও কয়েকবার জাপানে তাঁকে আসতে হবে। তখন সময় করে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বসতে পারবো। হক ভাইয়ের পরবর্তী জাপানে আগমনের জন্য আমাকে যে ১৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে, তা আমি তখন একেবারেই ভাবতে পারিনি। সেই সূত্রে সম্ভবত ২০১২ সাল থেকে বার তিনেক তিনি জাপানে এসেছিলেন এবং হক ভাইয়ের সান্নিধ্য তখন আমি অনেক বেশি পেয়েছিলাম।
তখনই আমার মনে হয়েছিল নানা পরিচয়ে খ্যাতিমান এই মানুষটির নিজের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে নিয়ে পরবর্তীতে কোন এক সময়ে বাংলাদেশে তাঁর ভক্ত ও পাঠকদের সেটা জানাতে পারলে মন্দ হবে না। বলা যায় এটাই হচ্ছে এই সাক্ষাৎকারের পেছনের কথা, যা আমি এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করছি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পেছনে অন্য যে আরেকটি উদ্দেশ্য একই সাথে ছিল, তা হল এর বাছাই কিছু অংশ জাপান বেতারের শ্রোতাদের শোনার সুযোগ করে দেয়া।
দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে নিজের জীবন, সৃজনশীলতা, সাহিত্য ভাবনার পাশাপাশি একান্ত ব্যক্তিগত অনেক কিছু হক ভাই সেদিন তুলে ধরেছিলেন। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বিরল এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার আমার সংরক্ষণে থেকে যাওয়ায় নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি এবং সাক্ষাৎকারটি এখন নিবেদন করছি আপনাদের সামনে। আমি এখানে নিতান্তই গৌণ, এর মূলের সবটাতেই আছেন সৈয়দ শামসুল হক নামের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মৃত্যু যাকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেলেও নিজের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অমর হয়ে আছেন তিনি।
—মনজুরুল হকের নোট

সৈয়দ শামসুল হকের কোলে মনজুরুল হকের কন্যা মায়া। লন্ডনে তোলা ছবি © মনজুরুল হক
মনজুরুল হক: হক ভাই, আপনি তো নানা পরিচয়ে পরিচিত—কোন পরিচয়টা আপনার নিজের কাছে সবচেয়ে কাছের বলে মনে হয়?
সৈয়দ শামসুল হক: আমার ধারণা যিনি কবিতা লেখেন বা কবিতাও লেখেন তাঁর কবি পরিচয়টাই সবকিছুর ওপরে। কারণ কবিতা এমন একটি সৃজন যেখানে সংকেতে, ইঙ্গিতে, প্রতীকে, রূপাভাসে কথা বলতে হয় এবং সেটার অগ্রাধিকার আছে বলে আমি মনে করি।
মনজুরুল হক: তার মানে আপনি নিজেকে কবি হিসেবে পরিচয় দিতেই তৃপ্তিবোধ করেন।
সৈয়দ শামসুল হক: আমার মনে হয় বরং এইভাবে বলা যেতে পারে যে, কবি যে সত্ত্বা সেখান থেকেই বাকিগুলো উৎসারিত।
মনজুরুল হক: কিন্তু আপনি তো শুরু করেছেন গদ্য দিয়ে—
সৈয়দ শামসুল হক: কাছাকাছি সময় কবিতাও। গদ্য আমি লিখতে শুরু করি ৫২ সালের অক্টোবর বা নভেম্বরে, গল্প দিয়ে। তেমনি ৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি বা জানুয়ারিতে কবিতা শুরু করি।
মনজুরুল হক: তার মানে খুব পাশাপাশি সময়ে...
সৈয়দ শামসুল হক: হ্যাঁ। তবে যেমনটা হয়, বারো বছর বয়স থেকে পদ মেলাবার অভ্যেস ছিল। কাজেই সেইদিক থেকে সব বাঙ্গালির মত আমার মধ্যে কিছুটা তো ছিলোই।
মনজুরুল হক: আচ্ছা এই যে লেখালেখি এর উৎসটা কোথায় আপনি মনে করেন। কোথা থেকে প্রেরণা পেলেন? পারিবারিক কোনো সম্পর্ক আছে কি অথবা পারিপার্শ্বিকতার?
সৈয়দ শামসুল হক: লেখা কাজটাকে যে আমার খুব ভাল কাজ মনে হতো সেটা বোধহয় আমার বাবার স্মৃতি থেকে পাওয়া। আমার বাবা ডাক্তার সৈয়দ সিদ্দিক হোসাইন। উনি বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ৭ টি বই লিখেছিলেন। তো আমি বাবার পাশে ঘুমাতাম। বাবা তো ডাক্তার মানুষ, সকাল থেকে রাত অবধি তাকে রোগী দেখতে হতো। তিনি শেষ রাতে উঠে লিখতেন। বহু রাতে—আমার বয়স তখন কত হবে—ছয়, সাত, আট বা দশ—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম বাবা আমার পাশেই থাকা টেবিলে লণ্ঠনের আলোয় লিখছেন। অন্ধকারের ভেতরে মুখখানা একেবারে ফুলের মত দেখা যাচ্ছে। আর ওই রাতে কাগজের খসখস শব্দ—নিবে, কলমে।
তো, নিশ্চয়ই বালক বয়সে একটা তো প্রভাব পড়ে, একটা ছাপ পড়ে। তখন মনে হতো এই কাজটি খুব ভাল কাজ নিশ্চয়ই, নইলে বাবা কেন করবেন। সেটা একটি দিক। তবে লেখার প্রেরণা, ক্ষেত্র বা উৎস হচ্ছে মানুষ। এবং যে এলাকায় আমার জন্ম, কুড়িগ্রাম, সেটা সেই বৃটিশ আমল থেকেই—বাবার কাছেই শুনেছি—সবচেয়ে পশ্চাৎপদ, সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে অভাবী, ক্ষুধার্ত একটি জায়গা। ছিল নিরক্ষর। এমন কি পরনের বস্ত্রও ছিল না—তারা এত দরিদ্র যে আমি দেখেছি একটা পূর্ণাঙ্গ পোশাক এদের নেই—হাটে বাজারে তারা আসতেন নেংটি পড়ে। একটা হয়ত তেলের বোতল হাতে, সঙ্গে একটা নাতি। নাতিটি উলঙ্গ এবং দাদার পরনে শুধু একটি নেংটি। তো, এগুলোর বোধহয় একটা প্রভাব আছে। তারপর আমার কুড়িগ্রাম শহরেরে পাশ দিয়ে ধরলা নদী, ধরলার ভাঙন, বাড়ি, ঘরদোর ভেঙে পড়ছে, লোকেরা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। আমার যে বাড়িতে জন্ম সেই বাড়িটাই একসময় ভেঙে পড়ে।
মনজুরুল হক: এখন আর নেই সেটা?
সৈয়দ শামসুল হক: না, না। এখন আর নেই সেটি। তো, অনেককিছু কাজ করে। তারপরে আরেকটা কথা বলি—আমার জন্ম ১৯৩৫ সনে। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এবং আমার কুড়িগ্রাম ছিল এমন একটি স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে, জাপানিরা [যে জাপান থেকে আমি কথা বলছি] যদি ভারতবর্ষে বার্মা ভেদ করে আসাম দিয়ে ঢোকে, তাহলে বাংলাদেশে তারা প্রবেশ করবে মোটামুটি কুড়িগ্রামের ওপর দিয়ে। সেজন্য আমি কুড়িগ্রামে সেই ১৯৪০-৪১/৪২/৪৩ সালে, যখন আমার বয়স ৬/৭/৮ হবে, তখন সমস্ত শহর অধিকার করে নিয়েছে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা, যাদেরকে গোরা সৈন্য বলা হতো। গোরা সৈন্যরা শহরের দখল নিয়েছে, তারা পোস্ট অফিস চালাচ্ছে, ইস্টিশন চালাচ্ছে, তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে—সমস্ত শহরে এরা গিজ গিজ করছে। তো এটার একটা প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। আর রাতদিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে এদের আসা-যাওয়া। আমার বাড়ির সড়কটিই হচ্ছে সোজা সড়ক, যেটা দিয়ে নদী পেরিয়ে আসামের দিকে যাওয়া যায়। এবং শোনা যায় যে, এই সড়ক দিয়েই নাকি মীর জুমলা আসাম জয়ে বেড়িয়ে ছিলেন। জয় করতে পারেননি। তো এই যে রাস্তা দিয়ে অনবরত কনভয় যাচ্ছে, কনভয়ের পর কনভয় যাচ্ছে, কামান যাচ্ছে, সৈন্যরা যাচ্ছে, মাথার উপরে সেই ছোট্ট আকারের বিমান দেখা যাচ্ছে। তিনটে, চারটে বিমান একসাথে উড়ে যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে জানি না। এর একটা তো প্রভাব আছেই।
তারপরে ৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তর। আমাদের জয়নুল আবেদিন ভাই যার ছবি এঁকে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। সেই দুর্ভিক্ষ তো ভোগ করেছি। একবেলা খেয়ে থেকেছি। কত বয়স তখন আমার। কত আর হবে ৭ বছর বোধহয় বয়স। ৭ বছর আমার বয়স, আমার মনে আছে যে একবেলা ফ্যান ভাত খেতাম আর একবেলা ছোলা সিদ্ধ খেয়ে থাকতে হতো। তাও তো আমাদের দিচ্ছেন। বাবা-মা না জানি কত কষ্ট করেছেন! সে সময় সন্তানকে খাবার দিয়ে তারা যে যথেষ্ট খাবার পেয়েছে তা মনে হয় না।
আমার বড় বাবা, যিনি আমার বড় চাচা। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রোপাগান্ডা অফিসার। প্রচার বিভাগের একজন অফিসার—কুড়িগ্রামে। তার কাছে সব ভাল ভাল বাক্য শোনা যেত। মানে তাঁকে প্রচার করতে হতো। এটাই তাঁর চাকরি ছিল। যে এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ। যেটা কমিউনিস্ট পার্টিরও সে সময় স্লোগান ছিল যে এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ। এ—ও তা এরকম হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীকালে জানি তো যে ওটা জনযুদ্ধ ছিল না। তো এরকম অনেকগুলো দিক কাজ করেছে। তারপরে ৪৭ সালে দেশভাগ হল। দেশভাগ মানে কী! বিরাট একটা পরিবর্তন এল।
মনজুরুল হক: তখনও তো আপনি ঢাকা আসেননি?
সৈয়দ শামসুল হক: না। তখন, ৪৭ সালে আমি ঢাকা আসিনি। আমার বন্ধুবান্ধব, প্রাণের বন্ধুবান্ধব—শ্যামল, পরিমল, দেবদাস, শিবতোষ রাতারাতি চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানি না! আবছা আবছা শুনি। আর আমার বাবা জিন্না সাহেবকে দেখেছিলেন যে, মিটিঙয়ে সবাই যখন—আছরের ওয়াক্ত হয়েছে—নামাজ পড়ছেন, তখন জিন্না সাহেব মঞ্চের ওপর বসে একা সিগারেট ফুকছেন। তো বাবা সেই থেকে, পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে সন্দিহান হতে শুরু করেন। এটা যে আদতেই ভুয়া একটা ব্যাপার—সেরকম ধারণা তাঁর মধ্যে তৈরি হয়। সেই কারণে যখন পাকিস্তান হয়েছে সেটাতে তিনি খুব একটা খুশি হতে পারেননি। এমনকি ৪৮ সালের মার্চ মাসে আমাকে ঢাকা পাঠালেন—স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করবার জন্য। কিন্তু পাঠালেন মার্চের ৩০ কিংবা ৩১ তারিখে। কেন? তার আগে জিন্না ঢাকা সফর করেছিলেন। তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে ঐ ব্যক্তি ঢাকা থাকাকালীন ছেলেকে তিনি ঢাকা পাঠাবেন না। তো এইরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি।
৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আমি তখন ছিলাম না। আমি পলাতক, তখন আমি বোম্বেতে বাস করি। কিন্তু ৫২ সালও একটা ভীষণ প্রভাব রেখে গেছে আমার উপরে। পাঁচ জন বাঙালি তরুণের সঙ্গে আমি যে ঘরে থাকতাম, সেখানে দরজার ফাঁক দিয়ে রোজ ভোরে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকা দিয়ে যেত। আমরা শেয়ার করে পত্রিকা কিনতাম। পত্রিকা এসে পড়তো দরজার ফাঁকের ভেতর দিয়ে। আর দরজার পরেই আমি শুয়ে থাকতাম মেঝের ওপরে। সবাই আমরা, পাঁচ জনই মেঝের ওপরে ঘুমাতাম। আমার বুকের ওপরে কাগজটা এসে পড়ত। আর আমি ওই ঘুমঘোরে শুধু হেডলাইনটা দেখে রেখে দিতাম। আমার তখন মাত্রই ষোল বছর বয়স হবে। হ্যাঁ, ষোল। তো সেই সময় একদিন হঠাৎ দেখি ঢাকায় গুলি। ছাত্র নিহত। পত্রিকা অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। এটা আমার ওই পলাতক জীবনে একটা ধাক্কার মত লাগল। মনে হল আমি এখানে কি করছি! এখানে কি করছি! আমাকে ফিরে যেতে হবে। ভেতরে একটা টান এল। সে সময় থেকেই সাহিত্যের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল। খুব পড়তাম। আমি যাদের সঙ্গে থাকতাম তারা আমাকে খুব যত্ন করে ইংরেজি বই পড়াতে শুরু করেন।
আমি বহুবার এটা বলি, সেদিন যদি আমরা দুর্বলতম একটা প্রেমের কবিতাও লিখি সেটাই আমার সফলতম মুক্তিযুদ্ধ। বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। বাংলা ভাষা- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অন্য কথা। কিন্তু বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাঙালি যা পেয়েছে সেই বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবং সেদিক থেকে আমি বলে থাকি যে, পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা হচ্ছেন প্রথম প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা...
মনজুরুল হক: এই সংযোগটা কোথায় হল? কেননা আপনার সাহিত্য, সাহিত্যের যে ধারার সাথে আপনি যুক্ত, মানে সৃজনশীলতা; এটা করতে হলে তো আধুনিকতার সাথে সংযোগ থাকতে হয়, বিশ্ব সাহিত্য এবং এর পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। আপনি কুড়িগ্রাম থেকে এলেন এবং আপনার জন্য এই দুয়ারটা উন্মুক্ত করায় কারা ভূমিকা রেখেছিলেন?
সৈয়দ শামসুল হক: এটা ওই বোম্বেতেই। বোম্বেতে সিলেটের এক বাঙালি—আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবেন তিনি।
মনজুরুল হক: আপনার বোম্বেতে যাওয়ার সূত্রটা আমরা জানতে চাই। কবে, কেন আপনি বোম্বে গেলেন? আপনি তো ঢাকা এসেছিলেন ১৯৪৮ সালে।
সৈয়দ শামসুল হক: বোম্বে যাওয়ার কাহিনিটা বলি। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর মত আমি ডাক্তার হই। আমাকে ডাক্তার বানাবেন। কিন্তু ততদিনে আমার মনে হয়েছে, ওই যে বাবাকে লিখতে দেখেছি—ওই রকম একটা কিছু আমি হতে চাই। ডাক্তারি আমার দ্বারা চলবে না। বাবার ওই সত্তাটা আমাকে খুব টানতো। তো বাবা জোর করছেন। বিজ্ঞানে, জগন্নাথ কলেজে আমাকে ভর্তিও করে দিলেন। বললেন যে, তুমি ডাক্তার হতে চাও না, আসলে বিজ্ঞানে তোমার মন নেই বলে। তো বিজ্ঞানে আমি টেস্ট পরীক্ষায় এগার শ ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাবাকে যখন দেখাতে পারলাম যে বিজ্ঞান আমার কাছে একেবারে ফেলনা কিছুই নয়, আমিও পারি। তখনই বাড়ি থেকে আমি পালিয়ে গেলাম। কেননা বাড়িতে থাকলেই বাবা আমাকে জোর করে মেডিকেলে ভর্তি করে দিতেন। কিন্তু আমি ডাক্তার হব না। কেন যে আমার ভেতরে এটা হয়েছে, এই অবোধ আকাঙ্ক্ষা আমি বলতে পারব না। ব্যাখ্যার অতীত।
মনজুরুল হক: পালিয়ে কোথায় গেলেন?
সৈয়দ শামসুল হক: বোম্বে। কলকাতা গিয়েছিলাম। কলকাতা গিয়ে মনে হল যে, বাবা তো এখানে চলে আসবেন আমাকে খুঁজতে। এসেছিলেনও। আমি ওখান থেকে হাওড়া স্টেশন গিয়ে প্রথম যে ট্রেন পাই, বোম্বের সেই ট্রেনে উঠে পড়ি। একেবারে অজানা শহর। এবং সেখানে—অনেক দীর্ঘ কাহিনী—একদিন কোন একসময় হয়ত লিখব। লিখব কী! আমি এখনই শুরু করেছি—‘হে বৃদ্ধ সময়’ নামে। আমার ওই অংশ, যে অংশে ‘আমার দেখা আমার জীবন’। অন্য যে দুটো আত্মজীবনী লিখেছি—‘প্রণীত জীবন’ ও ‘তিন পয়সার জোৎস্না’ তাতে আমি অন্যদিক থেকে নিজেকে দেখেছি। প্রণীত জীবন-এ যেমন আমি দেখেছি, একটি রক্ষণশীল, মুসলিম পরিবার থেকে, যে পরিবারে এক পুরুষই মাত্র ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, সেখান থেকে আমি কি করে বেরিয়ে এলাম। আমার পটভূমিকাটা কি? এটা প্রণীত জীবনের পুরো কথা। আর ‘তিন পয়সার জোৎস্না’ নামে যে দ্বিতীয় একটা আত্মজীবনীর খণ্ড এ বছরই বেরিয়েছে—২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে—সেখানে পঞ্চাশের দশকে আমি ও আমার সাহিত্যিক পরিমণ্ডল, এটা নিয়ে লিখেছি। যা হোক, যেটা বলছিলাম—বোম্বেতে পালিয়ে যাই এবং সেখানে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, সেগুলো তো লিখব একসময় ‘হে বৃদ্ধ সময়’ নামে বইটাতে। যেটা মাথার ভেতরে রয়েছে এখনো। সেখানে সিলেটের ওই বাঙালি যুবক—আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়—তাঁর নাম আশিক উদ্দীন চৌধুরী। কিন্তু বোম্বেতে তিনি অশোক চৌধুরী নামে চলেন-ফেরেন এবং সেই নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। তিনি ডাঙ্গে সাহেবের একজন সেবক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আশ্রয়ে আমি ছিলাম। এবং তিনি আমাকে একসময় বলেন যে, দেখো ইংরেজি না পড়লে, ইংরেজি সাহিত্য না পড়লে, বাংলা সাহিত্যে তুমি কোন অবদান রাখতে পারবে না। ততদিনে আমার মনে হয়েছে যে, আমি গল্প-কবিতা লিখব। তো আমার তো ইংরেজি দেখেই ভয় লাগে, একটা আস্ত বই পড়ে শেষ করব—কী করে সম্ভব! তো উনি আমাকে কোনান ডয়েল [স্যার আর্থার কোনান ডয়েল]-এর ‘দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল’ বইটা পড়তে দিলেন। এবং গল্পটাও আমাকে বললেন আর এটাও বললেন যে, এটি একটি ডিটেক্টিভ উপন্যাস শার্লক হোমসের—এটা তুমি শেষ কর। এবং আমি সত্যিই শেষ করে উঠলাম। ওটা হচ্ছে আমার প্রথম ইংরেজি বই যেটা আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং পরের বই [শুনলে অবাক হবেন] বার্নার্ড শ’র নাটক ‘এন্ড্রোক্লেস অ্যান্ড দ্য লায়ন’ বইটি—ওই অশোকই আমাকে পড়ালেন। তিনি আমাকে তৈরি করেছেন—সাহিত্যে যেমন, তেমনি কমিউনিজমে। বামপন্থী আন্দোলন কি, কমিউনিজম কি, মার্কসবাদ কি, কেমন সমাজ আমরা চাই, কেমন হলে পৃথিবীটা আরও ভাল হবে—এসব পাঠ আমি ওর কাছ থেকে পাই। ওর অনেকটা অবদান রয়েছে আমার ভেতরে। তাঁর কথা আমি আমার তিন পয়সার জোৎস্না বইয়েও একটুখানি লিখেছিলাম। এটা পড়ে একেবারে সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে একদিন একটা টেলিফোন পেলাম যে ওই অশোক চৌধুরীর মেয়ে আমাকে ফোন করেছে। সে বাংলাদেশেই থাকে এবং অশোক চৌধুরী মারা গেছেন। আমার সাথে সেই ৫২ সালের পরে আর কোন যোগাযোগ হয়নি। এত বছর পরে। মেয়েটি বলছে যে, আপনি আমার বাবার কথা লিখেছেন। কে আপনার বাবা? বলল—আপনি যার কথা লিখেছেন, অশোক চৌধুরী। আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এখনো তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারেননি। তবে ফোন নম্বর বিনিময় করেছেন এবং বলেছেন যে, আপনি কখনো সিলেটে এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। তার কাছেই শুনলাম যে অশোক চৌধুরী একসময় বামপন্থার রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন কিছু কিছু কারণে। আপনারা জানেন, অশোক মেহতা, ডাঙ্গে নানা বিভক্তিতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং বোম্বেতে খুব সম্ভবত থাকাটাও আর্থিক দিক থেকে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। পরে তিনি সিলেটে চলে আসেন। যেটা আমি এত বছর পরে তার কন্যার কাছে শুনতে পাই।
মনজুরুল হক: বোম্বেতে থাকার সময় আপনার তো চলচ্চিত্র জগতের সাথেও একটু সম্পর্ক হয়েছিল।
সৈয়দ শামসুল হক: এটা খুবই আকস্মিক। বোম্বেতে সবাই যায়—পালিয়ে—ফিল্মে নাম লেখাবেন বলে। কিন্তু আমার যোগাযোগটা একেবারেই আকস্মিক। সেটা হচ্ছে আমি যে ট্রেনে বোম্বে প্রথম যাচ্ছিলাম, সেই ট্রেনে সতীশ পাকড়াশি বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন—তিনি আমাকে বেঞ্চের উপর বসে থাকতে দেখেন। ওর ওপরে তার বার্থ ছিল। উনি আমাকে ওখানে বসে থাকা দেখে উপর থেকে বললেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা হয়েছে বুঝি। তো আমি চমকে উঠি। তিনি বললেন যে, যখন বের হয়েছো, তখন কিন্তু মাথা উঁচু করে ফিরবে। এই কথা তিনি রাতেই বললেন। এবং বোম্বেতে দুদিন পরে যখন ট্রেন থেকে নামলাম—তখন উনি বললেন, উঠবে কোথায়, চল আমার সঙ্গে, আমি কয়েক দিনের জন্য আপিসের কাজে এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তো একটা হোটেলে উনি আমাকে নিলেন। সেই হোটেলে নির্মল গুপ্ত নামে একজন ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে দেখা, তারা পূর্বেই পরিচিত ছিলেন—তাকে আবিস্কার করলেন পাকড়াশি বাবু। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন যে, এই ছেলেটিকে একটু দেখে রাখবেন তো। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এই নির্মল দা—তিনি কামাল আমরোহী সাহেবের ছবি করবার বাসনা [পোষণ করেছিলেন]—আনারকলি নামে একটি ছবি—যেটি তিনি পরে করে ওঠেননি। তার জন্য ক্যামেরাম্যান সুধীন মজুমদার এসেছিলেন কলকাতা থেকে এবং সুধীন দা নির্মল দাকে নিয়ে এসেছিলেন। এইভাবে আমি নির্মল দা থেকে সুধীন দা, সুধীন দা থেকে কামাল আমরোহীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। কামাল আমরোহী—আমি এখনো তাকে আমার একজন শিক্ষক মানি। অনেক দিক থেকে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।

জাপানে সৈয়দ শামসুল হক। ছবি © মনজুরুল হক
মনজুরুল হক: আপনার যে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে আসা, সেট কি সেই পথ ধরেই?
সৈয়দ শামসুল হক: সেটা কামাল আমরোহীর জন্য। তিনি আমাকে ধরে ধরে শেখাতেন। আমি তাঁর সহকারী ছিলাম—শিক্ষানবীশ সহকারী ছিলাম—শিক্ষানবীশ সহকারী মানে শুনতে খুবই বড় শোনায়, আসলে আমার কাজ ছিল ওর স্ক্রিপ্টটা হাতে রাখা সবসময়, ব্যাগের ভেতরে লাল-নীল পেন্সিল রাখা এবং যখন উনি হাত বাড়াতেন তখন এগিয়ে দেওয়া যে এই শটটা নিতে হবে। উনি কখনো কখনো দয়া পরবশ হয়ে আমাদের বোঝাতেন যে, দেখো এই শটটা—এই জন্য এইভাবে নিচ্ছি এবং একে এই শট বলে। ক্যাজুয়ালি এসব কথা তিনি বলতেন, আর তখন তো গুরু-শিষ্যের পরম্পরার ব্যাপারটা এরকমই ছিল—এটা পুরো ভারতবর্ষীয় একটা রীতি। কেউ ব্যাকরণ ধরে শেখায় না, দেখে দেখে শেখায়। মুচির কাজের মত আর কি! গুরুমুখী বিদ্যা। তো গুরুমুখী বিদ্যা হিসেবে কিছু দূর যাই। যাই হোক ধ্যান-ধারণা যাই ছিল—চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। তারপর সবটা তো… আমি বলি কি আমি স্বশিক্ষিত মানুষ। আমি তো লেখাপড়াও করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্য পড়তে—
মনজুরুল হক: আপনি তো ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে?
সৈয়দ শামসুল হক: হ্যাঁ, ভর্তি হয়েছি। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ছি। দু’বছর পড়ছি। এর ভেতরে তখনকার রিডার যিনি ছিলেন আমাদের ইংরেজি বিভাগের এবং তিনি আমার টিউটোরিয়াল টিচারও ছিলেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন। বিখ্যাত সেই পাকিস্তানপন্থি রাজাকার, একাত্তর সালের। যখন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। যাই হোক, সাজ্জাদ সাহেবের ওখানে। তো সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার লেগে গেল। লেগে গেল কিভাবে—উনি একটা টিউটোরিয়াল ক্লাসে এসে রচনা তৈরি করতে দিয়েছিলেন, কিছু বই বলে দিয়েছিলেন—এইসব বই দেখে, এইভাবে লিখবে। তো আমি সেই পথে না গিয়ে, আমার কাছে যেরকম মনে হয়েছে, আমার বোধবুদ্ধিতে আমি সেইরকম লিখেছিলাম। তো উনি ভরা ক্লাসের ভেতরে বললেন যে, তুমি যদি এইরকম লেখো তাহলে প্রথম শ্রেণী পাবার আশা করতে পারো না। তখন একটা জনরব দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, ৪/৫ জন যারা প্রথম শ্রেণী পাবে, তাদের মধ্যে আমার নামও তুলতো অনেকে। তো উনি বললেন, তুমি প্রথম শ্রেণি পাবে না। চিন্তা করুন যে ভরা ক্লাসে এরকম একটি কথা এবং তারপরে তিনজন সহপাঠিনী ওখানে বসে আছে তাদের সামনে। আমি নিতে পারলাম না। আমি বললাম, স্যার যদি তাই হয়—তাহলে কোন ক্লাসেরই আমার দরকার নেই। এমনকি ইউনিভার্সিটিতেও আর আমার পড়বার দরকার নেই। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আমি বের হয়ে যাচ্ছি। এবং বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে সেই মধু দা’র ক্যান্টিনে ঢুকলাম, বেলা তখন এগারোটা। কেউ নেই ক্যান্টিনে। সবাই যার যার মত ক্লাস করছে। মধু দা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, মধু দা পড়া ছেড়ে দিলাম। মধু দা বললেন, ভাল করছেন। তো মধু দা’র এই কথাটা আমি এখনও খুব মানি। বোধয় ভাল করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়াশোনা শেষ করতাম তাহলে কি হতো!
মনজুরুল হক: এটা তো অনেকটা কাকতালীয় মনে হয়! আপনিও শেষ করেননি। শামসুর রাহমানও তো বোধহয় শেষ করেননি—ইংরেজিতে?
সৈয়দ শামসুল হক: শামসুর রাহমানকে পরে একেবারে একান্ত চাপে একটা বিএ [পাস] কোর্স দিতে হয়েছিল। সেটাও একেবারে পারিবারিক চাপ। আর আমার পারিবারিক চাপের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ৫৪ সালে বাবা মারা গেছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি ৫৬ সালে। স্বাধীন, মুক্ত বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান। যা করছি তাই ঠিক।
মনজুরুল হক: তখন তো একটা ট্রেন্ড ছিল অথবা সবাই যেটা মনে করতো যে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে একটা ক্যারিয়ার ট্র্যাকে যাওয়া। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীও তো বামপন্থা দিয়ে শুরু করে তারপরে সরকারি চাকরি, সিএসপি এসব দিকে সরে গেছেন। আপনার কি কখনো মনে হয়নি, জীবনে একটা পথ খুঁজে পাওয়া দরকার। লেখালেখি তো তখন খুব অনিশ্চিত পেশা— লেখালেখি করে যে জীবনধারণ করা যাবে?
সৈয়দ শামসুল হক: না, না। না মনজুর। আমার এগুলো কিছুই মনে হয়নি। আমি এখন একটু অবাক হই নিজের সেই বয়সের দিকে তাকিয়ে। এই ভাবনাগুলোই আসেনি মাথায়। বাবা মারা গেছেন ৫৪ সালে। আমার বয়স তখন সাড়ে সতেরো-আঠারো। আমার নিচে সাতটা ভাইবোন। বিধবা মা। আর আমাদের পরিবার খুব বিচ্ছিন্ন ছিল এইদিক থেকে যে, বাবা ইংরেজি পড়াশোনা করেছিলেন বলে আমার দাদা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছিলেন। তিনি গ্রামে কখনো ফিরে যাননি। তিনি পরিবারের আর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। শুধু তার নিজের দুই ভাইকে তিনি টেনে নিয়েছিলেন—বড় ভাই ও ছোট ভাইকে। আমরা যখন দেখতে পেলাম যে, একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। তখন আমার ভেতরে একটা বেপরোয়া ভাব কাজ করেছিল যে, যা ইচ্ছে করে তাই করব। দেখি না! কি করলে কি হবে—এই দুশ্চিন্তা আমার কখনো হয়নি। এখনো নেই কিন্তু। আমি কখনোই তেমন ভাবিনি।
কলকাতা গিয়ে মনে হল যে, বাবা তো এখানে চলে আসবেন আমাকে খুঁজতে। এসেছিলেনও। আমি ওখান থেকে হাওড়া স্টেশন গিয়ে প্রথম যে ট্রেন পাই, বোম্বের সেই ট্রেনে উঠে পড়ি। একেবারে অজানা শহর। এবং সেখানে—অনেক দীর্ঘ কাহিনী—একদিন কোন একসময় হয়ত লিখব। লিখব কী! আমি এখনই শুরু করেছি—‘হে বৃদ্ধ সময়’ নামে। আমার ওই অংশ, যে অংশে ‘আমার দেখা আমার জীবন’। অন্য যে দুটো আত্মজীবনী লিখেছি—‘প্রণীত জীবন’ ও ‘তিন পয়সার জোৎস্না’ তাতে আমি অন্যদিক থেকে নিজেকে দেখেছি...
মনজুরুল হক: আপনি কি কখনো চাকরি করেননি?
সৈয়দ শামসুল হক: না। চাকরি করিনি। আবার করেছিও। করেছি। যেমন আজকে এই যে কথা বলছি—এরকম বিবিসিতে, ৭২ সালে আমাকে বেশ কয়েক বছর কাজ করতে হয়েছিল। ওটাই একমাত্র চাকরি। আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কখনো আমাকে উপদেষ্টা, কখনো পরামর্শক হিসেবে রেখেছে। কখনো শুধুই বসিয়ে বৃত্তি দিয়েছে, ভাতা দিয়েছে। এখনো দেয়। এটা দেশের ভালবাসা বলেই আমি মনে করি। তবে না। চাকরি আমি করিনি। আর আমার বাবা—তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে আমার হাত ধরে কয়েকটা আজ্ঞা, নিষেধ ইত্যাদি করে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—সরকারি চাকরি কখনো করবে না। গোলাম হয়ে যাবে। যার জন্য ওইটে খুব মাথার মধ্যে ছিল। আর ওই বিএ পাস করলেই যেটা হতো—হ্যাঁ, যেহেতু আমার লেখার উপরই উপার্জন নির্ভরশীল ছিল—অনেক সময় অনেক ফাঁকা সময় গেছে যখন আমি জানি না আমি পরের দিন কি খাবো! বা পকেটে টাকা থাকবে কিনা? তখন হয়ত বিএ পাসটা থাকলে একটা চাকরি নিয়েও ফেলতে পারতাম। ওইটে বরঞ্চ আমার একটা প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল। না, আমি কখনো ভাবিনি মনজুর, এখনো নয়। এটা বলব না যে, আমি আশাবাদী মানুষ, আবার দুঃখবাদীও নই। নিরাশাবাদীও নই। আমি মনে করি যে সবকিছুর একটা সময় আছে, সময় দিতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে। এই যে অনেকে বলে না—৪৩ বছর হয়ে গেল, [বাংলাদেশের স্বাধীনতার] কী হল? কিচ্ছু হয়নি। আমি বলি, আরে চোখের পলক তো, অপেক্ষা কর। তোমাদের জীবনে না হোক, পরের জীবনে হবে। নিজের আয়ু দিয়ে ইতিহাসকে মেপো না। কিংবা ৭১ সালে যখন—আমি তো সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ অব্দি ঢাকায় ছিলাম। অবরুদ্ধ শহর। এমনকি আমার চোখের সামনেও—ফার্মগেটে, ঢাকার ফার্মগেটে একদিন একটা অপারেশনের সামনে, মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন ছিল আমি সামনে পরে গিয়েছিলাম। আমি সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম। সেই সিগারেটওয়ালা আমাকে তার বাক্সের ভেতরে কিভাবে লুকিয়ে ফেললো—তার দোকানের নিচে একটা বাক্সের মতো ছিল—বড় সিন্ধুকের মতো—তার ভেতরে লুকিয়ে ফেললো। তো নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলেও কোনো সময় ভয় আমার করেনি। এবং ভয় মানে কি—এমনকি মৃত্যু ভয়ও আমার নেই। আমি এই মুহূর্তে যে কথা বলছি, আমি এই মুহূর্তেই চলে যাবার জন্য প্রস্তুত আছি। কারণ এর উপরে আমার কোনো হাত নেই। সুতরাং এটা নিয়ে ভীত হবার কিছু নেই। তেমনি কোনো সংকট আমাকে কাবু করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে, সংকট যেমন আছে, সংকটের সমাধানও আছে। আমি যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখি তাহলে একটা পথ বের করতে পারব। আর এদিক থেকে অনেকে বলেন যে, আমি নাকি অনেক ভাগ্যবান। কোন দিক থেকে—যে এখনো, এই বয়সেও যখন অনেকে বলেন—আমার বয়স এখন ৭৯ চলছে। বাংলায় ঊনআশি বললে আশির ঘরে–ইংরেজিতে সেভেন্টি নাইন বললে সেভেন্টির ঘরে! যাই হোক, এই ৭৯ বছর বয়সেও অনেকে বলেন যে—আপনি নিত্য নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করছেন, লিখছেন। এদিক থেকে সত্যি যে আমি আমার ভাগ্যতারাকে অভিবাদন করি যে, প্রতিদিন আমার কাছে জীবনের নতুন নতুন দিক চোখে পড়ে। নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে আমার ভাবনা উদ্বেলিত হয় এবং সেগুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। এই যে সক্রিয়তা—এইটে কিন্তু আমার জীবনের প্রথম থেকে ছিল। আমি কখনো বাজে সময় নষ্ট করেছি এটা আমার মনে হয় না। বইপড়া, লেখা আর যখন অবসরের সময়, যেমন আমার বন্ধুদের ভেতরে চিত্রকরদের আমি খুব গ্রহণ করেছিলাম—সেই পঞ্চাশের দশকে।
মনজুরুল হক: তারা তো এখনো আপনার খুব কাছের মানুষ, সব সময়ের?
সৈয়দ শামসুল হক: হ্যাঁ। আমার একটা ধারণা ছিল—আমি যে লিখছি, অন্য মাধ্যমের সৃজনশীল মনের সঙ্গে আমি যদি বন্ধুত্ব করতে পারি, তাহলে আমার এই লেখার দিগন্তটা হয়ত আরও প্রসারিত হতে পারে। যার জন্য এটা খুব সচেতনভাবে করা। যার জন্য আমিনুল ইসলাম, রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মুর্তজা বশীর, আব্দুর রাজ্জাক, বাসেত, এমদাদ, কাইয়ুম চৌধুরী এরা সবাই শুধু যে আমার বন্ধু তা নয়, প্রাণের বন্ধু এবং ২/১ জন এমন আছে যারা আমার ভাইবোনের চেয়েও অধিক সম্পর্কিত। এখনো। অনেকেই চলে গেছে। এটা একটা বেদনা, মনজুর, আমার সঙ্গের মানুষ প্রায় সবাই চলে গেছে। এই যে সাহিত্যের কথা বলি, শামসুর রাহমান নেই, হাসান হাফিজুর রহমান নেই, সায়ীদ আতিকুল্লাহ নেই, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ নেই, আলাউদ্দিন আল আজাদ নেই, নাম করতেই থাকব। সব ঘাসের তলায় চলে গেছে। আর আমি যে ঘাসের উপরে আছি, লিখে নিজের সঙ্গে—লেখাটা তো হচ্ছে নিজের সঙ্গে নিজের বন্ধুত্ব স্থাপন। নিজের সঙ্গে নিজের বন্ধুত্ব স্থাপন হচ্ছে লেখা। তো সেই লেখাটা করে যাচ্ছি। তারপরেও এমন মুহূর্ত আসে—এমন সময় আসে—যখন এই বন্ধুদের কথা মনে হয়। এবং একসঙ্গে যে আমরা শুরু করেছিলাম পঞ্চাশের দশকে, সেটা একটা অসাধারণ দশক ছিল।
মনজুরুল হক: আমার মনে হয় সবচেয়ে উর্বরা একটা দশক আমাদের বাংলা সাহিত্যে। এদিককার বাংলা সাহিত্যের দিকে আমি যদি তাকিয়ে দেখি, তাহলে তো মনে হয় এটা স্বীকার করতেই হয়।
সৈয়দ শামসুল হক: সবটা মিলিয়ে। ‘তিন পয়সার জ্যোৎস্না’র ভূমিকাতে এই কথাটা বলার চেষ্টা করেছি। বইটা যখন হাতের কাছে আছে তখন আমি এইদিক থেকে একটা জিনিস পড়তে চাই। লিখেছি যে—এখন আমার মনে হয় এমন একটা দশক মানে সেই পঞ্চাশের দশক—এই বাংলাদেশে কখনো আর আসেনি। আর আসবেও না। এই অর্থে আসবে না যে, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, রাজনীতিতে একসঙ্গে এতগুলো প্রতিভাবানের অভ্যুত্থানও আর ঘটবে না। আবার এত অনেক প্রতিভাবানের বিনষ্ট হওয়াও এর আগে পরে কোন দশকে আমরা দেখব না। পঞ্চাশের দশক বাঙালির জাগরণ, রাষ্ট্রভাষার বায়ান্ন, চুয়ান্নতে মুসলিম লীগের ভরাডুবি, আটান্নতে সামরিক শাসন, পঞ্চাশের দশক রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে উঠতে থাকা, চিত্রকলায় আমিনুল ইসলামদের প্রবর্তনা, সাহিত্যে একদল তরুণ—আমাদের আধুনিকতার চর্চা, বাঙালি তথা রবীন্দ্র চর্চায় ওয়াহিদুল, সানজিদা খাতুনদের আবির্ভাব। আবার এই পঞ্চাশের দশকে বামপন্থা থেকে তরুণদের দ্রুতই বিচ্যুত হতে থাকা। জাগতিক উন্নতির আশায় সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে কারও কারও পাক হয়ে ওঠা। উচ্চ সরকারি চাকরির অশ্বে আরোহন করে বসা। কাজেই সবদিক থেকেই পঞ্চাশের দশক কিন্তু একটা অসাধারণ দশক। এবং এটা অপেক্ষা করছে এমন এক ভবিষ্যতের, কোন সমাজতাত্ত্বিক যখন এটা নিয়ে লিখবেন।
মনজুরুল হক: সাহিত্যের দিক থেকেও এখন পর্যন্ত কেউ কিছু লিখেছে কি? পঞ্চাশের দশক নিয়ে? আমার তো মনে হয় না।
সৈয়দ শামসুল হক: না, না। পঞ্চাশের দশক— শামসুর রাহমান বলতেন যে, এটা হচ্ছে নীরবতার দশক। তো শামসুর রাহমান নেই। বেঁচে থাকলে আমি বলতাম যে, শামসুর রাহমান দেখো, আমি নীরব থাকিনি। অন্তত আমাদের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। সাহিত্যের কথা। না। রাজনীতি বা এ আলোচনা করিনি। দু-একজন আমাকে বলেছেন যে, আপনি রাজনীতির কথা বললেন না কেন? আমি বলি যে, অপেক্ষা করুন, সেটা আরেকজন লিখুক। এ কথা তো কেউ লিখতে পারবে না যে, আমরা সাহিত্যিকেরা কিভাবে বেড়ে উঠেছি। তখন কি পরিবেশ ছিল। পাকিস্তান একদিক থেকে বলছে আরবি হরফে বাংলা লেখো, রোমান হরফে বাংলা লেখো, বাংলার তালব্য শ, দন্তস্য, মূর্ধণ্য ষ মুছে দিয়ে একটাই স কর। র ড় ঢ় এগুলোকে বাদ দিয়ে একটা র কর। সহজ বাংলা লেখো। এই যে এতকিছু পাকিস্তান করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা যদি সেদিন না দাঁড়াতাম—আমি বহুবার এটা বলি, সেদিন যদি আমরা দুর্বলতম একটা প্রেমের কবিতাও লিখি সেটাই আমার সফলতম মুক্তিযুদ্ধ। বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। বাংলা ভাষা- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অন্য কথা। কিন্তু বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাঙালি যা পেয়েছে সেই বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবং সেদিক থেকে আমি বলে থাকি যে, পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা হচ্ছেন প্রথম প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা।
সম্পাদকীয় নোট
বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি সৈয়দ শামসুল হকের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন লেখক, অনুবাদক ও সাংবাদিক মনজুরুল হক। জাপানেই দুই লেখক কথোপকথনের জন্য মুখোমুখি হন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের আমরা ছোট্ট এক টুকরো তর্ক বাংলার ওয়েবে প্রকাশ করেছি। বাকি অংশ প্রকাশিত হবে আসন্ন ছাপা পত্রিকা তর্ক-এ। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করতে পেরে তর্ক বাংলা সম্মানিত বোধ করছে। সাক্ষাৎকারটির অনুলিখন করেছেন কবি সোহেল তারেক।

সাক্ষাৎকারটি পড়ে অনেক কিছু জানলাম। হক ভাইয়ের যে কোনো লেখা বা আলাপ সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক দু-অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে লেখাটিতে দু-একটি শব্দ-ব্যবহার ও বানানে ত্রুটি আছে বলে মনে হয়। যেমন, 'পরবর্তীতে', আবিস্কার'।
jewel mazhar
মে ০২, ২০২১ ০২:০৭

একটানে পড়ে ফেললাম পুরো সাক্ষাৎকার। কবির জীবন ও দর্শনকে জানলাম। পাশাপাশি সাক্ষাৎকার গ্রহণকার মনজুরুল হককেও জানলাম। তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তর্ক বাংলা এইভাবে তার পাঠকদের জন্য নতুন নতুন জানালা খুলে দিক। নিষ্কণ্টক হোক তার পথচলা।
Omar kaiser
মে ০৩, ২০২১ ১১:১০

ভালো লাগলো
সুরঞ্জিত বাড়ই
মে ০৩, ২০২১ ২২:০২

একটানা পড়লাম। সাক্ষাৎকারটি সৈয়দ হককে বিস্তৃত আকারে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে। ধন্যবাদ মনজুরুল হককে সুন্দর একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য।
সরকার আশরাফ
মে ০৮, ২০২১ ০০:৪৫

আহারে! আরেকটু যদি পড়তে পারতাম। এত দ্রুত শেষ হয়ে গেলো লেখাটা! পরবর্তী অংশ পড়ার জন্যে অবশ্যই অপেক্ষায় থাকব। শ্রদ্ধা।
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
মে ১১, ২০২১ ০১:০১

Very Interesting Interview -- liked it.
Syed Kamrul Hasan
জুলাই ০৫, ২০২১ ১৮:২০




সাক্ষাৎকারটি আনন্দ জাগানিয়া এবং অনেক তথ্যবহুল। তর্ক বাংলা এবং লেখক মুমনজুরুল হককেও সাধুবাদ।
শাখাওয়াত বকুল
মে ০১, ২০২১ ১৯:১২