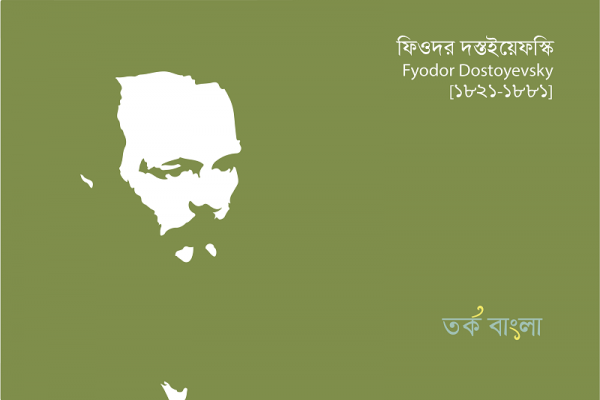ইউক্রেনের গল্প ‘কোস্তিয়া’
কাতেরিনা বাবকিনা
ইউক্রেনীয় কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার। জন্ম পশ্চিম ইউক্রেনের ইভানো–ফ্রাংকিফস্ক শহরে, ১৯৮৫ সালে। কিয়েভের তারাস শেফচেনকো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতা পড়েছেন। এখন কিয়েভে থাকেন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস মাই গ্র্যান্ডফাদার ড্যান্সড দ্য বেস্ট ২০২১ সালে পোল্যান্ডের আঙ্গেলুস পুরস্কার জিতেছে।
গল্পটি মূল ইউক্রেনীয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন হান্না লেলিভ। বাংলায় তর্জমা করেছেন মশিউল আলম
ব্যাপার হলো, ছোটবেলায় যে মানুষটা আমার জামাকাপড় বানিয়ে দিত, সে দাদু (দাদি নয়)। যুদ্ধের আগে দাদু লেদ মেশিনে নানা রকমের জিনিসপত্র বানাত, খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসপত্র। দাদুর আঙুলগুলো ছিল অনুভূতিপ্রবণ আর বেশ নমনীয়। কিন্তু তারপর, মানে যুদ্ধের সময়, দাদুর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল। চোখ, হ্যাঁ, নষ্ট হলো চোখ, পা নয়। তাই দেখে দাদি যুদ্ধফেরত দাদুকে বাড়িতে বরণ করে নিল। যুদ্ধের আগে ওরা ঠিক জুটি ছিল না; ছিল স্রেফ নাচের সঙ্গী। কিন্তু যুদ্ধের পরে, দাদু তখন সত্যিকারের পুরুষ, মানে শক্তসমর্থ, উষ্ণহৃদয়, শুধু চোখ ছাড়া তার সবকিছুই ছিল ঠিকঠাক; সবাই মনে করত যে দাদু এক অবিশ্বাস্য ভাগ্যবান পুরুষ। দাদু শুধু যে ভালো নাচতে পারত তা নয়, লোকজনের সঙ্গে কায়কারবারেও ভালো ছিল; তাই সব সময়ই এখানে সেখানে কোনো না কোনো কাজকর্ম পেত। আর সাধারণত যা করত, যুদ্ধফেরত সৈনিকদের সমিতি টেকনিক্যাল স্কুলে লেকচারের আয়োজন করলে দাদু সেখানে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ নিয়ে লেকচার দিত, কিন্তু কে শোনে তার সেসব লেকচার। নাইট স্কুলে লেকচার দিতে দিতে কেমন করে যেন ইতিহাসের একটা ডিগ্রিও জোগাড় করেছিল দাদু। স্টাইলিশ চশমা চোখে চিকন লাঠিতে ঠকঠক শব্দ তুলে দাদু সবখানে চলাচল করত হেঁটে। সবাই তাকে সাহায্য করত।
দাদু তার লেদ মেশিন ভীষণ মিস করত। পাদোলস্ক সেলাই মেশিনটা দাদুকে একটা লেদের কথা মনে করিয়ে দিত; সেটার ধাতব শব্দ, গ্রিজ দেওয়া সহজ-সাবলীল পার্টসগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত। দাদি তার সেলাই মেশিনে ছেঁড়া কম্বলের ওয়াড় থেকে বানাত চাদর, ছেঁড়া চাদর থেকে বানাত বালিশের ওয়াড় আর ছেঁড়া বালিশের ওয়াড় থেকে বানাত শস্য রাখার থলে। সুতি কাপড়ের বাকহুইটের থলের চেয়ে সূক্ষ্ম কিছু দাদি কখনো বানায়নি; চেষ্টাও করেনি। আসলে, দাদি আর্মি এক্সচেঞ্জে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করত তো, মানে তার কারবার ছিল টাকাপয়সা আর কানেকশন নিয়ে; তাই কাপড়চোপড় যা চাইত, তা-ই যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়েই বানিয়ে নিত।
দাদু সেলাই মেশিনটার স্পর্শ ভালোবাসত। ভালোবাসত ওটার গায়ে থাবা দিতে, আদর করতে, হুইলটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে, সুই সঞ্চালনের শব্দ শুনতে, বা সুইয়ের নিচে এক শিট কাগজ রেখে দিতে, তারপর সেই কাগজে তৈরি হওয়া ছিদ্রগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে। সেলাই মেশিনে সুতা কীভাবে গাঁথতে হয় তা দাদু শিখে নিয়েছিল, সেলাইয়ের ফোঁড় কত বড় হলো বা কত ছোট হলো, তা-ও ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুঝে নিতে পারত; আর সেলাইয়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারত সুইয়ের গতি কম না বেশি। সুতা কী করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ঘুরে ঘুরে এত সহজে সেলাই বোনে, তা বোঝার চেষ্টায় দাদু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিত। অবশ্য আমি নিশ্চিত করে এসব বলতে পারি না; স্রেফ কল্পনা করে বলছি; কারণ, দাদুটা আমার জন্মের সময় থেকেই সেলাইয়ের কাজে খুব ভালো ছিল।
আমি ঠিক জানি না, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে কে কীভাবে সামলে নিয়েছিল; কিন্তু আমার দাদু খুব দরকারি লোক হয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের কিছুই ছিল না, এমনকি খাবার-দাবারও ছিল না। দাদু-দাদি দুজনেই ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছিল, মা একটা স্কুলে কাজ করত। পড়াত সাহিত্য, একটা হোপলেস সাবজেক্ট, যেটার জন্য কেউ টিউটর রাখার ধার ধারত না। তাই আমাদের কোনো বাড়তি আয়-রোজগার ছিল না। অবশ্য ছাত্রছাত্রীরা মাকে ভালোবাসত। পাস করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তারা বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন উপলক্ষে মাকে ফুল উপহার দিতে আসত। কিন্তু জানেনই তো, ফুল খেয়ে বাঁচা যায় না।
সেলাই ছিল একমাত্র দাদুর কারবার, আর কারও নয়; সেলাই ছিল একধরনের বিনোদন, যা শুধু দাদুই উপভোগ করতে জানত। দাদু আমাকে গিফট হিসেবে হয়তো একটা সবুজ বা লাল শার্ট বানিয়ে দিত; সেটার সেলাই হতো নিখুঁত সুন্দর, আমার গায়ে ফিটও হতো দারুণভাবে; আর বোতামের ঘরগুলো হতো সব একই রকমের নিখুঁত। বা হয়তো একটা হ্যান্ড-পাপেট বানিয়ে দিত; আমি সেটার ভেতরে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে হয়তো ভালুক বা হাতির মতো অভিনয় করতাম। পাপেটটার মুখ আর চোখগুলো সেলাই করত খুব শক্ত, মজবুত সুতা দিয়ে, আর সব সময়ই সেই সুতার রং হতো ঘন খয়েরি।
তারপর আমি ঠিক করলাম, দাদুকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা গোপনে একটা চুক্তি করলাম; চুক্তিটাও ছিল বেশ মজবুত, তার কোনো নড়চড় ছিল না। ওই চুক্তির কারণে আমরা পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হলাম, ওই চুক্তির কারণেই আমাদের মেজাজ-মর্জি ঠিক থাকল; চুক্তিটা আমাদের দুজনের জন্যই খুব উপকারী হলো। তখন আমার বয়স প্রায় নয় বছর, আর দাদুর প্রায় সত্তর।
একদিন দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘দাদি কাপড়ের ছিটগুলো কোথায় রাখে?’
আমি জানতাম, দাদি আর্মি এক্সচেঞ্জে কাজ করার সময় থেকে আমাদের বাড়িতে প্রচুর ছিট কাপড় আসত; উন্নত মানের সুন্দর কাপড়ের অবশিষ্ট টুকরো-টাকরা রোল করে গুটিয়ে নিয়ে আসত দাদি। দাদির ওই সব ছিট কাপড়ের প্রতি দাদুর কোনো আগ্রহ ছিল না; দাদু পছন্দ করত সরল সাধারণ কাপড়; সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত মোটা সুতি কাপড়। কিন্তু দাদুর নিশ্চয়ই জানা ছিল দাদি তার ছিট কাপড়গুলো কোথায় রাখত। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে একমাত্র যে কাজটা করতে হতো, তা হলো দাদুকে জিজ্ঞেস করা; বাড়ির কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে—সবকিছু দাদু অন্য সবার চেয়ে ভালো জানত। তাই তাকে জিগ্যেস করলে সে ঠিক ঠিক বলে দিত জিনিসটা কোথায় আছে, তার প্রায় কখনোই ভুল হতো না।
আমি চাইছিলাম মেরুন রঙের ভেলভেট বা রেশমি কাপড়। আমার মনে হতো ওগুলো বিলাসী কাপড়, ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোতে যেসব কাপড় দেখা যেত। মা খুঁজে খুঁজে ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলো বাসায় নিয়ে আসত, একদিন বা দুদিনের জন্য, স্রেফ পাতা উল্টিয়ে দেখতে আরকি। কিন্তু দাদির তখন ছিট কাপড় নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত ছিল না। সে তখন বাজারে চিনি আর শস্যদানা বিক্রি করা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আমরা যাতে না খেয়ে মারা না যাই, সে জন্য দাদি তার সেলাই করা প্রতিটা বলে ভর্তি করে চিনি আর গম-ভুট্টা-চাল—এসব শস্য সংগ্রহ করে রেখেছিল। মা স্কুল থেকে ফিরে ইংরেজি পড়ত; মা মনে করত পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাটাতে পাস করলেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সে পেশাটা পাল্টে ফেলবে। তখন সবাই ইংরেজি শিখতে চাইত। মা কিছুদিন ‘ওয়ার্ডরোব’, ‘অবসোলিট’, ‘এডুকেশন’—এই সব শব্দ নিয়ে ধস্তাধস্তি করল, তারপর পরীক্ষায় পাসও করে গেল; কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা সে রপ্ত করতে পারেনি।
গল্পটা লম্বা, সংক্ষেপে বলি, আমার আর দাদুর দিকে কারও ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমি বলতাম, দাদু মন দিয়ে শুনে যেত। আমি বলতাম আমার জামা কেমন হতে হবে; সোজা, হ্যাঁ স্ট্রেইট; কিন্তু কোমরটা একটু সরু হবে (একটুখানি), সামনের দিকে কুঁচি থাকবে (দাদু হেসে জিগ্যেস করত, ‘কুঁচি লাগবে কেন, নাস্তিয়া?’), যেন শোল্ডার প্যাড ঢোকানো যায় (দাদির জ্যাকেট থেকে কেটে বের করে নেওয়া শোল্ডার প্যাড), আর থাকবে তিনটা বোতাম (আমি নিজেই লাগাব!), গলাটা হবে গোল, হাতা থ্রি-কোয়ার্টার, আর জামার শেষ প্রান্তটা থাকবে হাঁটুর ওপরে, কিন্তু খুব বেশি ওপরে নয়।
দাদু আঙুল দিয়ে খুব যত্ন করে আমার শরীরের আকারটা মেপে নিল; আমার দুই কাঁধ, নিতম্ব, হাত, কণ্ঠার হাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাপ নিল। বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, তখন সে কার্পেট তুলে মেঝেতে বিছিয়ে দিল মেরুন রঙের বেশম কাপড়। তারপর তার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যেভাবে কাপড়টা কাটল, সেভাবে আর কেউ জামার কাপড় কাটতে জানে না। কাপড় কাটার কাজে ব্যবহার করল দুই দিকে ধারালো একটা বিশেষ রকমের ছুরি; ছুরিটা দাদু নিজেই বানিয়েছিল অনেক আগে। কাঠের মেঝেতে ছুরির আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ পড়ে গেল অনেক; কার্পেটের নিচে মেঝেতে আগে থেকেই অনেক দাগ ছিল, এবার আরও বেড়ে গেল। দাদু সেলাই করত খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু এত ভালো সেলাই করত যে সে জন্য অপেক্ষা করা যেত।
তো স্কুলে আমার প্রথম নাচের অনুষ্ঠানের জন্য আমি সেরা ড্রেসটা পেলাম। সেই সময় হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরা ছিল ফ্যাশন; আমি কয়েকটা পুরোনো মোটা কালো স্টকিং কেটে নিয়ে দাদুকে দিলাম, দাদু সেগুলো সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে দিল। মোজা দুটো সব সময় খালি নিচে নেমে যেত; কিন্তু ওই রকম সুন্দর একটা ড্রেস পরলে মোজার দিকে কারও চোখ যায় না।
দাদু কখনো জানতে চায়নি ওই ড্রেসটা পরে আমার কেমন লাগত। দাদু শুধু জানতে চাইত, পরেরবার আমার জন্য কেমন জামা তাকে বানাতে হবে।
পরের তিনটা বছর আমাদের এভাবেই কেটে গেল। মা যেসব ম্যাগাজিন বাসায় নিয়ে আসত, আমি সেগুলো পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে যা কিছু দেখতাম, সব দাদুর কাছে বর্ণনা করতাম: কাপড়, প্যাটার্ন, স্টাইল, কুচি, ল্যাপেল, দৈর্ঘ্য, আকৃতি ইত্যাদি। আমরা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দাদির ছিট কাপড়গুলো চিনে নিতাম, বেছে বেছে রাখতাম যত্ন করে। তারপর অপেক্ষা করতাম কখন বাসার সবাই বাইরে যায়। সবাই যখন চলে যেত তখন কার্পেটটা তুলে মেঝেতে কাপড়গুলো বিছিয়ে দিতাম; দাদু সেগুলো কাটত; আঙুলের স্পর্শে আন্দাজ করে করে কাটত, আর কাঠের মেঝেতে আরও কাটাকুটির দাগ তৈরি হতো। আজও সেই দাগগুলো রয়ে গেছে, মেঝেটা চেঁছে পালিশ লাগানো হয়নি; সেই কার্পেট কবেই জরাজীর্ণ হয়ে বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু আমার দর্জি দাদুটার হাতের সেই সব কাটাকুটির দাগগুলো এখনো রয়ে গেছে; বছরের পর বছর ধরে পায়ের ঘষায় মুছে যাওয়ার উপক্রম হলেও এখানে ওখানে দিব্যি রয়ে গেছে।
দাদু ছিল আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু; আমি কী ভাবতাম না ভাবতাম—সব দাদু জানত; আমার সব গোপন কথাই তার জানা ছিল; দাদুর বানিয়ে দেওয়া আমার একটা ড্রেস ক্লাসমেট মারিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, আমার সেই অপরাধও দাদু মাফ করে দিয়েছিল। ওই প্রথম আমি কিছু বিক্রি করেছিলাম; বিক্রি যে করতে পেরেছিলাম, সে জন্য আমার গর্ব হয়েছিল; কিন্তু একটা কারণে দাদু সেটা পছন্দ করেনি। দাদুর সোভিয়েত-স্টাইলের মন আমার চুপি চুপি বেচাকেনা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু আমি জামা বিক্রি করা চালিয়ে গেলাম, অবশ্য চুপ চুপ করে। দাদু আমাকে কখনো জিগ্যেস করত না এই জামাটা কোথায় গেল, ওই জামাটার কী হলো, কিংবা কোন জামাটা আমি বেশি পরতাম। লুকিয়ে লুকিয়ে জামা বিক্রি করে পাওয়া টাকাগুলো আমি চুপ চুপ করে মার পার্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতাম; ছোট ছোট নোট করে রাখতাম যাতে মনে হয় টাকাগুলো পার্সের মধ্যে সব সময়ই ছিল। বা হয়তো বলতাম যে আমি টাকাগুলো রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি; কিংবা হয়তো ওই টাকা দিয়ে কেক, কোক—এসব কিনে খেতাম; নিজের জন্য লিপস্টিক কিনতাম, পোস্টার কিনতাম।
একটা সময়ে আমার জামার চাহিদা কমতে থাকল; তখন জামার বদলে পরতাম বেল-বটম জিনস আর শার্ট; টি-শার্ট আর সোয়েটার। দাদুর সঙ্গে সময় কাটানো ক্রমেই কমতে লাগল। আমি রেডিওতে যেসব মিউজিক শুনতাম, দাদুর সেগুলো ভালো লাগত না। আর এমন চিন্তাভাবনাও বেশি ছিল না যেগুলো দাদুর সঙ্গে শেয়ার করা যেত। দাদুর সব গল্প আমার শোনা হয়ে গিয়েছিল; দাদি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই আর বাজারে যেত না, প্রায়ই দাদুর পাশে বসে থাকত; দাদু সেলাই মেশিনের হ্যান্ড হুইলটা ঘোরাত আর দাদি দাদুর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত, যেন আগে কখনো অত ভালো করে দাদুকে দেখেনি, তাই এখন সেটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।
দাদু তখনো আমার জন্য জামাকাপড় বানাত; অবশ্য সেলাইয়ের গতি ক্রমেই আরও কমে আসছিল। কিন্তু সবগুলো জামাই হয়েছিল দারুণ জমকালো; একদম শেষটা পর্যন্ত, যেটা পরে আমি মিউজিক স্কুলের আবৃত্তি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তারপর দাদু চুপচাপ মরে গেল, তার সেলাই মেশিনটার সামনে। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একা হয়ে পড়েছিল বেচারা; পরে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম, কী কারণে যেন দাদু কয়েকটা বই আর অনেকগুলো পুরোনো ফটোগ্রাফে সেলাইয়ের ফোঁড় করে রেখে গিয়েছিল।
দাদুর সেলাই করা জামাগুলোর একটাও আমি ফেলে দিইনি। ওগুলো অন্ধ ভালোবাসা আর অপরিবর্তনীয় স্মৃতিতে ভরপুর। যদি পারতাম, তাহলে দু-একবার পরার পর ক্লাসমেটদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া জামাগুলোও হয়তো আবার কিনে নিতাম।
***
তার প্রায় বিশ বছর পরে শাস্তিয়ার যুদ্ধে অন্ধ হয়ে যাওয়া কোস্তিয়া নামের এক তরুণ ঘটনাক্রমে এসে জোটে আমার অ্যাপার্টমেন্টে; ব্যাপারটা আমার জন্য হয়ে ওঠে ভীষণ অসুবিধাজনক।
শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় আমি তাকে তুলে নিয়ে আসি; সে তখনো ছিল আউটপ্যাশেন্ট ক্লিনিকে, যদিও ইতিমধ্যে ব্রেইল শিখে নিয়েছিল, কাজ খুঁজতে শুরু করেছিল আর কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করছিল। সেদিন আমাদের প্ল্যানটা ছিল সিম্পল: নদীর ধারে হাঁটতে যাওয়া; গাছে গাছে ফুল ফুটছিল, নতুন পাতা গজাচ্ছিল, আমরা সেসবের মধ্যে শ্বাস নেব, পাখিদের কলকাকলি শুনব, শুনব শিশুদের হাসি। আমি তাকে বলে-কয়ে শপিং মলে যেতে রাজি করাতে পারতাম, সেখানে তার জন্য খুব সুন্দর কিছু দৈনন্দিন কাপড়চোপড় কেনা যেত; কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম, তাকে শপিং মলে যেতে রাজি করানো যেত না, একদমই না। কারণ, সেদিন সন্ধ্যায় তাকে আমার নিয়ে যেতে হতো নদীর ওপারে তার মা-বাবার কাছে; সে উইকএন্ডটা মা–বাবার সঙ্গেই কাটাবে বলে প্ল্যান করেছিল।
শেষমেশ কোস্তিয়ার চিকিৎসার খরচপাতি আমিই দিয়েছিলাম; উদ্ভট যুদ্ধটা (নিজেদের দেশের মধ্যে যুদ্ধ) থেকে ফিরে আসা সৈনিকদের হেল্প করার সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিল এটাই, নিজের মানিব্যাগ খুলে সাহায্য করা। ভলান্টিয়ারদের একজন আমাকে বলেছিল, কোস্তিয়াও চেয়েছিল আমি যেন ওর কাছে যাই, ওর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু কীভাবে আমাদের দেখা হবে? কীভাবে আমরা পরস্পরকে দেখব, যখন একজনের চোখই নেই?
আমরা নদীর দিকে যেতে যেতে বৃষ্টি শুরু হলো। আমি হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করছিলাম, সব সময় হাসছিলাম, যেন কোস্তিয়া আমাকে দেখতে পাচ্ছিল, নির্বোধের মতো হেসেই যাচ্ছিলাম। আসলে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল, তাই বকবক করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোস্তিয়াকে আত্মবিশ্বাসী আর গম্ভীর দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল আমাকে তার খুব একটা ভালো লাগেনি।
বৃষ্টি শুরু হলে দুজনের কারোর হাঁটতে যাওয়ার ইচ্ছেটা আর রইল না। আমরা সেতুর দিকে যেতে লাগলাম, কোস্তিয়ার মা-বাবার কাছে। কিন্তু যেতে যেতে আমার মনে হলো, পুরো শহরটাই বুঝি সেতু পার হওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে; মনে হলো আমাদের হয়তো পরদিন সকাল পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যামেই আটকা পড়ে থাকতে হবে।
এই অবস্থায় ঘণ্টা দুয়েক প্রফুল্ল থাকার একটা পথ ভেবে বের করতে হবে; অন্ধ কোস্তিয়ার মন ভালো রাখার একটা উপায় খুঁজে পেতে হবে আমাকে, যে কিনা আমাকে খুব একটা পছন্দ করে না।
‘মুভি দেখতে যাবে?’ আমি বললাম। বলার পরে আমার বুঝতে একটু সময় লাগল যে কিছু একটা ভুল হয়ে গেল।
একটা দীর্ঘ নীরবতা চলল। কোস্তিয়া বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট; বছর দশেকের হবে, কিংবা হয়তো আরও বেশি।
দীর্ঘ নীরবতার পর কোস্তিয়া অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অকপট, প্রাণখোলা, সত্যিকারের অট্টহাসি। আমিও জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হলো আমাকে কোস্তিয়ার ভালো লাগেনি।
‘কোনো মুভি না,’ কোস্তিয়া বলল, ‘কোথায় যেতে চাও তুমি?’
‘আঁ?’
‘হুম...কোথায় যেতে চাও?’ কোস্তিয়া একই প্রশ্ন আবার করল।
আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাতির সামনে; গাড়ির উইন্ডশিল্ডের ওপরে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছিল, ওয়াইপারগুলো চলছিল সর্বোচ্চ গতিতে।
‘আমি তো চাইছিলাম বাসায় যেতে,’ আমি বললাম, ‘দিনটা লম্বা, অনেক কাজ করতে হয়েছে আমাকে, খিদে পেয়েছে, বাসায় যেতে চাই। বাসায় যেতে, হ্যাঁ।’
আমি সাধারণত বাসায় পুরুষদের দাওয়াত করি না; কিন্তু কোস্তিয়াকে সেই অর্থে ঠিক পুরুষের মতো মনে হচ্ছিল না। সে কিচেন টেবিলের সামনে বসে ছিল; তার মধ্যে একটা যেন সারল্য ছিল, যেন ভালো একটা-কিছু ছিল।
আমি ফ্রাইং প্যানে দুটো স্টেক ঢুকিয়ে স্টোভের ফ্যানটা অন করে দিলাম। সে উঠে নিজের চারপাশের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল; তারপর একটা হাত রাখল শেলফের ওপর, শেলফের জিনিসপত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল: একটা মোমদানি, আমার নোটবুকগুলো, গাড়ির স্পেয়ার চাবি, রাজ্যের খুঁটিনাটি, আর ফ্রেমহীন ফটো: মা, দাদি, দাদুর ছবি; দাদুর পরনে ইউনিফর্ম, যুদ্ধের ঠিক পরপরই তোলা ছবি; আর কিছু ছবি আমার বন্ধুদের।
স্টোভের ফ্যানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, স্টেকের মাংস ফ্রাই হচ্ছিল। আমি জানালা খুলে একটা সিগারেট জ্বালালাম; বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরছিল। আমরা একসঙ্গে ডিনার করতাম, আমি কোস্তিয়াকে গাড়িতে করে তার মা-বাবার কাছে রেখে আসতাম; ভালো লাগছিল যে আমাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়নি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি হয়তো ওকে বলব যে ও টাকাপয়সা রোজগার করে ওর চিকিৎসার টাকাটা আমাকে ফেরত দেবে, বা এই ধরনের কিছু হয়তো বলতাম। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটল না; ফলে কোনো চাপ আর বোধ হচ্ছিল না।
আমি প্রথমে টের পাইনি যে কোস্তিয়া কিছু বলছিল।
বাইরে মাটির কোথাও আধখাওয়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বৃষ্টি থেকে সরে ঘরের ভেতরে এসে আমি বললাম, ‘আঁ?’
‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, নাস্তিয়া,’ সে আবার বলল, ‘এখনো ছোঁয়া থেকেই তোমাকে আমার মনে পড়ে। এখনো।’
আমার প্রথমে মনে হলো, বেশি কথা না বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে ওকে বিদায় করি। ভাবছিলাম ওকে বলব, ভাগো এখান থেকে! চোখ নেই? তো কী হয়েছে তাতে? কী মনে করেছে সে? কাকে বলছে এই ধরনের কথা? কী মনে করে সে? কিন্তু তারপর ঝট করে মনে হলো, আমার সঙ্গে কথা বলছিল যে, সে আসলে কোস্তিয়া নয়, অন্য কেউ। অন্য কেউ কথাটা বলেছিল, কোস্তিয়া শুধু তার পুনরাবৃত্তি করল, কথাটা আমার কাছে পৌঁছে দিল।
কোস্তিয়ার হাতে ছিল আমার দাদুর একটা ফটোগ্রাফ; তাতে কয়েক সারি সেলাইয়ের ফোঁড়। আমি ভাবতাম, বুড়ো মানুষটা গভীর বিষণ্নতা মুহূর্তগুলোতে ওই খেয়ালিপনাটা করত
কোস্তিয়া ফটোটার গায়ের ঘষা-খাওয়া ছিদ্রগুলোর ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে আস্তে আস্তে আবার বলল, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, নাস্তিয়া।’
মন্তব্য-পরামর্শ লিখে কতগুলো বই দাদু আমার জন্য রেখে গেছে? মজার মজার মন্তব্যসহ, কিংবা মজার নয় এমন মন্তব্যসহ কতগুলো ফটোগ্রাফ রেখে গেছে আমার জন্য?
‘এখনো ছোঁয়া থেকে তোমাকে আমার মনে পড়ে।’
আমি চিনি না, এমন লোকজনের পাঠানো পুরোনো পোস্টকার্ডগুলোতে দাদু সেলাই মেশিন দিয়ে ছিদ্র করে করে রেখে গেছে আমাকে বলার জন্য তার কাছে ওই সব লোকজন কী, আমার কাছেও তাদের মূল্য কত। দাদু আমাকে কত ভালোবাসত যে ওই মুহূর্তটার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতেই পারিনি? এত এত দীর্ঘ, অসীম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত? এই সম্পদ হয়তো আমি কখনোই খুঁজে পেতাম না; হয়তো ওই চিঠিগুলো কখনোই বুঝতাম না; কিন্তু দাদু নিশ্চয়ই জানত যে আমি ওগুলো একদিন খুঁজে পাব এবং বুঝব।
কোস্তিয়া পড়া শেষ করল, ‘এখনো।’