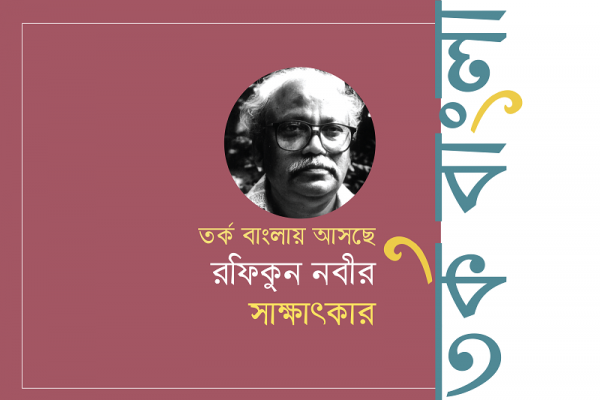পর্দা ও রুচি পরিবর্তনের ইতিহাস!
উত্থান ও পতন মানুষের বেলায় শুধু নয়, কারখানার বেলাতেও ঘটে। বহু শিল্প ও কারখানা এখন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, সময়ের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে। প্রযুক্তির উন্নতির কারণে, মানুষের রুচি পরিবর্তনের জন্য অনেক পণ্য বা দ্রব্য হারিয়ে গেছে, সেগুলো তৈরির কারখানাও উঠে গেছে, বা যাচ্ছে। যেমন ধরুন এখন আর কেউ টাইপরাইটারে লেখেন না, কম্পিউটার চলে এসেছে। হাতঘড়ির চলও কমেছে অনেক, স্মার্টফোনই তো সময় বলে দেয়। ক্যাসেট বা সিডিতে এখন আর কাউকেই গান শুনতে দেখা যায় না, ইউটিউবই বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছে। কাজেই টাইপরাইটার, টুইন-ওয়ান টেপরেকর্ডার তৈরির কারখানা এখন আর নেই। হাতঘড়ি তৈরির কারখানা টিকে আছে শৌখিন লোকদের কল্যাণে।
বড় পর্দাতেও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার চল আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। করোনার কারণে ওভার দ্য টপ [ওটিটি] প্ল্যাটফর্মের চাহিদা বেড়েছে, বড় পর্দার সামনে ভিড় কমেছে। বন্ধ হয়েছে অনেক সিনেমা হল। মাল্টিস্ক্রিনগুলোও আছে চাপের মুখে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সময় বোধ হয় এখনই পার করছে বাংলাদেশ। এমনিতেই আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প মৃতপ্রায় ছিল, মহামারি এসে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য কফিন তৈরি করে ফেলেছে। আগে এমন হাহাকার না থাকলেও, অন্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রকেও যাত্রার শুরু থেকেই চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে।
সেই ১৯৫৬ সালের ‘মুখ ও মুখোশে’র কথা যদি বলি, পূর্ব বাংলার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, সেটি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তারপরও এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। এরপর ১৯৫৯ সালের উর্দু-বাংলা মেশানো ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ ছবিটিও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দর্শক মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ষাটের দশকের শুরুর দিকে উর্দু ভাষায় নির্মিত ছবিতে পরিমাণমতো বাণিজ্যিক উপাদান মেশাতে শুরু করলে মানুষ হলমুখী হয়। এই যাত্রা শুরু হয় চান্দা [১৯৬২] ছবির মধ্য দিয়ে। তবে এই দশকে উল্লেখ করার মতো বাংলা ছবিও তৈরি হয়েছে; জোয়ার এলো [১৯৬২], সুতরাং [১৯৬৪] ইত্যাদি। উর্দু ছবির জোয়ার তখন এতোটাই প্রবল ছিল যে, জহির রায়হানও উর্দু ছবি তৈরি করেন। তবে এই জোয়ারে ভাটা পড়তে সময় লাগেনি। মানুষ যখন হতাশ, তখন নতুন এক ব্যাপার আমদানি হলো চলচ্চিত্রের কারখানায়, তার নাম লোককাহিনি। বানানো হলো রূপবান [১৯৬৫], বেহুলা [১৯৬৬], সিরাজউদ্দৌলা [১৯৬৭], সাত ভাই চম্পা [১৯৬৭] ইত্যাদি।
লোককাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রেও রুচি উঠে গেল দর্শকের ষাটের শেষ ভাগে। তত দিনে উত্তাল হয়ে উঠছে পূর্ববঙ্গের রাজনীতি। তাই মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়ের ওপর। তৎকালীন রাজনীতির বাস্তবতাকে রূপকের আশ্রয় নিয়ে নির্মিত হলো জীবন থেকে নেয়া [১৯৭০]। মুক্তিযুদ্ধের আগে নির্মিত এই চলচ্চিত্র রাজনৈতিকভাবে আয়নিত ছিল। এ কারণেই মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে পেরেছিল ছবিটি। এরপর তো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও লড়াই শুরু হলো, নয় মাস যুদ্ধ করল বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও শিল্পীরা। তখন জহির রায়হান, আলমগীর কবিররা গেরিলা কায়দায় বানাতে থাকেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র। মূল বিষয় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায়-অত্যাচার এবং একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে চলচ্চিত্রশিল্প যাত্রা শুরু করে। বিধ্বস্ত দেশ, বিধ্বস্ত অর্থনীতি, কিন্তু এর ভেতরেই চলচ্চিত্র ঘুরে দাঁড়াতে থাকে। সত্তরের দশকেও মুনাফাভিত্তিক চলচ্চিত্রে ন্যূনতম কিছু সারবস্তু দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি বাদেও এই দশকে আমরা তিতাস একটি নদীর নাম [১৯৭৩], সূর্যকন্যা [১৯৭৬], বসুন্ধরা [১৯৭৭], গোলাপী এখন ট্রেনে [১৯৭৮] বা সূর্য দীঘল বাড়ি’র [১৯৭৯] মতো চলচ্চিত্র পেয়েছি। কিন্তু গোটা আশির দশকে বাণিজ্যিক ধারা ছুটতে শুরু করে ভারতীয় বাণিজ্যিক ছবির পিছু পিছু। নারীকে ভ্যাম্প চরিত্রে দেখানো ঢাকাই ছবির রীতিতে দাঁড়িয়ে যায় তখন। যৌনতা, সহিংসতা ও হাস্যকর নকলপ্রবণতার দৌরাত্ম্যে প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে এই ভাটা আসার মূল কারণ আমার মনে হয়, নিজের কাজের প্রতি অসততা। অনেকে আবার নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কেও সচেতন নন। সমাজের সর্বস্তরে যে-মাত্রায় দুর্নীতি ও অসততা বাসা বেঁধেছে, তার ঢেউ আছড়ে পড়ছে চলচ্চিত্রেও। সকলেরই অর্থ চাই এবং সেটা বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রস্তুতিতে। এমন মনোবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যায়, শিল্পচর্চার সঙ্গে নয়...
আশির দশকে নকল, কাটপিস ছবি, তারকানির্ভর দুর্বল ছবি ইত্যাদির বিপরীতে শিল্পকে মাথায় রেখে চলচ্চিত্র বানাতে থাকেন তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম, তারেক মাসুদ প্রমুখ। বাণিজ্যিক ছবির ধরাবাঁধা সূত্রের বাইরে থাকা বিকল্পধারার নির্মাতারাই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করতে শুরু করেন। তারাই দেশের বাইরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং এখনো সেই ধারা কিছুটা অব্যাহত আছে। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই ধারাও ম্রিয়মাণ হয়েছে। এই ধারায় আগেও সব ছবি যে বিশ্বমানের হয়েছে, তা-ও নয়। আর ইদানীং অনুদান পাওয়া তথাকথিত বিকল্পধারার ছবি দেখলে যেকোনো চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কান্না পাবে। সেখানে দেদার বাণিজ্যিক উপাদান প্রবেশ করছে। বা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই অনুদান নিয়ে ছবি নির্মিত হচ্ছে। সরকারি টাকা তো নেওয়া হয়ই, ছবি শেষ করতে যুক্ত করা হয় বাইরের প্রযোজক। এবং শেষ পর্যন্ত ছবিটির মালিক বনে যান ওই বাইরের প্রযোজক। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, যেনতেন প্রস্তুতি নিয়ে শুধু অর্থের লোভে যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে এলেবেলে অনেক ‘পরিচালক’ ছবি বানাতে চলে আসছেন। অনেকে আবার জাতীয় পুরস্কারও বাগিয়ে নিচ্ছেন। তাই এসব ছবি নিয়েও দর্শক আর অতটা আগ্রহ দেখায় না।
বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে এই ভাটা আসার মূল কারণ আমার মনে হয়, নিজের কাজের প্রতি অসততা। অনেকে আবার নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কেও সচেতন নন। সমাজের সর্বস্তরে যে-মাত্রায় দুর্নীতি ও অসততা বাসা বেঁধেছে, তার ঢেউ আছড়ে পড়ছে চলচ্চিত্রেও। সকলেরই অর্থ চাই এবং সেটা বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রস্তুতিতে। এমন মনোবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যায়, শিল্পচর্চার সঙ্গে নয়। এখন আবার মহামারির কারণে চলচ্চিত্রশিল্পকে চাঙা করতে গঠন করা হয়েছে সরকারি তহবিল। কয়েক হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করলেও আসলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী করা সম্ভব নয়, যত দিন না এই নীতিনির্ধারকেরা প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্রকে ভালোবাসতে পারবেন, এর শক্তিকে অনুধাবন করতে পারবেন। শুধু অর্থ ঢাললেই উন্নত মানের ছবি নির্মাণ সম্ভব নয়। এযাবৎকালে অনেক টাকাই তো খরচ হয়েছে চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য। ধরুন, এফডিসি বা বিসিটিআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠান আছে, ফিল্ম আর্কাইভ আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে সারা বছরই নানা ধরনের ব্যস্ততা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেসব প্রতিষ্ঠান চালান কারা? তারা কি চলচ্চিত্রপ্রেমী? তাদের কি কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা দূরদৃষ্টি আছে?
আমাদের কাহিনিচিত্রের মতো জোয়ারভাটার দৃশ্য অবশ্য প্রামাণ্যচিত্র বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে পাওয়া যাবে না। না পাওয়ার কারণ, এসব ছবি কখনোই খুব একটা বড় আকারে আমাদের দেশে চর্চিত হয়নি, মানুষও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। ইদানীং মানুষের আগ্রহ বাড়ছে প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রতি, এমনকি ধারাবাহিকের প্রতিও। প্রযুক্তির সহজলভ্যতাই আসলে এই পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছে। কাহিনিচিত্রের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটা বলা মুশকিল, কিন্তু পরবর্তী দু-তিনটি ধারায় বাংলাদেশের উজ্জ্বল দিন রয়েছে বলেই অনুমান করতে পারি।
বাংলাদেশে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। তখন টিভির প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয়। ছোট পর্দায় ধীরে ধীরে যখন সপ্তাহান্তে চলচ্চিত্র দেখানো শুরু হলো, তখন সিনেমা হলমুখী মানুষের সংখ্যাও কমতে থাকে। অবশ্য এই দর্শক কমার পেছনে এককভাবে টিভিকে দোষারোপ করলে চলবে না। এর পেছনে ছবির লোকজনের অদক্ষতা, সিনেমা হলের দর্শক-অনুপোযোগী পরিবেশ এবং ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিও দায়ী। ষাট থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত চলচ্চিত্রের পাশাপাশি অনেক মানসম্মত টিভি অনুষ্ঠান ও নাটক আসলে দর্শকের মনকে তুষ্ট করেছে। ‘যদি কিছু মনে না করেন’, ‘হারজিৎ’, ‘সপ্তবর্ণা’, ‘আনন্দমেলা’, ‘ইত্যাদি’ নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান; ‘রক্তকরবী’, ‘সংশপ্তক’, ‘বহুব্রীহি’, ‘কোথাও কেউ নেই’ প্রভৃতি আকর্ষণীয় নাটক, মুভি অব দ্য উইকে ধ্রুপদি চলচ্চিত্র, শিশুদের জন্য বিদেশি কার্টুন ছবি এবং বাংলায় অনূদিত বিদেশি ধারাবাহিক—মানুষকে আটকে রেখেছিল জাদুমন্ত্রের মতো। এরপর একপর্যায়ে প্যাকেজ নাটকের যুগ এলো। একুশে টিভিতে নতুন স্বাদ পেল দর্শক। একুশে টিভি বন্ধের পর একই রুচির আরও কয়েকটি বেসরকারি টিভি শুরু হয়ে গেলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে অজস্র অনুষ্ঠানের চাপে। নতুন শতকের শুরুর দেড় দশকে মধ্যরাতের টক শো বেশ জমে উঠেছিল, ইদানীং আর সেগুলো মানুষ দেখছে না। গত দুই দশকে টিভিতে প্রচারিত নাটকের মানেরও অবনমন ঘটেছে। তা ছাড়া ঘড়ি ধরে টিভির অনুষ্ঠান দেখার অভ্যাসও বদলে গেছে। দর্শক এখন স্মার্টফোনের খুদে পর্দায় মজেছে। সেখানে ঘড়ি ধরে অনুষ্ঠান দেখার চাপ নেই। ইন্টারনেট সেবা থাকলে চাহিবামাত্রই মানুষ অনুষ্ঠান দেখতে পারছে কম্পিউটার ও স্মার্টফোনে। ইউটিউব ছাড়াও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বদৌলতে দর্শক এখন যেকোনো সময় দেখতে পারছে বড় পর্দার সিনেমা, আর ছোট পর্দার ধারাবাহিক।
সমাজ থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রের সমালোচনা আসলে গণতান্ত্রিক চর্চার একটি রূপ। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সমাজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তখন সে শিল্পচর্চাকেও বাধাগ্রস্ত করে। রাষ্ট্রের ‘বড় ভাই’সুলভ আচরণের কারণে সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি দানা বাঁধে। এই সংস্কৃতির ভেতর প্রচুর ‘জি-হুজুর’ ও ‘নির্বিষ’ ছবি নির্মিত হবে। এমন সময়েই দরকার হয় সাহসের, প্রয়োজন পড়ে ‘জীবন থেকে নেয়া’র...
দেশীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মতো খুনোখুনি, চোর-পুলিশ খেলা, যৌনতা—এসব সহজ সূত্রেই কাহিনি সাজাচ্ছে। মানুষ সেসবই দেখছে। অর্থাৎ দেড়-দুই ঘণ্টার কাহিনিচিত্রের চেয়ে, ঘরে বসে দশ থেকে আশি ঘণ্টা পর্যন্ত তারা ব্যয় করছে ওয়েব সিরিজের পেছনে। এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো। একসময় বাংলাদেশের দর্শক হুমড়ি খেয়ে বিটিভির ‘রুচিশীল’ ধারাবাহিক দেখত। সেখানে শিল্পকে মানুষের কাছে নেওয়ার জন্য সহজ পথ অবলম্বন করা হয়নি। কারণ, সেগুলো ছিল জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত এবং পরিবারের সবাই মিলে দেখার জন্য নির্মিত। কিন্তু এখন তো দর্শক কালেক্টিভ নেই। তারা সিনেমা হলেও খুব একটা যায় না, বাসাতেও পরিবারের সদস্যরা মিলে কিছু দেখে না। দেখাটা এখন অনেক বেশি সাবজেক্টিভ। যার যার দেখা তার তার রুচি অনুযায়ী। স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের পর্দাই তাদের এখন প্রেক্ষাগৃহ বা টেলিভিশনের পর্দা। যেহেতু একা একা দেখা হয়, আধুনিক কালের প্রযোজনাগুলো তাই সেখানে সামষ্টিক নীতিনৈতিকতার বালাই নেই।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও কিন্তু এরই মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। মানুষ একটু একটু করে সরে আসছে কাহিনিচিত্রের কাছ থেকে। হলিউডের স্বনামধন্য চিত্রনাট্যকার পল শ্রেডার সম্প্রতি ‘দি নিউ ইয়র্কার’ পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, কাহিনিচিত্রের দিন শেষ হওয়ার পথে। বাস্তবতাকে অনুধাবন করে তিনি বলছেন দুই-আড়াই ঘণ্টার ছবিগুলো প্রেক্ষাগৃহের উপযোগী করে বানানোর কথা। সেখানে মানুষ যাবে, দেড়-দুই ঘণ্টা সময় কাটিয়ে চলে আসবে। কিন্তু মহামারি ও অন্যান্য বাধাবিপত্তি, চলমানচিত্র দেখার সংস্কৃতি পরিবর্তনের কারণে মানুষ আর প্রেক্ষাগৃহে খুব একটা যাচ্ছে না। শ্রেডার বলছেন, এই কারণেই মানুষ ওটিটিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং কাহিনিচিত্রের পাশাপাশি প্রামাণ্যচিত্র ও ধারাবাহিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ, ওটিটির শোকেসে ভরপুর প্রামাণ্য বা তথ্যচিত্রও আছে।
আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সময়ে মানুষ অনেক বেশি তথ্যনির্ভর হয়ে উঠছে, আর তথ্যের প্রতি তাদের ভালোবাসাও বেড়ে গেছে। এ কারণেই বোধ হয় গল্প-কাহিনির চলচ্চিত্র নয়, তথ্যের জোগানদাতা প্রামাণ্যচিত্রের কাছে দর্শক বেশি যাচ্ছে নিজেদের চাহিদা মেটাতে। কারণ, ইদানীং মনে করা হচ্ছে তথ্যই জ্ঞান, তথ্যই ক্ষমতা। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে, সে তত এগিয়ে আছে। তথ্যনির্ভর এই সভ্যতা স্বভাবতই বোধ করি মানুষকে তুলনামূলকভাবে তথ্যচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছে অনেকাংশে।
বড় পর্দা, ছোট পর্দা এবং খুদে পর্দা—এই তিন পর্দাতে যুগে যুগে মানুষের রুচি অনুযায়ী দৃশ্যগত আধেয় পাল্টেছে, মানুষ একটা ছেড়ে আরেকটা ধরেছে। আধারের সঙ্গে আধেয়তে এসেছে পরিবর্তন। তবে আগের দুই পর্দার মতো ইদানীং খুদে পর্দাতেও চলছে লাগাম পরানোর পাঁয়তারা। যেহেতু কর্তনের ভীতি নেই, তাই দেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে লাগামহীনভাবেই যৌনতা ও সহিংসতানির্ভর দৃশ্য নির্মাণ চলছে। ইদানীং সেসব নিয়ে তর্ক উঠেছে। তবে যেটি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হলো, অশ্লীলতা ও সহিংসতা বন্ধের নামে আমরা ওয়েব সিরিজে শিল্পের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছি কি? কারণ, ওয়েবে চলচ্চিত্রও মুক্তি দেওয়া যায় কোনো রকম সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়া। কাজেই সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলও এটি নিয়ে চিন্তিত।
শাসকশ্রেণির দুশ্চিন্তা নিয়ে এটুকু বলা যায়, চলচ্চিত্র, আন্তর্জালিক ধারাবাহিক বা প্রামাণ্যচিত্র যদি সমাজের দর্পণ হয়, তাহলে এটাই তো স্বাভাবিক যে, মাধ্যমগুলোতে সমাজের নানা বিষয় উঠে আসবে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সমাজের ওপর নানা কায়দা-কানুন নিয়ে চেপে বসে তখন শিল্পচর্চা স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে; স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনীস্রোত বাধাগ্রস্ত হয়। অশ্লীলতা বন্ধের নামে ‘উচিত সমালোচনা’ বা ব্যঙ্গবিদ্রূপও বন্ধ করে ফেলার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। সমাজে সমালোচনা থাকবেই। সমাজ থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রের সমালোচনা আসলে গণতান্ত্রিক চর্চার একটি রূপ। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সমাজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তখন সে শিল্পচর্চাকেও বাধাগ্রস্ত করে। রাষ্ট্রের ‘বড় ভাই’সুলভ আচরণের কারণে সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি দানা বাঁধে। এই সংস্কৃতির ভেতর প্রচুর ‘জি-হুজুর’ ও ‘নির্বিষ’ ছবি নির্মিত হবে। এমন সময়েই দরকার হয় সাহসের, প্রয়োজন পড়ে ‘জীবন থেকে নেয়া’র।