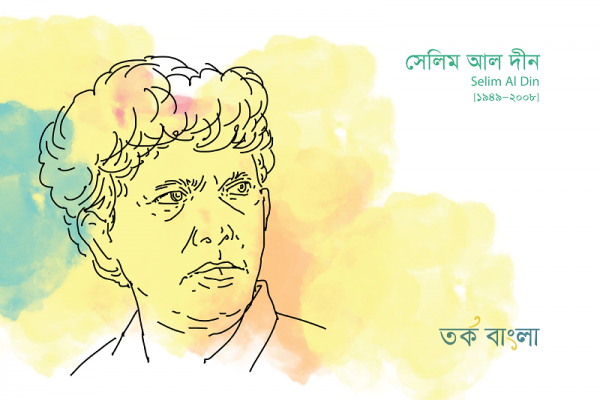
সেলিম আল দীনের দোদুল্যমানতা!
আমার চাচা সেলিম আল দীন। চাচা মানে বড় চাচা, আমার বাবার ইমিডিয়েট বড় ভাই। তাঁরা মোট তিন ভাই, চার বোন। তাঁদের মধ্যে এক বোনের মৃত্যু হয়েছে আমাদের ছোটবেলাতেই। সেলিম আল দীনের বড় বোন এখনো বেঁচে আছেন। বাকি সব ভাই-বোনও বেঁচে আছেন। শুধু তিনি নাই। তাঁর স্ত্রীও গত হয়েছেন। তাঁদের কোনো সন্তান নাই। ফলে বড় চাচা আমাদের জন্য এখন শুধুই রক্তের সম্পর্কের স্মৃতি। তিনি নাই—এটা আমাদের বিশ্বাস হতো না দীর্ঘ সময়। অন্তত আমার, অনেক দিন তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নে দেখতাম—তিনি মারা যান নাই! কিছুটা অসুস্থ অবস্থায় ওনার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় একা একা বেঁচে আছেন। অথবা দেখতাম, তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছেন আবার। তখনো একা। ওনাকে আমি স্বপ্নে সব সময় একাই দেখেছি, আর অসুস্থ। মৃত্যু থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত, অবসন্ন এক মানুষ। আমার সঙ্গে তাঁর স্বপ্নে দেখা হতো। বলশালী দেহ ও মনের স্মৃতি নিয়ে এক ন্যুব্জ মানুষ তিনি।
সেলিম আল দীন মারা যাবেন, সেটা কখনো আমার মনে হয় নাই। তাঁকে যখন জাহাঙ্গীরনগর থেকে নিয়ে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, তখন আমি সঙ্গে ছিলাম। আমার কখনো মনে হয় নাই তিনি আর ফিরে আসবেন না। সারাক্ষণ স্বাস্থ্য-সচেতন এক মানুষ শরীরে এত রোগ নিয়ে বেঁচে ছিলেন, আমার সেটা মনেই হয় নাই। তাঁর মৃত্যু আমাদের ভাবনারও অতীত ছিল। তিনি চলে যাওয়ার পর যখন গ্রামে যেতাম, মনে হতো তিনি আছেন। আমাদের বাড়ির ছাতিম গাছ, তাঁর লাগানো শিউলি, বকুল, আম, নিম—সব গাছের মতোই তিনি আছেন। বাড়িতে গেলে তিনি হুল্লোড় করতেন। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতেন। ফেনীর সেই বিরান গ্রামে গায়ক চলে আসত আমাদের বাড়িতে তাঁর আসার খবরে। রাতে গান হতো, আগুন জ্বলত। গভীর রাতের মতো আমাদের চোখের পর্দা ভারী হয়ে যেত। জ্যান্ত শঙ্খিনী সাপ ধরে তিনি আমাদের ভয় দেখাতেন। শঙ্খিনী সাপের নাকি দুই মাথা, কথাটা মিথ্যা—তিনি ধরে ধরে আমাদের দেখাতেন। মাছ ধরতে তাঁর সঙ্গে নেমে যেতাম পুকুরে।
তাঁর বাড়ি যাওয়া মানে হুলুস্থুল ঘটনা। দল বেঁধে যেতেন, হইচই করতেন, আবার ফিরতেনও দল বেঁধে। যতটা সময় বাড়িতে থাকতেন, ততটা সময় তিনি মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। সব বয়সের, অর্থনৈতিক অবস্থার আত্মীয়দের কেন্দ্র হয়ে উঠতেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে পারিবারিক ব্যবধান, রেষারেষি বিলুপ্ত হতো। খুশির বায়ু সবাইকে আচ্ছন্ন রাখত। বাড়ি যেতেন সাধারণত শীতে। অথবা ঈদের সময়। তিনি যেতেন সবার আগে, যখন বাড়িতে কেউ থাকত না। গিয়ে লেখালেখি করতেন। গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন। ভোরে তাঁর সকালের হাঁটার সঙ্গী খুঁজতেন। শীতের হিম সকালে সূর্য ওঠার আগে লেপের ওম ছেড়ে ওনার সঙ্গে হাঁটতে যাওয়া কষ্টের ছিল। আমাকে খুব বেশি তিনি নিজের সঙ্গী হিসেবে চাইতেন না। জানি না কেন। আমি কিছুটা নির্লিপ্ত স্বভাবের—সে জন্য হয়তো। অথবা ভাবতেন, আমাকে আমার মতো ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কী ভাবতেন আমাকে নিয়ে, সেটা আমি ভেবেছি। ভেবে কী পেয়েছি, সেটা পরে বলব কখনো।
তাঁর বাড়ি যাওয়া মানে হুলুস্থুল ঘটনা। দল বেঁধে যেতেন, হইচই করতেন, আবার ফিরতেনও দল বেঁধে। যতটা সময় বাড়িতে থাকতেন, ততটা সময় তিনি মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। সব বয়সের, অর্থনৈতিক অবস্থার আত্মীয়দের কেন্দ্র হয়ে উঠতেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে পারিবারিক ব্যবধান, রেষারেষি বিলুপ্ত হতো। খুশির বায়ু সবাইকে আচ্ছন্ন রাখত।

সেলিম আল দীন © পারিবারিক অ্যালবাম
সেলিম আল দীনের শেষ বাড়ি যাওয়ার বছরগুলোয় আমি পড়তাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়গুলোতে ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল মিশ্র। কখনো ওনার আচরণে বিরক্ত হয়েছি, কখনো ওনার ভালোবাসায় আপ্লুত। সেলিম আল দীনকে ছোটবেলা থেকে আমি যেভাবে দেখেছি, বড় হতে হতে সেই দেখায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে আসলে। নিজেকে তিনি অনেক বড় হিসেবে দেখাতে চাইতেন আমাদের সামনে, তাঁর স্টুডেন্টদের সামনে। আবার যখন ব্যক্তিগতভাবে মিশতেন, তখন দেখতাম তিনি আমাদেরই সমাজের আরও কোনো মানুষের মতো মিশছেন। তিনি পা ছুঁয়ে সালামে আমাদের বাধ্য করতেন। তাঁর কারণেই আমাদের পরিবারে এটা একটা রেওয়াজ হয়ে গেল যে, মুরব্বিদের পা ছুঁয়ে সালাম করতে হবে। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁর লেখা নাটক টিভিতে দেখায়, তাঁর সাক্ষাৎকার ছাপা হয় পত্রিকায়—আমরা যখন ফেনীতে ছিলাম, তখন এসব ছিল বড় ব্যাপার। ফলে তাঁর যেকোনো আদেশ-নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। যেমন, তিনি বলতেন থুতু না ফেলতে। থুতু হলো শরীরের আঠা। সারাক্ষণ যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা আমাদের কয়েকজন আত্মীয়কে দেখতাম—তিনি বলার পর সেটা গিলে খাচ্ছেন। তিনি আমাদের খেতেও শিখিয়েছিলেন। এ সময় জামআলুর ভর্তার কথা মনে পড়ছে। এর বাইরে ছোট মাছ, টাটকিনি মাছ, ব্রকলি, বিভিন্ন সবজি। মৃত্যুর আগে নাকি তিনি বীজধান খেতে চেয়েছিলেন। মফস্বলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে ক্রমে মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠা আমাদের পরিবারে তিনি ছিলেন একমাত্র ‘এলিট’।
ফেনী ছোট্ট এক মফস্বল তখন। সকাল থেকে হাঁটতে শুরু করলে দুপুরেই যে শহর শেষ হয়ে যায়। আর আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি সেখানে সন্ত্রাস, অস্ত্র, রক্ত। লেখাপড়া বলতে শুধু স্কুল আর কলেজ। কিছু কিছু নাটকের চর্চা অবশ্য ছিল। আমাদের একেবারে ছোটবেলায় বইয়ের দোকানও ছিল না। সেই ফেনীতে থেকে সেলিম আল দীনের আত্মীয়তা আমাদের জন্য ছিল গৌরবের। নিজেরা নিজেরা এ নিয়ে মনে মনে পুলক অনুভব করতাম। বলতামও হয়তো প্রতিবেশী বা বন্ধুদের—এখন মনে নাই। চাচা ছোটবেলায় আমাদের ফেনী আসতেন শীতকালে। আমার বড় চাচি মেহেরুন্নেসা সেলিম আমাদের জন্য উলে বোনা সোয়েটার আর বড় বড় কমলা নিয়ে আসতেন। বিভিন্ন দেশের রূপকথার বই নিয়ে আসতেন। জাপান আর চীনের রূপকথার বই, রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন—সবই অনুবাদের। আমার জন্য সেগুলো ছিল বড় বড় জানালা। আমি তাঁদের আনা বই গোগ্রাসে গিলে ফেলতাম। এক বই নেড়েচেড়ে বারবার পড়তাম, ছবি দেখতাম, ভাবতাম। আমার মধ্যে নিভৃতচারিতার শুরু তখন থেকে। বই পড়ায় আমার কোনো সঙ্গী ছিল না। নিজে পড়ে নিজেই ভাবতাম কত কিছু। চাচাকে আমরা জানতাম লেখক হিসেবে। তিনি যে ‘নাট্যকার’, সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। চাচার মতো বিখ্যাত হব ভেবে আমিও লিখতাম। সেসব লেখা পরে গ্রামের ‘মোস্তফা ভাই’কে দিয়ে ওনার কাছে পাঠাতাম। তিনি সেসব পড়ে এত অট্টহাস্য করতেন যে, সুদূর ফেনী থেকে আমি শুনতে পেতাম। মুষড়ে পড়তাম তাঁর এই প্রতিক্রিয়ায়। তাঁকে ঘিরে অপছন্দ তৈরি হতো আমার। আমার সঙ্গে ছোট ভাই সিফাতও লিখত। তার লেখা হেসে উড়িয়ে দিলেও সেগুলো নাকি বেশি পছন্দ হতো ওনার। সেই মোস্তফা ভাই জাহাঙ্গীরনগর থেকে ঘুরে এসে এসব বলতেন আমাদের। মোস্তফা ভাই লোকটা অবশ্য গপ্পবাজ ছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতেন। তারপরও আমার লেখক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার দুনিয়াকে তাঁর সেসব কথা এত বড় বড় বজ্রপাতের মতো আহত করতে যে, সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মানসিক জোর ছিল না। আমি লেখা পাঠিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম চাচার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। সেই প্রতীক্ষার এমন অবসানের মানসিক ধকল দীর্ঘদিন সামাল দিতে পারি নাই। চাচার সঙ্গে পারিবারিক দূরত্বও বাড়ছিল নতুন করে আবার। তিনি ফেনী বা বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর বা চাচির কোনো কথা হতো না, আমি আর বই পেতাম না, সোয়েটার পরে দেখানো হতো না কাউকে—দেখো, চাচি নিজ হাতে বানিয়েছেন। বই পড়ার অভ্যাসটাও আমার জন্য সমস্যার হয়ে যাচ্ছিল। আমি চাচার সিলেবাসের বাইরে গিয়ে সেবা প্রকাশনী আর হুমায়ূন আহমেদ পড়তে শুরু করেছিলাম। যদিও তিনি আমাদের বাসায় হুমায়ূন আহমেদ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর নাটক দেখা-ও নিষিদ্ধ করলেন। আমরা সত্যি সত্যি ভয়ে ভয়ে যেন কোনো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছি এমন ভঙ্গিতে টেলিভিশনে বসে হুমায়ূনের নাটক দেখতাম। তবে তাঁর বই পড়তে হয়েছে আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে। সেই বই পড়তে গিয়ে মা-বাবার হাতে ধরা খেয়ে শাস্তিও পেতে হয়েছে।
চাচা ছোটবেলায় আমাদের ফেনী আসতেন শীতকালে। আমার বড় চাচি মেহেরুন্নেসা সেলিম আমাদের জন্য উলে বোনা সোয়েটার আর বড় বড় কমলা নিয়ে আসতেন। বিভিন্ন দেশের রূপকথার বই নিয়ে আসতেন। জাপান আর চীনের রূপকথার বই, রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন—সবই অনুবাদের। আমার জন্য সেগুলো ছিল বড় বড় জানালা...

গ্রামের বাড়িতে সাপ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছেন সেলিম আল দীন © পারিবারিক অ্যালবাম
চাচা বলতেন, হুমায়ূন আহমেদ ‘অসাহিত্য’ করেন। তাঁর সাহিত্য নিম্নমানের। আমি নিজে বই পড়া বা লেখালেখি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও ‘সাহিত্য’ ব্যাপারটা বুঝতাম না সেই বয়সে। আমি তখন শুধুই পাঠক। যা পাই তা-ই পড়ি। আমার দুই আত্মীয়ার প্রলোভনে পড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হুমায়ূন আহমেদও পড়ে ফেলি। তবে হুমায়ূনে আমি মগ্ন হতে পারি নাই। আমার কাছে ‘সাহিত্য’ ছিল আরও ব্যাপ্ত একটা বিষয়। এমন ঘটনা থাকবে যেটা দীর্ঘ সময় আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আমি স্কুলে যেতে যেতে বা হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকব—তেমন পরিসরের লেখা হুমায়ূনে পাই নাই। ফলে তা আর বেশি পড়া হতো না। কলকাতার উপন্যাসে যা পেতাম। আমার কিছুটা বয়স বাড়তে বাড়তে আমার স্কুলের পাশে একটা মোটামুটি ‘আধুনিক’ বইয়ের দোকান চালু হয়েছিল। নামটা মনে নাই তার। তাদের কাছ থেকে কিনে অনেক বই পড়তাম। তত দিনে চাচা আমার নিতান্তই চাচা হয়েছিলেন। তিনি নাট্যকার, কী নাটক লেখেন, তার গুরুত্ব কী সেসব বেমালুম ভুলেছিলাম। একেই বোধ হয় বলে চোখের বাহির তো মনেরও বাহির।
অথচ চাচা যখন আরও ছোট থাকতে আমাদের ফেনীর পূর্ব উকিল পাড়ার বাসায় আসতেন, সে দিনগুলো ছিল আমোদে ভরপুর। তিনি অনেক নাট্যাভিনেতাকে নিয়ে আসতেন। তাঁদের মধ্যে রাইসুল ইসলাম আসাদ, শহীদুজ্জামান সেলিম, ফারুক আহমেদদের কথা মনে পড়ছে। তাঁরা বাসায় এসে আমাকে কোলে নিতেন। কান্নার অভিনয় করে দেখাতেন। ফেনীর জহির রায়হান মিলনায়তনে নাটক করে আবার চলে যেতেন। তাঁদের চলে যাওয়ার স্মৃতি দীর্ঘদিন কাঁথামুড়ে ঘুমানোর মতো করে জড়িয়ে থাকতাম। সেই চাচা এরপর দীর্ঘদিন কেন যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সেই সময়ে বোধ করি তিনি ‘কেরামতমঙ্গল’ এর মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজে পাল্টে ফেলছিলেন।
তাঁর জাহাঙ্গীরনগরের বাসায় আমার যাওয়া হয়েছিল ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়। জাহাঙ্গীরনগর তখন থেকে আমার মনে ছাপ ফেলে। সেখানকার নীরবতা, মসৃণ নির্জন রাস্তা, বড় বড় গাছ, থির থির কাঁপুনির লেক—সব আমার মনে গেঁথে ছিল। জাহাঙ্গীরনগরও আমার এক অবসেশন হয়েছিল সেই সময়ে। ওনার বাসায় কয়েকবারই বাবা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর মতো বড় হওয়ার অনুপ্রেরণা পাই, সে জন্য। তাঁর বাসায় আমরা সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’ সিনেমাটা দেখেছিলাম। তিনি খুব ভক্ত ছিলেন সত্যজিতের আর রবীন্দ্রনাথের। নিজের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের মতো করে লেখার কেদারা আর টেবিল বানিয়েছিলেন। আমাদের দাদা পাকিস্তান আমলে কাস্টমসের মতো জায়গায় চাকরি করলেও অর্থনৈতিকভাবে ছিলেন সৎ। ফলে টানাপোড়েন ছিল। তাই সেলিম আল দীনসহ তাঁর অন্য ভাইদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল আত্মীয়ের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ছাত্রজীবনে। নিজের পরবর্তী জীবনে তিনি সেই আক্ষেপ ভুলতে পারেন নাই। গ্রামের আধাটিনের বাড়িকে ডুপ্লেক্সে রূপান্তরে তাঁর অদম্য চেষ্টা আমি দেখেছি। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল না তাঁর। ওনার বিরোধিতা, আর্থিক কমতির মধ্যেও ডুপ্লেক্স বাড়ি করেছিলেন। ওনার দীর্ঘদিনের সঙ্গী স্টেশন ওয়াগন বাদ দিয়ে পরে প্রিমিও কিনেছিলেন। প্রিমিও যেদিন আসে জাহাঙ্গীরনগরে, আমাকে ডেকে নিয়ে চড়িয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন তিনি আর বেঁচে থাকেন নাই।
তাঁর মামার বাড়ির লোকদের নিজের কীর্তি আর সাফল্য দেখানোর একটা ঝোঁক ওনার মধ্যে কাজ করত। নিজের মায়ের খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু জানা যায়, মায়ের মৃত্যুর পর দাফনের সময় তিনি দূর থেকে লাশ দেখে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। বিয়েও করেছিলেন নিজের ইচ্ছায়। বিয়ের পর কোথায় উঠবেন, তা নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। অনেক অভাবের মধ্য দিয়েই আসলে তাঁকে জীবন পার করতে হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি তাঁর ভেতরে আরেক ক্ষরণের জন্ম দিয়েছিল, যা থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসতে পারেন নাই।
জাহাঙ্গীরনগর বিষয়ে আগের মোহ আমার ফিকে হয়ে গেছে। জীবনের অন্য অনেক অর্থ আমার ভেতর ধরা দিয়েছে। মফস্বলে থেকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা, টেবিল-চেয়ারে খাওয়া, সোফায় বসা—যাবতীয় ইউরোপীয় কেতা ভন্ডুল করে দিলেন সেলিম আল দীন। নতুন করে তাঁর কাছে যাওয়ার পর আমি দেখলাম, সেলিম আল দীনের ভক্ত, শিষ্য অথবা শিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় অর্থে শুদ্ধ এবং আধুনিক জীবনযাপন করার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকলেও তিনি তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গীয়। গ্রাম ব্যাপারটা ওনার মধ্যে সব সময় ছিল।

ভাইয়ের মেয়ের বিয়ের আসরে অভিভাবক সেলিম আল দীন © পারিবারিক অ্যালবাম
ছোটবেলায় তাঁর বাসায় যাওয়ার পর বড়বেলায় আবার যখন গেলাম তখন আমি সবকিছুর অর্থ উদ্ধার করতে শিখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। যদিও জাহাঙ্গীরনগর বিষয়ে আগের মোহ আমার ফিকে হয়ে গেছে। জীবনের অন্য অনেক অর্থ আমার ভেতর ধরা দিয়েছে। মফস্বলে থেকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা, টেবিল-চেয়ারে খাওয়া, সোফায় বসা—যাবতীয় ইউরোপীয় কেতা ভন্ডুল করে দিলেন সেলিম আল দীন। নতুন করে তাঁর কাছে যাওয়ার পর আমি দেখলাম, সেলিম আল দীনের ভক্ত, শিষ্য অথবা শিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় অর্থে শুদ্ধ এবং আধুনিক জীবনযাপন করার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকলেও তিনি তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গীয়। গ্রাম ব্যাপারটা ওনার মধ্যে সব সময় ছিল। যথেষ্ট প্রমিত হতে পারেননি তিনি। ভাষায় ‘নোয়াখালীর টান’ ওনার মধ্যে ছিল। পরিপাটি আর মেকি অভিজাত ঢাকার সমাবেশে তাঁর ভাষার টান ধরা পড়ছে—এমন নানা ঘটনা তিনি মজা করে বলতেন। তাঁর বাসায় সোফা ছিল না। বেতের আসন ছিল বসার জন্য। ডাইনিং টেবিলে তিনি খেতেন না, খেতেন মাটিতে বসে। ডাইনিং টেবিল ছিলও না। জাহাঙ্গীরনগরের শীতের সময়ে খেতেন রান্নাঘরে। আবার তাঁর ঘরেরই এক কোণে ফরাসি আর্টিস্ট পিয়েরে অগাস্তের ‘দ্য স্টর্ম’ পড়েছিল। একসময় তিনি বা তাঁর স্ত্রী কত যত্ন নিয়ে সেই আর্ট বাঁধাই করেছিলেন।
তিনি ফোনে হ্যালো না বলে হা বা হ্যাঁ বলতেন। হ্যালো ইংরেজি, ফলে তিনি বলবেন না। স্যুট পরতেন না, শার্টও না তেমন। ভেষজ খেতেন নানা রকম। চিকিৎসাপদ্ধতির প্রশ্নেও তিনি অ-ইউরোপীয় থাকতে চেয়েছেন। নাটক বিষয়ে তিনি বরাবর ইউরোপের গুণগান করতেন। মার্লো, ব্রেশট, মায়াকোভস্কি—এঁদের নিয়ে বলতেন বেশি বেশি। গ্যেটে, দান্তের কথা বলতেন। দেশি নাট্যকারদের কারও নাম নিয়েছেন মনে পড়ে না। জীবনে একবার ইউরোপ যাওয়ার শখও তিনি মিটিয়েছেন। কলকাতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। সেখানকার খোঁজখবর রাখতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সেলিম আল দীনের প্রেমের কারণ আবার ইউরোপ না। সামন্তীয় বাংলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো সামন্তীয় স্বভাব ছিল তাঁর কিছু কিছু। রাবীন্দ্রিক জমিদারি শান-শওকত পেতে চাইতেন। অ্যাসথেটিক্যালি উনি রবীন্দ্রনাথের জীবন পেতে চাইতেন। আবার রবীন্দ্রনাথের দিকে তাঁর একটা ইগো টের পাওয়া যেত খেয়াল করলে। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি অবশ্য আমাদের বুদ্ধিজীবী আজফার হোসেন তাঁকে দিয়েছিলেন। আজফার হোসেন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার বলেছেন।
সেলিম আল দীন কিছুটা ‘গ্রাম্য’ও ছিলেন। নিজের লেখা, নাটক—এসব বিষয়ে শহুরে শিল্পচর্চাকারী, পুরস্কারাকাঙ্ক্ষী হতে পারেন নাই। নিজের অবদান বিষয়ে নিজেই বেখেয়াল থাকতেন। নিজেকে ছোট গণ্ডির মধ্যেই বড় করে দেখাতেন। বড় পরিসরে, ঢাকায় থেকে অন্যদের মধ্যে নিজেকে বৃহৎ করে দেখানোর কনফিডেন্স ওনার ছিল না। শেষ সময়ে আমার মনে হয়—তিনি ঢাকা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। ঢাকায় থেকে এখানকার সাহিত্যের রাজনীতি, কষ্টকর জীবন-যাপন থেকে দূরে জাহাঙ্গীরনগরে কাটিয়ে দিয়েছেন। শেষ দিকে খুব গ্রামে যাওয়ার কথা বলতেন। নিজের অবদানের বিষয়ে অবশ্য গর্ব করে আমাদের বলতেন, ‘আমার মৃত্যুর পর তোরা আমার গুরুত্ব বুঝতে পারবি’।

মঈনুদ্দিন আহমেদের গল্প। সেলিম আল দীন নয়
জাহেদুল আলম হিটো
জুন ০২, ২০২১ ০২:৪৭

মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ। লেখাটা সীমিত পরিসরে আছে। এটা আরো বিস্তৃত করলে আপনাদের পাঠতৃপ্তি মিটবে। সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
সালাহ উদ্দিন শুভ্র
জুন ০২, ২০২১ ১৫:১৫

নয়া বুদ্ধিজীবি! তাঁর একটা চুলেরযোগ্য হও।
অভাগা বাঙালি
জুলাই ১০, ২০২১ ২০:৪৩




কী পেলাম এই লেখা থেকে! দোদুল্যমানতা! হায়! তর্ক বাংলাকে দোষ দেবো না লেখককে বুঝে উঠতে পারছি না। এমন স্কুল পড়ুয়া ছেলের গদ্য তর্ক বাংলায়! সেলিম আল দীনের লেখা নিয়ে তো নয়ই জীবনটাও গভীরে গিয়ে দেখাতে পারলেন না এই লেখক। অথচ তিনি শুভ্র সাহেব গল্প-উপন্যাস লেখেন বলে শুনেছি। পড়েছিও কিছুটা। সত্যিকার অর্থে খুব হতাশ লাগছে এই লেখা পড়ে। আমি সেলিম আল দীনকে আবিষ্কার করতে চাই একটু একটু করে সারাজীবন ধরে। আর লেখার শুরুতেই তিনি নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করায় ভেবেছিলাম ব্যক্তি সেলিমকে খুব করে পাবো। কিন্তু তা আর হলো কোথায়। এমন লেখা তর্ক বাংলায় না প্রকাশ করে স্কুল ম্যাগাজিনে খুব মানাতো। আর কিছু লেখার ধৈর্য নেই। স্যরি।
বোকাসোকা
জুন ০১, ২০২১ ১৩:২০