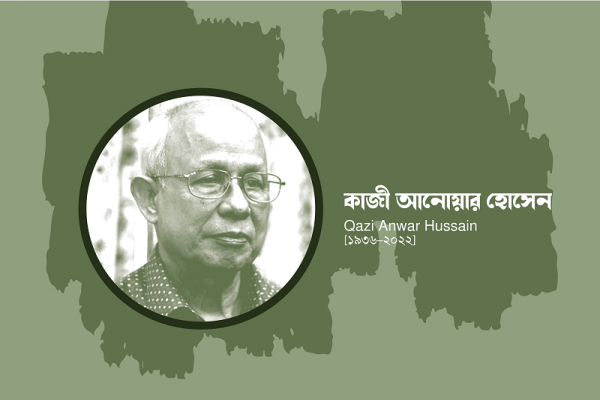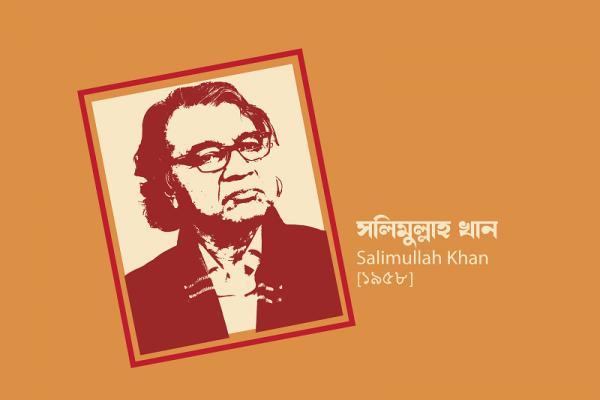জসীমউদ্দীনের দুষ্প্রাপ্য ও অগ্রন্থিত রচনা ‘মেঘনা’
জসীমউদ্দীন প্রসঙ্গে
বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ধারার কবি জসীমউদ্দীন। জন্ম ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে। মোহাম্মাদ জসীমউদ্দীন মোল্লা তাঁর পূর্ণ নাম হলেও তিনি জসীমউদ্দীন নামেই পরিচিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং এমএ ডিগ্রি লাভ করেন যথাক্রমে ১৯২৯ এবং ১৯৩১ সালে।
জসীমউদ্দীন স্কুলজীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতাটি প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যবইয়ে স্থান পায়। গাঁয়ের লোকের দৃষ্টিতে গ্রাম্য জীবন এবং পরিবেশ-প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলার জন্য জসীমউদ্দীন বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাখালী। পরে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় নকশী কাঁথার মাঠ, এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বইটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল নাগাদ, দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে জসীমউদ্দীন কাজ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকার একজন সংগ্রাহকও। তিনি ১০ হাজারের বেশি লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন, যার কিছু অংশ তার সংগীত সংকলন জারি গান এবং মুর্শিদা গানে স্থান পেয়েছে। তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের বিশদ ব্যাখ্যা এবং দর্শন খণ্ড আকারেও লিখে গেছেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে গেছেন।
জসীমউদ্দীন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী অনেক গান রচনা করেছেন। বাংলার বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন, তাঁর সহযোগিতায় কিছু অবিস্মরণীয় লোকগীতিতে সুর দিয়েছেন, বিশেষত ভাটিয়ালি ধারার। জসীমউদ্দীন রেডিওর জন্যও আধুনিক গান লিখেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন তিনি বহু দেশাত্মবোধক গান লিখেন। জসীমউদ্দীনের নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যটি ‘দি ফিল্ড অব এমব্রয়ডার্ড কুইল্ট’ এবং বাঙালীর হাসির গল্প গ্রন্থটি ফোক টেল্স অব ইস্ট পাকিস্তান নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বালুচর [১৯৩০], ধানখেত [১৯৩৩], সোজন বাদিয়ার ঘাট [১৯৩৪], হাসু [১৯৩৮], রূপবতি [১৯৪৬], মাটির কান্না [১৯৫১], এক পয়সার বাঁশী [১৯৫৬], সখিনা [১৯৫৯], সুচয়নী [১৯৬১], ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে [১৯৬২], মা যে জননী কান্দে [১৯৬৩], হলুদ বরণী [১৯৬৬], জলে লেখন [১৯৬৯], পদ্মা নদীর দেশে [১৯৬৯], কাফনের মিছিল [১৯৭৮] ও দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি [১৯৮৭]।
নাটক পদ্মাপার [১৯৫০], বেদের মেয়ে [১৯৫১], মধুমালা [১৯৫১], পল্লীবধূ [১৯৫৬], গ্রামের মেয়ে [১৯৫৯], ওগো পুস্পধনু [১৯৬৮] ও আসমান সিংহ [১৯৮৬]। আত্মকথা যাদের দেখেছি [[১৯৫১], ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় [১৯৬১], জীবন কথা [ ১৯৬৪], স্মৃতিপট [১৯৬৪], স্মরণের সরণী বাহি [১৯৭৮]। উপন্যাস বোবা কাহিনী [১৯৬৪]। ভ্রমণ কাহিনি চলে মুসাফির [১৯৫২], হলদে পরির দেশে [১৯৬৭], যে দেশে মানুষ বড় [১৯৬৮] ও জার্মানীর শহরে বন্দরে [১৯৭৫]। সঙ্গীত রঙিলা নায়ের মাঝি [১৯৩৫], গাঙের পাড় [১৯৬৪], জারি গান [১৯৬৮], মুর্শিদী গান [১৯৭৭]। অন্যান্য বাঙালির হাসির গল্প ১ম খণ্ড [১৯৬০], ২য় খণ্ড [১৯৬৪] ও ডালিমকুমার [১৯৮৬]।
তিনি প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড অব পারফরম্যান্স, পাকিস্তান [১৯৫৮] ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি, ভারত [১৯৬৯] লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে একুশে পদক ও ১৯৭৮ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার [মরণোত্তর] লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন জসীমউদ্দীন।
তর্ক বাংলা জসীমউদ্দীনের ‘মেঘনা’ নামের দুষ্প্রাপ্য ও অগ্রন্থিত রচনা পাঠকের জন্য উপস্থাপন করছে। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রায় ৭ দশক আগে, ১৯৫৪ সালে। এটি তিনি পাকিস্তান রেডিওতে পাঠ করেন। নদী পরিক্রমা নামের এক সংকলনে কথিকাটি প্রকাশিত হয়। সংকলনটির প্রকাশক পাকিস্তান পাবলিকেশান্স। বইটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় করাচি ও ঢাকা থেকে। কবির অমূল্য লেখাটি আমাদের সরবরাহ করেছেন শিল্পী গৌতম ঘোষ।
—সম্পাদক
এই সর্বনাশা মেঘনা নদীকে তবু আমার ভালো লাগে। চাঁদপুরের একটু সামনে যেখানটিতে পদ্মার সঙ্গে এর মিলন হয়েছে, সেই দৃশ্যটিকে মহাকবি কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ কাব্যের গঙ্গা-যমুনা-সংগমের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। পদ্মা এসেছে তার খোলা জলের গেরুয়া বসন গায়ে জড়িয়ে, আর মেঘনা এসেছে তার সুনীল জল-লহরীর নীলাম্বরীর অঞ্চল উড়িয়ে। কলো-ধলো দুটি মেয়ে যেন এখানে এসে হাত ধরাধারি করে নাচন শুরু করে দিয়েছে।
মেঘনা
আসামের খাসিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা আর কুশিয়ারা নদী পূর্ববঙ্গে এসে একসঙ্গে মিশে মেঘনা নাম নিয়েছে। ভৈরবের কাছে এসে ব্রহ্মপুত্র নদ তার সমস্ত জলধারার অঞ্জলি এই নদীতে ঢেলে দিয়েছে। তারপর নানা আকাঁবাঁকা পথ বেয়ে চাঁদপুরের কাছে এসে পদ্মার সঙ্গে সয়ালী পাতিয়ে, জলকল্লোলের ঘুঙুর বাজিয়ে একসঙ্গে নৃত্য করে ধীরে ধীরে নিজের প্রসারিত বক্ষ দুই তীরে বিস্তার করে হাতিয়া-সন্দ্বীপ অঞ্চলের কাছ ঘেঁষে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। লোকে কথায় বলে,—
যার নাই এগানা
সেই যায় মেঘনা।
এ-নদীর এপার হতে ওপার দেখা যায় না। অনন্ত জলধারার সীমানা মেলে ধরে আল্লাহর আসমান যেন তারই ওপরে সন্ধ্যা-সকালের রঙিন মেঘের রং মিশিয়ে চন্দ্র-সূর্যের, গ্রহ-নক্ষত্রের লেখন লিখে নীরবে পাঠ করছে। পদ্মার মতো এ-নদী তেমন খরস্রোতা নয়; তবু পদ্মার মতো সে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে তীরের ঘর-বাড়ি, বৃক্ষ-লতা ভেঙে, আপন বক্ষে ভেঙে বিলীন করে।
এই নদীর সঙ্গে যেন কত কাল ধরে তীরবাসীদের সংগ্রাম চলছে। নদীর কূলে কূলে গরিব কৃষাণেরা মা, বোন, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করে। জাংলা-ভরা সিম-লতা আর লাউলতার লহর। উঠান ভরা লাল নটে শাকের আলতা ছড়ানো। হঠাৎ কয়েকটি তরঙ্গের আঘাত দিয়ে এই উন্মাদিনী ভৈরবী নদী তাদের সকল চিহ্ন ভেঙে চুরমার করে তীরের সবকিছুকে আপন বক্ষে বিলীন করে। মেঘনা নদীর চাষি নদীর কাছে পরাজয় বরণ করে না। বড় বড় ঘাসী নৌকায় করে সে তার ঘর-বাড়ি বয়ে নিয়ে যায় ওপারের বালুচরে। সেখানে সাদা সাদা কাশগুচ্ছের সঙ্গেই বুঝি আড়াআড়ি করে চখাচখি, সরালি, বক, কাক পাখ বিস্তার করছে।
আবার নতুন গ্রাম তৈরি হয়ে ওঠে, আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা ছোট ছোট খড়ের ঘর। শেষ রাত্রের মোরগ না ডাকতে কৃষাণ-কনের ঢেঁকির পাড়ে সমস্ত গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে। লাউলতা আবার তার শাখা-বাহু বিস্তার করে জাংলার ওপর সাদা ফুল দোলায়। ‘কনে সাজানী’ সিঙ-লতার লহরে আসমানের সন্ধ্যা-সকালের সবগুলো রংকে হার মানায়। রাতের বেলায় উদাস কৃষাণের বাঁশের বাঁশির সুরে আসমানের চাঁদ বেয়ে বেয়ে জ্যোৎস্না ঝরতে থাকে।
মেঘনা আবার এ-কূল ভাঙে, ওরা অপর কূলে যেয়ে আবার আবাসের নীড় রচনা করে। কত যুগ-যুগান্তর ধরেই চলেছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা। আজও কেউ কারও কাছে হার মানল না। মেঘনা নদীর চাষি সমানে যুদ্ধ করে চলেছে এই কূল-ভাঙা নদীর সঙ্গে।
মেঘনা নদীতে ভাটির অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা বয়। জোয়ারের সময় মেঘনা নদীতে কেউ নাও ভাসাতে সাহস করে না।
বিশ্বকোষে এই নদীর অনেক কীর্তি-কাহিনি লেখা আছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই নদীতে প্রকাণ্ড ঝড় হয়। ৪০/৫০ ফিট উঁচু ঢেউ উঠে সমস্ত দ্বীপ নিমজ্জিত করে দেয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর আরেক ভীষণ ঝড় হয়। সেই ঝড়ে নোয়াখালী জেলার কিছু কিছু অংশ, হাতিয়া এবং সন্দ্বীপ অঞ্চল জলপ্লাবনে ভেসে যায়। সেই মহাঝড়ে গরু-বাছুর, পশু-পক্ষী যে কত মরেছিল, তার কোনো হিসাবই নেই। এক লক্ষের অধিক মানুষ এই রণ-তাণ্ডবিনীর চরণ-তলে দলিত হয়েছিল।
এই সর্বনাশা মেঘনা নদীকে তবু আমার ভালো লাগে। চাঁদপুরের একটু সামনে যেখানটিতে পদ্মার সঙ্গে এর মিলন হয়েছে, সেই দৃশ্যটিকে মহাকবি কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ কাব্যের গঙ্গা-যমুনা-সংগমের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। পদ্মা এসেছে তার খোলা জলের গেরুয়া বসন গায়ে জড়িয়ে, আর মেঘনা এসেছে তার সুনীল জল-লহরীর নীলাম্বরীর অঞ্চল উড়িয়ে। কলো-ধলো দুটি মেয়ে যেন এখানে এসে হাত ধরাধারি করে নাচন শুরু করে দিয়েছে।
বিশ্বকোষে এই নদীর অনেক কীর্তি-কাহিনি লেখা আছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই নদীতে প্রকাণ্ড ঝড় হয়। ৪০/৫০ ফিট উঁচু ঢেউ উঠে সমস্ত দ্বীপ নিমজ্জিত করে দেয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর আরেক ভীষণ ঝড় হয়। সেই ঝড়ে নোয়াখালী জেলার কিছু কিছু অংশ, হাতিয়া এবং সন্দ্বীপ অঞ্চল জলপ্লাবনে ভেসে যায়। সেই মহাঝড়ে গরু-বাছুর, পশু-পক্ষী যে কত মরেছিল, তার কোনো হিসাবই নেই। এক লক্ষের অধিক মানুষ এই রণ-তাণ্ডবিনীর চরণ-তলে দলিত হয়েছিল।

মেঘনায় সূর্যাস্ত © ছবি: সাহাদাত পারভেজ
শীতের আরম্ভ হতেই মেঘনা নদীর চরে চরে গাঁয়ের চাষিরা এসে বোরো ধানের সবুজ নকশা পরিয়ে যায়। বালুর বক্ষ লাঙলের আঘাতে চৌচির করে জলীধানের বীজ ছড়িয়ে যায়। চৈত্র মাসে নদীর কাছাকাছি ভিজে-মাটির পাকা বোরো ধানের রং সোনারুর গয়নার সোনাকে হার মানায়। ওপরে বালুচরে জলীধানের নতুন অঙ্কুরগুলো ধীরে ধীরে সবুজ পাতা বিস্তার করছে। সমস্ত চরটাই যেন সুন্দরী কৃষাণ-কুমারী, তার রঙের সবুজ শাড়িতে বোরো ধানের সোনালি রঙের পাড় নদীতীরের ঝিলিমিলি রোদে ঝিকমিক করে। তার ওপর দিয়ে সাদা সাদা বক মেয়েরা দলে দলে উড়ে বেড়ায়। রঙ-রঙিলা মাছরাঙা চঞ্চুতে করে মেঘনা নদীর পানি ছড়ায়। এতে সেই শাড়িতে বুনট-করা নকশার মতো কত রকমের ছবি ফুটে ওঠে।
আমাদের গোড়ই নদীর মতো সরু জলধারা বয়ে গাঁয়ের পথে পথে কেয়া-বনের আড়াল দিয়ে কদম গাছের ছায়ায় ছায়ায় গ্রাম্য মেয়েদের জল-ভরণের শব্দ শুনতে শুনতে গাঁয়েরই একজন হয়ে যায়নি। এর ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকোর ওপরে সাবধানে পা মেলে সওদা মাথায় করে হাটফেরা লোকগুলো বাড়ি ফেরে না। রূপকথার মায়াজালে একে আমরা আবদ্ধ করতে পারিনি।
এ-নদীর মাঝিয়াল গান করে—
ঘাটে লাগাও রে নাও,
কূলে লাগাও রে নাও,
আমি চিনে লই ব্যাপারীরে নাও ঘাটে লাগাও।
বাইলাম নৌকা ঘাটে হারে নাহি পাইলাম রে কূল,
আমি চিনে লই ব্যাপারীরে, নাও ঘাটে লাগাও।
আগা নৌকায় ঝামুর হা রে, পাছা নৌকায় রে দয়া,
তারির মদ্দি বইছেরে মনুয়া তনু হেলান দিয়া।
কাঠা লইলাম, কাছি হা রে, আরও লইলাম রে গুণ,
জনম ভইরা বায় রে মইলাম নাহি পাইলাম কূল।
কালো হেন মাঝি হা রে বেটা নৌকা বাইয়া রে যায়,
মলন কাষ্ঠ ধইরা রে কান্দে তোমার বাপ-মায়।
মেঘনা নদীর তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গের মাঝিয়াল এ-দেশের অপূর্ব ভাটিয়ালি সুরের সন্ধান পেয়েছে। এই মেঘনা নদীরও যেমন শেষ নেই, তার গানের সুরেরও শেষ নেই। সেই সুর, সে জীবন-গতির শেষ নেই, তার গানের সুরেও শেষ নেই। সেই সুর, সেই জীবন গতির অনন্ত জিজ্ঞাসার পথে ভাসিয়ে দিচ্ছে।
কেউ মেঘনা নদীর মাঝিকে আর এক চক্ষে দেখেন। মেঘনা নদীর মাঝিয়াল, সে ভেসে চলেছে, তার পেটের তাড়নায়। ভূমিহীন কৃষক সে। দেশ এখনো শিল্পায়িত হয়নি, সেই জন্য ডাঙ্গায় তার জন্য কাজ নেই। সে হয়তো তার স্ত্রীকে তিন দিন অনাহারে রেখে এসেছে। কচি ছেলেগুলোকে অনাহারে চিৎকার করতে দেখে এসেছে। তাদের মুখে অন্ন দিতে নদী-পথের যাত্রীদের সে পারাপার করে। যারা পার হয়ে যায়, তারা তাকে ঠকিয়ে যায়। তার পরিশ্রমের যা সত্যিকার মূল্য তার চাইতে অনেক কম তাকে দেয়। তাতে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের কথা তো দূরে থাকুক, তার নিজেরই পেটের ক্ষুধা মেটে না। আধপেটা খেয়ে তার উপার্জন থেকে সামান্য বাঁচিয়ে যা কিছু থাকে, তা সে তার পরিবারের লোকদের পাঠিয়ে দেয়। সে যাতে দিনের পর দিন এমনি করে ওদেরকে পারাপার করে, সেই জন্যে যাবার সময় মাঝিয়ালের কানে কানে তারা একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে যায়। তারা তাকে বলে: এই যে নদী, এ-নদী আসলে নদী নয়, সত্যকার নদী, এই ভব-নদী। এ-নদী পার হলেই তোমার জন্য সুখময় স্বর্গ। এখানে যত দুঃখ-কষ্ট করবে, সেই স্বর্গ তোমার কাছে তত লোভনীয় হবে।
আমি কিন্তু ওপরের ব্যাখ্যা মানিনে। সাহিত্যে আমরা কি দেখতে পাই? গ্রামের লোকেরা শহরের কথা শুনতে চায়; শহরের লোকেরা গ্রামের কথা শুনতে চায়। যা তারা নয়, সেই দূরের কল্পনাময় জগৎকে কাছে এনে তারা স্বপ্ন-জাল বুনতে চায়।
জেলেরা নদীতে জাল ফেলে বসে থাকে। মাসের পর মাস তারা নদীতে কাটায়। ভিন-গেরাম থেকে বৈরাগী আর বৈরাগিণী আসে তাদের গান শুনতে। এই জনহীন একক জীবনে, বৈরাগিণীর একতারার গান তাদের একঘেয়ে জীবনে, বৈচিত্র্য এনে দেয়। বৈরাগিণী গানের বদলে মাছ পায়, চাউল পায়। তাই নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যায়। হয়তো মাঝে মাঝে জেলে-বধূর পল্লির বিরল কুটিরে যেয়ে গেয়ে আসে সেই গানটি, যে গান নদী-তরঙ্গে ভেসে সে তার জেলেকে শুনিয়ে এসেছে।
মেঘনা নদী যখন শান্ত হয় তখন তার ওপরে রংবেরঙের পাল তুলে দিয়ে ছোট-বড় নৌকাগুলো হেলতে দুলতে থাকে। এ-দৃশ্য ভারি সুন্দর দেখায়। রংবেরঙের পাখিগুলো যেন জলের আসমানে উড়ে চলেছে।
জেলেরা নদীতে জাল ফেলে বসে থাকে। মাসের পর মাস তারা নদীতে কাটায়। ভিন-গেরাম থেকে বৈরাগী আর বৈরাগিণী আসে তাদের গান শুনতে। এই জনহীন একক জীবনে, বৈরাগিণীর একতারার গান তাদের একঘেয়ে জীবনে, বৈচিত্র্য এনে দেয়। বৈরাগিণী গানের বদলে মাছ পায়, চাউল পায়। তাই নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যায়। হয়তো মাঝে মাঝে জেলে-বধূর পল্লির বিরল কুটিরে যেয়ে গেয়ে আসে সেই গানটি, যে গান নদী-তরঙ্গে ভেসে সে তার জেলেকে শুনিয়ে এসেছে।
গাঁয়ে আঁকাবাঁকা কত পথ। এখান দিয়ে ঘুরে, ওখান দিয়ে ফিরে, গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে, সর্ষে ফুলের রেণুতে রঙিন হয়ে, কদম কেয়ার গন্ধে উদাস হয়ে এসে মিশেছে এই মেঘনা নদীর বুকে। সেই পথ দিয়ে পায়ের কাঁসার খাড়ু বাজিয়ে মাটির কলসটি কাঁখে নিয়ে কৃষাণ-কুমারী আসে মেঘনা নদীর পানি নিতে।
নদী-তীরের এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ও-পাড়ার রাখাল ছেলে গাঙের ঘাটের কাছে এসে আপন মনেই যেন গেয়ে যায়—
জল ভর সুন্দরী কন্যা, জলে ছিটাও ঢেউ।
হাসিমুখে কও না কথা, সঙ্গে নাই মোর কেউ।।
কাঁখের কলসের আঘাতে নদীতে ঢেউ দিয়ে, তার চাইতেও বেশি ঢেউ সেই রাখাল ছেলের মনে জাগিয়ে, হাসি-হাসি মুখে মেয়েটি গান ধরে—
পর-পুরুষের সঙ্গে আমার কোন কথা নাই।
ওদিকে সরে যাও হে নাগর, আমি জল ভরিয়া যাই।।
মেঘনা নদীর তীরে তীরে এমনি কত প্রেমের কাহিনি অভিনীত হচ্ছে দিনে দিনে। হলুদের মতো ডুগুডুগু অঙ্গে হলুদ মেখে কত মেয়ে নদীতে নাইতে আসে। তাদেরই অঙ্গের হলুদে রঙিন হয়ে মেঘনা নদী ভেসে যায় তার সুদূর সাগরের পানে।