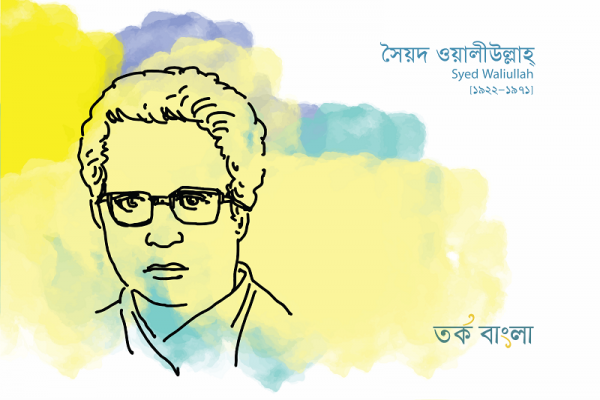উৎসের সন্ধানে রিজিয়া রহমান
আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় যে লেখকের কলম থেকে বেরিয়ে আসে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা, স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশটির সামাজিক বাস্তবতা, চা-বাগানের শ্রমিক বা সাঁওতাল কি বারবনিতাসহ সমাজের উপেক্ষিত মানুষের জীবনসংগ্রাম, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কিংবা অভিবাসী জীবনের নানান সংকট—তিনি আর কেউ নন, রিজিয়া রহমান। বহুমাত্রিক বিচিত্র পটভূমি ও চরিত্র নিয়ে সফলভাবে কাজ করে গেছেন তিনি, লেখক হিসেবে নিজেকে কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিভিন্ন ধরনের রচনা সৃষ্টি করে গেছেন, তবে তাঁকে চৌকস ঔপন্যাসিক হিসেবে উল্লেখ করলে অবিচার হবে না। বিচিত্র রচনার মধ্যে তাঁর উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অনন্য।
রিজিয়া রহমানের প্রতিটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও চরিত্রগুলো ভিন্নভাবে নির্মিত ও উপস্থাপিত। তিনি দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় কল্পকাহিনিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রাম যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়েছে, তেমনি বারবনিতার দৈনন্দিন জীবনও। একটি চরিত্রের কেবল কাহিনি বর্ণনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাকে অপ্রত্যাশিত অবস্থায় ফেলে প্রতিক্রিয়া দেখেছেন। উপন্যাসে বারবনিতার জীবনের কাহিনির সূত্র ধরে তাই আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের আগের আর পরের কাহিনি। তখন উপন্যাসটি না থাকে মুক্তিযুদ্ধের, না থাকে বারবনিতার জীবনের—সব মিলিয়ে সামগ্রিক সংগ্রামের এক দলিল হয়ে ওঠে। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে ছোট পরিসরে বিশাল জগৎকে ধারণের চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।
নারীর জীবনের হতাশা, পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হবার করুণ কাহিনি রিজিয়া রহমানের উপন্যাসে যেমন বিমূর্ত হয়েছে, তেমনি নারীর গর্জে ওঠার মতো চমকেরও অভাব নেই। সুদূর বেলুচিস্তানের স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে শুরু করে এ দেশের পতিতার জীবন কিংবা আদিবাসী জীবনগাথা—সবকিছুই মেলে তাঁর উপন্যাসে। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে রিজিয়া রহমান কোনো সাধারণ ঔপন্যাসিক নন, বরং একাধারে তীক্ষ্ম দৃষ্টিসংবলিত একজন সমাজতত্ত্ববিদ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস আশ্রয়ী সফল লেখক। একই ধারায়, কথাসাহিত্যিক, রিজিয়া রহমানের মুক্তিযুদ্ধ উপন্যাসের সংখ্যা বেশ কয়েকটি। আমাদের সমাজ ও জীবন বদলে দেওয়া, সার্বভৌমত্বের অধিকার জন্মানো চিরস্মরণীয় এ ঘটনাটিকে তিনি প্রতিটি উপন্যাসে ভিন্নমাত্রায় ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিচিত্র মানুষকে পৃথকভাবে প্রভাবিত করেছে, আর আজকের দিনেও মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী ভিন্নভাবে আলোড়িত করে। এর সুবিস্তৃত ব্যাপ্তিকে যে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করা যায়, তার প্রমাণ মেলে রিজিয়া রহমানের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আশ্রয়ী একাধিক উপন্যাসে।
ঠিক তেমনি উৎসে ফেরা উপন্যাসটি স্বাধীনতার বহু পরে লিখিত হলেও তার পরতে পরতে মুক্তিযুদ্ধ যেন টাটকা। এই উপন্যাস বর্তমানের হাত ধরে অতীতের দিকে ফেরার, খোদ মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের দিনগুলোতে ফেরা। রিজিয়া রহমানের নানান ঐতিহাসিক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাসগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কোনো কারণে এই উপন্যাস নিয়ে তেমন আলোচনা চোখে পড়েনি। এখানে ছোট পরিসরে মুক্তিযুদ্ধে কার্যকর বিভিন্ন দলভুক্ত মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে। বিপুল দক্ষতা নিয়ে অত্যন্ত অল্প বর্ণনায় অথচ স্পষ্টভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে সহজেই মুক্তিযুদ্ধে তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উৎসে ফেরা এক যাত্রার কাহিনি। শওকত আলীর যাত্রা উপন্যাস যেমন মুক্তিযুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা থেকে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় মানুষের জোরপূর্বক স্থানান্তরের কাহিনি, নাদিন গোর্ডিমারের শেষ যাত্রা [দ্য আলটিমেট সাফারি] যেমন বলপূর্বক অভিবাসনের পথে ধাবমান জনগোষ্ঠীর করুণ আর্তনাদ, তেমনি উৎসে ফেরা-ও এক যাত্রারই গল্প। তবে পার্থক্য হলো, এই যাত্রা অনিশ্চয়তার ভারে ক্লিষ্ট হয়ে পালানোর পথ খোঁজে না, বরং জেনেশুনে অতীতের ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার সাহস জোগায়। এখানে পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের যতই অভাব থাক, লেখকের সৃষ্ট বলিষ্ঠ চরিত্র, হাসনু দেশপ্রেমের আর্দ্রতায় সিক্ত হয়ে নিজের উৎসের কাছে ফিরবেই।
প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, উৎসে ফেরা নিছক কল্পকাহিনি নয়, বরং অনেকাংশেই ডকু ফিকশনের প্রভাব এতে লক্ষ করা যায়। কাহিনির বর্ণনার কোনো কোনো পর্যায়ে এ একেবারেই ডকু ফিকশন। লেখক উপন্যাস শুরুর আগের পাতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে ভূমিকার মতো করে উল্লেখ করেছেন, ‘সশস্ত্র বাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধার [মৃত অথবা জীবিত] এবং মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর নামের উল্লেখ এ উপন্যাসে গল্পের কাঠামোর প্রয়োজনেই করা হয়েছে।’ তবে ভূমিকাটির শুরুতে লেখক উপন্যাসে অবতারণা করা অন্য চরিত্রগুলোকে কাল্পনিক বলে দাবি করেছেন। কাল্পনিক বটে, তবে তারা আমাদের দেশের প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আগত সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।
এবারে আসা যাক উপন্যাসটির প্রসঙ্গে। জে এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের রানওয়ে অতিক্রম করার সময়ে উপন্যাসের পরদা ওঠে আর পরে তা বিস্তৃত হয় ঢাকা এয়ারপোর্ট অবধি। অর্থাৎ মূল চরিত্র, হাসনু তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের একপর্যায়ে আমেরিকা থেকে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন, ঠিক সেখানেই উপন্যাসের কাহিনির সূচনা। উড়োজাহাজে ওঠার মুখে তার দেখা হয় ইন্দিরা সিংয়ের সঙ্গে। হাসনু যখন দীর্ঘ বিরতির পর ঢাকার পথে উড়াল দিয়েছে আর মনে মনে ভাবছে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান, বিদ্যুৎ ঘাটতি, চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, পুলিশের অন্যায় নির্যাতন, ভেজাল খাবার, আর দূষণসহ নানান অধঃপতনের খবর জানার পরেও দেশের প্রতি নিজের তুমুল আগ্রহ বোধ করার কথা, তখনই ব্রাসেলসগামী প্রায় সমবয়সী নারী, ইন্দিরা সিং তার সঙ্গে কথা বলতে আসেন। ভারতীয় নারী, ইন্দিরা সিং হাসনুকে মনে করিয়ে দেন পাকিস্তানি সৈনিকদের অপরাধ, ‘জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ’-এর কথা। হাসনুর পরনে শাড়ি দেখে, বহুজাতিক সমাজ মানুষের সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিলেও নিজের শিকড়ের কাছে যে একসময় ফিরে যেতেই হয়, তা স্মরণ করে তিনি তৃপ্তি পান। আর তারপর হাসনুর মাথায় বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতির অনুরণনকে উসকে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে তিনি হুট করে হারিয়ে যান।
হাসনুর চেতনায় তোলপাড় করে তখন একাত্তর ঢুকে পড়ে। সেই সময়ের দিন-রাত আর অনুভূতির স্মৃতির মধ্যে হাবুডুবু খায় সে। আর সে কারণেই হয়তো সোজা চলে যায় একাত্তরে তাদের যৌথ পরিবারের উত্তাল দিনগুলোতে। হ্যাঁ, উপন্যাসটি এক পর্ব বর্তমানে, আর পরের পর্ব একাত্তরে, এই ছন্দে চলে। এই বিষয়টি যেকোনো কালের পাঠককে চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্তরে দিনযাপন করাতে বাধ্য। রিজিয়া রহমানের বর্ণনা ঋজু, কোথাও কোনো বাহুল্য নেই, খুঁজে পেতে একটা অপ্রয়োজনীয় বাক্যও মেলে না। অথচ সামান্য বর্ণনায়, ছাদে লেপ-কাঁথা মেলতে যাওয়া বাধ্য গৃহবধূ, হাসনু যে কাজ ভুলে আগুনরঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল উপচে পড়া গাছের দিকে উদাস তাকিয়ে থাকে, সেই ছবিটি দেখা যায়। তারপর প্রাচীনপন্থী নিয়মের ঘেরাটোপে আবদ্ধ পরিবারে শাশুড়ির ধমক আর ছাদে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার বেহায়াপনার অভিযোগের মুখে হাসনু ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢোকে। তখন ওটাই ছিল হাসনুর আশ্রয় আর দায়িত্ব পালনের জায়গা।
এরপর কাহিনি এগোনোর ছলে লেখক স্বভাবজাত হ্রস্ব বর্ণনায় একের পর এক চরিত্র বর্ণনা করেন। অসংবেদনশীল ও মুখরা শাশুড়ি, দায়িত্বশীল ও ডাকসাইটে শ্বশুর, নিরুপায় বড় জা, আহ্লাদি আর জেদি ননদ, চুপচাপ ও নিরপেক্ষ স্বামী আর ভাশুর, অন্যদিকে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর প্রতিবাদী দেবর—এই নিয়ে হাসনুর ব্যস্ত সংসার। দেবর রাশেদ কবিতা লেখে, গান গায়, শিল্পে তার বসবাস, তাই তার কাছে মানুষের অনুভূতির মূল্য আছে। হাসনু এ কারণে সুযোগ পেলে তার সঙ্গে কিছু সময় কাটায়। এ নিয়ে ননদ-শাশুড়ি চক্ষুশূলও হয়। হাসনু এসব মেনে নেয় স্বাভাবিকভাবে, উচ্চবাচ্য না করে গম্ভীর আর মোক্ষম জবাব দেয়।
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা যখন বাংলাদেশের মানুষ মেনে নিতে চায় না, তখন প্রতিবাদে রাশেদ রাস্তায় নেমে পড়ে। প্রতিবাদের ওই পথই তাকে একসময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করে। মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে চেনা মানুষগুলো অচেনা হয়ে ওঠে। গম্ভীর আর কথায় কথায় জাতপাত চলে যাবে বলে যিনি ধারণা করতেন, সেই শ্বশুর, রিয়াজই সবচেয়ে আগে বদলে যান। রক্ষণশীল গম্ভীর মানুষটি দেশের হালহকিকত বোঝার নিমিত্তে দুম করে একটা টেলিভিশন কিনে আনেন। ননদ ঝগড়া ভুলে মিলেমিশে থাকে। শাশুড়ি ভুলে যান ভুল ধরার জন্য বউদের চোখে চোখে রাখার কথা। এই সমস্ত বর্ণনায় লেখক রিজিয়া রহমান এটাই বোঝাতে চান যে, মুক্তিযুদ্ধের মতো সাধারণ শত্রু ধ্বংস করে স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ঘটনায় জাত আর মতের পার্থক্য ভুলে সবাইকে এক হতে হয়েছিল। রাজনৈতিক বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেককেই বদলে দিয়েছিল।
পরের পর্বে বর্তমানে ফিরে এলে দেখা মেলে হাসনু আর ইন্দিরার। তারা একই ভয়ংকর স্মৃতির অংশীদার হয়ে সামান্য দূরত্বে বসে একই উড়োজাহাজে গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ পলাতক ও বিদেশের বাসিন্দা এক রাজাকারের স্ত্রী আসে, হাসনুর পাশে বসে। নারীটি সেই আদর্শের কথা বলেন যা তাকে শেখানো হয়েছে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, ‘আমার সাহেব বলেন যে তারা ইসলামের জন্য কাজ করেছে পাকিস্তানিদের সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধারা সব ছিল হিন্দু।’ হাসনু রাগ গোপন করে প্রতিবাদ করলে তিনি নিষ্পাপ ভঙ্গিতে জানতে চান, ‘রাজাকার হওয়া কি খারাপ?’
হাসনু তখন প্রাণপণ চায়, চোখে ভিন্ন আদর্শের চশমা পরা রাজাকারের মূর্খ স্ত্রীটি দ্রুত তার সামনে থেকে সরে যাক। কিন্তু বাস্তবে এই ভেবেও তার মন ভারাক্রান্ত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরে রাজাকার বা পাকিস্তানিপন্থিরা কত বেশি সুসংগঠিত হয়েছে, যার থেকে মুক্তি নেই! এখন যেন মুক্তিযুদ্ধকালীন শত্রুর চেয়েও অনেক লুক্কায়িত শত্রু কিলবিল করছে চারদিকে। সামান্য কয়েকটা বাক্যে হাসনুর বিরক্তি আর বিপদগ্রস্ততা যেন আজকের এই সমাজের বেশির ভাগ মানুষের বিরক্তি আর বিপদ। স্বাধীনতার এত বছর পরে এ কোন মৌলবাদে আক্রান্ত বাংলাদেশ—এই হতাশা চরিত্রের সীমারেখা ছাড়িয়ে তখন পাঠককে আক্রান্ত করে। হাসনু নিজেও বিস্মিত হয়, এ কোন অদ্ভুত যাত্রা, যা তাকে ধীরে ধীরে পৌঁছে দিচ্ছে একাত্তরের সংগ্রামী দিনগুলোয়!
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ছাদে টাঙিয়ে উল্লাস করেছিল তাদের পরিবারটি। খোলা ছাদে আনন্দ প্রকাশে সেখানে পারিবারিক রক্ষণশীলতার বালাই ছিল না। এই সব আনন্দের স্মৃতিও হাসনুকে আক্রান্ত করে। ওদিকে উড়োজাহাজের আরেক যাত্রী, মাহবুব হাসান আসেন হাসনুর সঙ্গে গল্প করতে। বীর উত্তম মেজর রফিকুল ইসলামের কমান্ডে ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা মুক্তিযোদ্ধা তিনি। সেই পর্বে জানা যায়, একাত্তরে ২৫ মার্চের রাতেই হাসনু তার স্বামী, রাশেদকে হারিয়েছিলেন। ওষুধ কিনতে গিয়ে আর বাড়িতে ফেরেননি তিনি। এরপর দ্রুত বর্ণনায় জানা যায়, শেখ মুজিবকে বন্দি করেছে পাকিস্তানি জান্তা। দুদিন কোথাও আত্মগোপন করে থাকার পরে বাড়ির ছোট ছেলে, আবেদ ফিরে আসে। এরই মধ্যে বাড়ির বড় বউ অপরিণত শিশু প্রসব করে। একের পর এক ঘটনার ঘনঘটায় পরিবারটি স্তব্ধ হয়ে যায়।
পাতায় পাতায় বর্ণনার সূত্র ধরে মূল চরিত্র, হাসনুর ওপরে বিয়োগান্ত ইতিহাসের ভার স্পষ্ট অনুভূত হয়। পাঠক নিজেও তখন তার বুকের ভেতরের চাপা কান্না ঠাওর করতে পারেন। বর্ণনা এগোতে এগোতে দ্বাদশ পর্বে অতীত আর বর্তমান—দুই কাল এক বিন্দুতে মিলে যায়। অতীতের বর্ণনাটা যেন হাসনুর চোখ বুজে দেখা কল্পনা বা নিছক স্বপ্ন! একদিন বাড়ির বড় ভাই, হামিদ অফিস থেকে ফিরে জানায়, ভারত-বাংলাদেশের সশস্ত্র যৌথ বাহিনী সীমান্ত ধরে এগিয়ে আসছে, শিগগিরই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবে। এ রকম কথার পরে লেখক অল্প কথায় এ বিষয়ে তার রাজনৈতিক মতামতের কথা জানান। পরিবারের সবচেয়ে গম্ভীর ও সম্মানিত সদস্য, রিয়াজ সাহেবের মুখে বিবৃত করেন যে, ভারত-পাকিস্তান নয়, যুদ্ধ হবে বাংলাদেশ ও তার মৈত্রীশক্তি ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের। ভুল শোধরাতে গিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, ‘বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী চুক্তি, সামরিক চুক্তির কথা মনে রাখতে পারছ না?’
তবে এর পরের পর্বেই ভারত সরকারের সামরিক চুক্তি ও সামরিক অফিসারদের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এসে উপন্যাসের কাহিনিকে নতুন মোড় দেয়। সেই যে রানওয়েতে হাসনুর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রবাসী ভারতীয় নারী, ইন্দিরা, তিনি আবারও কাহিনির কেন্দ্রে আসেন। তাচ্ছিল্যের সুরে তিনি হাসনুকে বলেন, ‘আচ্ছা, বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তানি আদর্শে ফিরে যেতে চায়? তাহলে বলো, কেন করেছিলে তোমরা মুক্তিযুদ্ধ?’ ইন্দিরার এ প্রশ্নের সূত্র ধরে তার দীর্ঘদিনের ক্ষোভের উন্মোচন ঘটে। যেন সামনে অপরাধীই বসে আছে, কিংবা সেই দেশেরই বিজয়ভোগী একজন মানুষ, যার কারণে ইন্দিরার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এর দায় যেমন পাকিস্তানিদের, ততটুকুই বাংলাদেশের মানুষের, বিশেষ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা টাইগার কাদের সিদ্দিকীর। ‘সিজ ফায়ার’-এর পর যুদ্ধ আবার শুরু না হয়ে যেন আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে, এ ব্যাপারে জেনারেল নিয়াজিকে লেখা জেনারেল নাগরার ছোট্ট চিরকুটের কথা উল্লেখ করে রাগে-দুঃখে ইন্দিরা বলে ফেলেন, ‘তোমাদের দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীকে জিজ্ঞেস কোরো।’ হাসনুর বিস্ময়ের সামনে ইন্দিরা প্রশ্নাকারে ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি তার স্বামী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য, রাজের হত্যার কথা বলেন। নিজের বর্ণনায় নিজেই একসময় কাতর হন, ‘পনেরোই ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানিদের আচমকা আক্রমণে তাকে প্রাণ দিতে হলো। অথচ জেনারেল নিয়াজির প্রস্তাবে জেনারেল মানেকশ পনেরোই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা থেকে যোলোই ডিসেম্বর সকাল নয়টা পর্যন্ত সাময়িক সিজ ফায়ার ঘোষণা করেছিল। রাজ তখন কমান্ডো বাহিনী নিয়ে মিরপুর ব্রিজে প্যাট্রলিংয়ে গিয়েছিল, ব্রিজের ওপর থেকে সিজ ফায়ার ভঙ্গ করে পাকিস্তানিরা ফায়ারিং শুরু করেছিল।’
বলা বাহুল্য, উপন্যাসের চরিত্র, ইন্দিরার স্বামী, রাজ সেই ফায়ারিংয়ের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু বর্ণনাটি ডকুফিকশনের ঢঙে এবং বাস্তবের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী এর সঙ্গে জড়িত, তাই ইতিহাসটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।
মূলত ঔপন্যাসিকের বর্ণনা এবং কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের স্বাধীনতা ’৭১ [প্রকাশ: আগস্ট ১৯৯৭] বইটি মিলিয়ে দেখলে উপন্যাসের কাহিনির এই পর্যায়ে পাঠক কিছুটা বিভ্রান্তির কবলে পড়তে পারে। স্বাধীনতা ’৭১ বইটির ৫৫২-৫৫৪ পাতায় উপন্যাসে উল্লেখিত এই ঘটনার বাস্তব বর্ণনা আছে। বীর উত্তম কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন, ‘তিনজন মিত্র সেনা ও একজন মুক্তিযোদ্ধা নাগরার লেখা বার্তা নিয়ে সাদা পতাকা না থাকায় একটি সাদা জামা উড়িয়ে শত্রু অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর দিকে দুটি জিপে ছুটল। ...প্রতিনিধিদল নিয়াজির কাছে নাগরার চিঠি পৌঁছে দিলে নিয়াজি আত্মসমর্পণে রাজি আছে বলে জানিয়ে দেয়। সামনে রক্তক্ষয়ী বিরাট যুদ্ধ হচ্ছে না এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করছে জেনে আনন্দে প্রতিনিধিদল নিজেদের সেনাপতিদের কাছে এই দারুণ সুখবরটি পৌঁছে দিতে হাওয়ার বেগে ছুটে আসছিল। আসার পথে আনন্দ-উদ্বেল আনমনা হয়ে গাড়িতে লটকানো সাদা জামাটি কখন যে প্রচণ্ড বাতাসে উড়ে গেছে তা তারা জানতেই পারেননি। তাই এই বিভ্রাট। ভুল যখন ভাঙল তখন যা হবার তা হয়ে গেছে। তিনজন সাথে সাথেই নিহত হলো।’
বীর উত্তম কাদের সিদ্দিকীর বইয়ে উল্লেখিত ঘটনার ওই তিনজন নিহত ব্যক্তির মধ্যেই লেখক রিজিয়া রহমান তার সৃষ্ট চরিত্র ভারতীয় সেনাসদস্য, রাজকে কল্পনা করেছেন। তবে বাস্তবের বিচারে এই হত্যার ঘটনাকে হয়তো সরাসরি পাকিস্তানি জিঘাংসার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় না। যুদ্ধের ময়দানে তুচ্ছ্ব ভুলের কারণে এ রকম ‘কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ’ অবাস্তব নয়। কিন্তু মৃত সৈনিকের প্রাণের মূল্য আছে। যে কারণেই মৃত্যু হোক না কেন, মৃত সেনাসদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। কাহিনি আগাতে গিয়ে লেখক পরে চরিত্র, ইন্দিরার বক্তব্যে জানিয়েছেন, ‘মুক্তিযুদ্ধে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারাতে বসেছে। একাত্তর সালে বাংলাদেশের যুদ্ধে সহায়তা দেওয়ার পেছনে ভারত সরকারের স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল কি ছিল না, সেটা রাজনৈতিক ব্যাপার। ...কেন একজন বিদেশি সৈনিক প্রাণপণ যুদ্ধ করে তোমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল?’
ডকুফিকশনের এই পর্যায়ে লেখকের দুটো মনোভাব প্রকাশ পায়। প্রথমত, ‘উদ্দেশ্য ছিল কি ছিল না’ বলে এর সমাধানের দায়ভার লেখক পাঠকের ওপরে বর্তেছেন। তবে এই দ্বিধার মধ্যেই উত্তর আছে—ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবার জন্য বৃহৎ শক্তি পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া জরুরি ছিল। আর বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা। দুই দেশের চাওয়া এক বিন্দুতে মিলেছিল। যুদ্ধে যোগদানের আগেই বিদেশি সৈনিকের সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকার কথা। এভাবে প্রেক্ষিত ও কাহিনি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রত্যেক ইতিহাস ও ডকুফিকশন পাঠককে সুনির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী করার প্রচারে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে রিজিয়া রহমানের ইতিহাসঘেঁষা উপন্যাস, উৎসে ফেরা অনেক বিস্তৃত বর্ণনায় না গিয়েও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।
এই প্রসঙ্গে, একেবারে শেষে এসে জানা যায়, চরিত্র হাসনুর দেবর, মুক্তিযোদ্ধা আবেদকে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্যরা ক্রসফায়ারে খুন করেছে। ঘটনাচক্রে জানা যায়, ‘সৎ রাজনীতির ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিল বলে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাকে বন্দি করা হয় এবং শক্তিধরদের অন্যায় অপরাধ ঢাকার জন্য তাকে বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হতে হলো।’ এখানে লক্ষণীয় যে, উপন্যাসটি লিখিত হবার বেশ পরে, ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দুঃখজনক তৎকালীন পরিস্থিতিটি উল্লেখ করার কারণে উপন্যাসের প্রথম পাতায় এর ‘রচনাকাল ২০০৫’ তা বিশেষভাবে বড় অক্ষরে উল্লেখ করতে হয়েছে। এতে করে পরবর্তী শাসনামলেও বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম পরিস্থিতি যে একই রসাতলে গিয়েছে, তার আভাস এই ডকুফিকশনে পাওয়া যায় না।
যাহোক, সব মিলিয়ে উৎসে ফেরা উপন্যাসটি অল্প পরিসরে শৈল্পিক আঁচড়ে বাংলাদেশের চিরস্মরণীয় বৃহৎ সংগ্রামের সঙ্গে চলমান সংকটের একটি সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, যা পাঠকের জন্য উপভোগ্য।